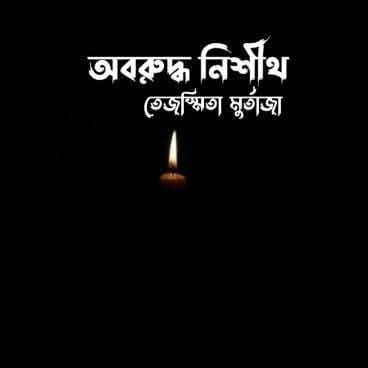#অবরুদ্ধ_নিশীথ
#তেজস্মিতা_মুর্তজা
৬৭. (প্রথমাংশ)
রাত দুটো। বৃষ্টি হালকা কমেছে বাইরে। হামজা শুয়ে ছিল। তার অভ্যাস এক কাত হয়ে মাথার নিচে হাতের তালু রেখে ঘুমানো। সাদা চশমাটা বালিশের পাশে পড়ে আছে। চশমা সে সবসময় ব্যবহার করে না, কেবল বই পড়ার সময়।
পরনে একটা অফ-হোয়াইট রঙা ফতোয়া। সাদা পাজামাটা উঠে আছে ঠ্যাংয়ের কাছে। কালো কুচকুচে পশমের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল রিমি। হাতে ছাদ থেকে তুলে আনা শুকনো কাপড়চোপড়। রিমি আগে একা অন্ধকার ড্রয়িং রুমে যেতেও ভয় পেত। এখন লাগে না। আরমিণ পারতো, এখন সেও পারে।
রিমি পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দরজার সামনে। তার কিচ্ছু ভালো লাগেনা আজকাল। সে কত খুশি ছিল সংসার জীবনে। ছোট্ট বয়সে কলেজের পড়ালেখা অবধি ছেড়েছিল এই লোকটার খাতিরে। আজ তার সঙ্গে এই দূরত্ব রিমির সহ্য হয় না।
সে নিজেকে রোজ বলছে, লোকটাকে সে ঘৃণা করে। খুব ঘৃণা। কিন্তু মনে হয় না কথাটা সত্যি। ঘৃণায় মায়া ও স্মৃতির দংশন থাকে কিনা জানা নেই রিমির। আবার রিমির আজও শুধু মনে হয়–হামজা শুধু একবার ফিরে আসুক এসব থেকে, সে হামজাকে কলিজা চেরা রক্ত দিয়ে ধুয়ে গ্রহণ করবে। ঘৃণায় এমন হয় কিনা তাও জানে না রিমি।
ঠান্ডা বাতাসে জানালার পর্দারা উড়ছে। সেই বাতাসে হামজার চুলগুলোও উড়ছে। রিমি অস্থির বুকটাকে নিয়ে মেঝেতে গেড়ে বসল হামজার সামনে। কান্নাটা থামানো যাচ্ছে না। এসব সময় কান্না ঠেকানো যায় না। খুব মুশকিল।
সে আসলেই ঘৃণা করে লোকটাকে। কিন্তু এটা ভাবলেও কষ্ট হয়। কোনো একসময় কাউকে প্রচণ্ড ভালোবেসে তারপর একবার তাকে যদি প্রচণ্ড ঘৃণা করতে হয়, সেটা করুণ এক যন্ত্রণার! এই যে রিমির ভেতরে যে প্রাচীর দাঁড়িয়েছে—লোকাটকে ভালোবাসার, ছোঁয়ার, অধিকার দেবার অথবা সমর্থন করার! এটা অসহ্য!
রিমি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। গম্ভীর মুখখানা। নেতা নেতা ভাব ছড়ানো। কঠোর ভদ্রলোক লাগে হামজাকে দেখতে। সেই ভদ্রলোকির মাঝে সূক্ষ্ণ এক ধূর্ততা, সাথে ভাবুকতাও। সময় পেলেই চোখে চশমা এঁটে ভারী ভারী সব বই খুলে বসতে দেখা যায়! তবু কীসের নেশায় ছুটছে হামজা! বড় হবার, আরও আরও বড় হবার! মানুষের মাঝে প্রবৃত্তি না থাকলে দুনিয়াটা স্বর্গ হতো।
চট করে এক লহমায় চোখ খুলে তাকায় হামজা। রিমি চমকে ওঠে। হামজা স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বলে, “কাঁদছো কেন?ʼʼ
রিমি জবাব দেয় না। দুজন তাকিয়ে থাকে দুজনের দিকে।
-“কিছু বলবে? এভাবে তাকিয়ে আছো কেন?ʼʼ
-“ঘৃণা মাপছি।ʼʼ
হামজা হাসল, “পেলে কতখানি?ʼʼ
-“মেপে শেষ করি!ʼʼ
হামজা উঠে বসে। অন্ধকারে প্যাকেট হাতরে সিগারেট বের করে তা ধরায়। ধোঁয়া ছেড়ে বলে, “পাবে না। আমি যাদেরকে জীবনে ভালোবেসেছি, তারা আমার প্রতি বিমুখ তো হতে পারে, আর সেটাই তাদের সবচেয়ে বড় যন্ত্রণার কারণ হবে।ʼʼ
রিমির গালে আলগোছে হাত রাখে হামজা।
রিমি শুধায়, “আপনার কষ্ট হয় না?ʼʼ
-“কষ্ট কী, রিমি?ʼʼ
-“বাঃ বাহ! সেটাও জানেন না! খুব সুখী লোক বুঝি, আপনি?ʼʼ
-“অসুখী?ʼʼ
-“বুঝি না আমি।ʼʼ
রিমি শক্ত হাতে চোখের পানি মুছলো। হামজার হাতদুটো সরিয়ে দিলো মুখ থেকে।
-“আমাকে খুব নিষ্ঠুর ভাবো?ʼʼ
তাচ্ছিল্যের সাথে স্লান হাসে রিমি, “না না। এমন সব বড় বড় ভুল ভাবনা ভাবতে নেই। তা ভাববো কেন?ʼʼ
-“এরকম সব কথা কে শেখাচ্ছে? আরমিণ?ʼʼ
-“আমার মুখ নেই?ʼʼ
হামজা চট করে হাসে, হাসির সাথে তামাকের ধোঁয়া উড়িয়ে বলে, “মুখ তোমার। কথাগুলো নয়।ʼʼ
-“আপনারা আরমিণকে ভয় পান?ʼʼ
-“নারীর প্রতিশোধপরায়নতা ও জেদ খড়ের গাদায় লাগা আগুনের চেয়েও ভয়াবহ। তা শুধুই ধিকিধিকি জ্বলতে জ্বলতে উপরের দিকে ওঠে, সব নিঃশেষ না করে নেভে না।ʼʼ
-“তাহলে আরমিণ সফল।ʼʼ
হামজা গভীর চোখে তাকা, কণ্ঠস্বর শ্লথ করে আবদার করে, “একটু কাছে আসবে?ʼʼ
রিমির মনে হলো—হামজা এক নিঠুর ও কৌশলগত শিকারী। যার মুখের বুলি বল্লম অথবা বর্ষার চেয়েও ধারালো। এভাবে একটা আহ্বানের মাঝে রিমির মতো দূর্বলপ্রাণ নারীকে মরণ দিতে শিকারী ছাড়া কে বা পারে?
রিমি ডুকরে কেঁদে উঠে হামজার বুকে হামলে পড়ল, “আপনি জানোয়ার। আপনি অমানুষ, আপনি আমাকে তিলে তিলে মেরে ফেলেছেন। একটুও দয় করেননি।ʼʼ শিউরে উঠছিল রিমির শরীর।
হামজা রিমিকে দুহাতের বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করে নিলো। রিমি ছটফট করছিল। হামজা শক্ত করে জড়িয়ে রেখে বলল, “তুমি আমার সহধর্মিনী হতে পারোনি, রিমি।ʼʼ
-“পারতে কী করতে হতো?ʼ
-“সহধর্মিনী শব্দটার একটা সাধারণ অর্থ আছে আমার কাছে।ʼʼ
-“আর সেটা কী?ʼʼ
-“সহ-ধর্ম। অর্থাৎ স্বামীর ধর্মে নিজেকে সমর্পিতকারিনী হয় সহধর্মিনী। সহযাত্রী বলতে যেমন একই পথের যাত্রাসঙ্গী বোঝায়। সহধর্মিনীর ব্যাপারটাও তাই। অথচ তুমি দিনেশেষে আমায় অস্বীকার করেছ, আমার ধর্মে ধার্মিক হতে পারোনি, সঙ্গ ছেড়েছ। মানতে পারোনি।ʼʼ
-“তার মানে আমি এখনও একটু হলেও মানুষ। মানুষেরা আপনাদের মানতে পারবে না।ʼʼ
হামজা অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল কেমন করে যেন। শান্ত, স্থির দৃষ্টি, একটু বিস্ময়। তার চোখদুটো হিসাবমেশিন যেন। কিছু মাপছে, হিসাব করছে। তা শেষে বলল, “শেখানো বুলি, রিমি। তোমাকে তৈরি করা হয়েছে।ʼʼ
রিমি চোখদুটো বুজে হিংস্র হাতে হামজার ফতোয়ার কলার খামছে ধরে, দাঁতে দাঁত চেপে ছটফট করতে করতে বলে, “কিচ্ছু শেখানো হয়নি। আমি ঘরের আসবাব নই, মানুষ। আপনি যে পর্দা আর খাঁচাটার সীমায় আমার বন্দি রেখেছিলেন, তা কোনো এক আঘাতে ভেঙে গেছে, এইতো! তবুও তো আপনার সব পাপকে প্রশ্রয় দিয়েছি তো। শুধু মনে মনে মানতে পারছি না। আর তো কিছু করার নেই আমার! নয়ত আজও পর্যন্ত পড়ে আছি আপনার এই নরকে? আমিও তো সমান পাপী। এত ভাবছেন কেন?ʼʼ
হামজা হাসে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বোজে, দুপাশে মাথা নেড়ে গাঢ় স্বরে বলে, “আরমিণ, আরমিণ! আমার খুব ক্ষতি করে ফেলেছে, রিমি।ʼʼ
-“কেমন ক্ষতি?ʼʼ
-“অনেক বড় ক্ষতি! বিশাল ক্ষতি। অপূরণীয় ক্ষতি।ʼʼ
কী যেন ছিল হামজার কণ্ঠে। শিউরে উঠে দ্রুত মুখ তুলল রিমি, “কী ভাবছেন আপনি?ʼʼ
হামজা হাসল, “তুমি জানো রিমি–ও কখনও কখনও চেঁচায়, তামাশা করে। তখন মনেহয় ও প্রচুর বোকা, অশান্ত নির্বোধ। কিন্তু সেইসবই যদি ওর পরিকল্পনামাফিক হয়? ও যদি এটাই চায় যে, আমরা ওকে ফাঁপা আর বোকা ভাবি? যেন ও কিছুই করতে পারছে না, শুধু তড়পাচ্ছে।ʼʼ
-“মানে?ʼʼ
হামজা হতাশ গলায় বলল, “রিমি, ভাঙনের চেয়ে ফাটল ভয়ঙ্কর। এই সূত্রটা আরমিণ প্রয়োগ করেছে। আমার পরিবারটাকে সূক্ষ্ণভাভে চিড়ে ফেলেছে। ও আমাদের সবাইকে ঘৃণা করতো। এরপর তরু জয়কে ঘৃণা করেছে, তুলি আমাদের সবাইকে ঘৃণা করেছে, তুমি আমাকে ঘৃণা করেছ, কখন না জানি জয় আমাকে……ও সফল, রিমি। সবার চোখে সবার জন্য ঘৃণার পটি বেঁধে দিতে পেরেছে।ʼʼ
রিমি মাথা নাড়ে, “আপনি ওর বিরুদ্ধে ভড়কাতে চাইছেন আমায়।ʼʼ
হামজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাসল, “আমার বোকা, বউ! খুব বেশি সময় কাটিয়েছ তুমি ওর সঙ্গে, হ্যাঁ?ʼʼ
রিমি চেতে উঠল, “ও আমাকে কখনোই কিছু বলেনি। ও খুব কম কথা বলে। আমি নিজে চোখে আপনাদের অপরাধ দেখেছি। ওকে এসব ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেও বলতে চায়নি।ʼʼ
-“আজ মনে হচ্ছে, তোমায় মূর্খ রেখে ভুল করেছি। তুমি জাননো রিমি, চিরকালই অনাগ্রহের প্রতি মানুষের প্রবল কৌতূহল। এজন্য ওর বেপরোয়া স্বভাব, ভীতিহীন চালে তুমি খুব ফেঁসেছ। জয়ের অবস্থাও খারাপ। পুরুষ মানুষ তো!ʼʼ
-“ফাঁসা কোনটাকে বলছেন?ʼʼ
-“এই যে! আমার সাথে তর্কে আসছো!ʼʼ
রিমি বলল, “আরমিণ বলেছিল, আপনি আমাকে আপনার অধীনে কয়েদ করে রেখেছেন। আপনার খারাপগুলো তাই দেখেও চোখে পড়েনা। আর আমি মেয়েও তো ভালো পরিবারের না। আমি শুধু ওর কথাগুলো মেলাচ্ছি, আর মুগ্ধ হচ্ছি ওর ওপর!ʼʼ
হামজা হেসে রিমিকে বুকে টেনে নিলো। শক্ত করে চেপে ধরে চোখ বুজল, “ওকে বন্দি রেখেছিলাম যাতে বাইরে বেরিয়ে কিছু পাকাতে না পারে। ও তখন ভেতরেই ছেঁদ শুরু করেছে। ইশ! বিশাল ক্ষতি, বিশাল ক্ষতি, রিমি! থেমে থাকেনি।ʼʼ
হামজার বুকে এভাবে সে হাজারবার মাথা রেখে তলিয়ে গেছে স্বর্গসমুদ্রে। আজও সেই বুক, সেই রিমি। শুধু সেই স্বর্গসমুদ্রের পানি শুকিয়েছে, সেখানে আজ খরখরে মরুর উত্তাপ বিরাজমান।
রিমির শরীরটা কাঁপছিল। হামজা বলল, “কাঁদছো কেন? ঘৃণা ফুরিয়েছে না বাড়ছে?ʼʼ
-“কোনোদিন ফুরোবে না।ʼʼ গর্জে উঠল রিমি। কান্নার সাথে ক্ষোভ ও গর্জন মিশে কেমন যেন লাগল রিমিটাকে।
হামজা হাসল, “যে অবধি কেউ পৌঁছায়নি, সেখানে তুমি জায়গা পেয়েছিলে। আর তুমিও সেখানে একটা খুব গভীর ছিদ্র করেছ, রিমি।ʼʼ
-“আপনি আমাকে খুব সুখ দিয়েছেন?ʼʼ
-“আশা রেখেছিলে কেন? আমি তো সুখের ব্যাপারী নই!ʼʼ
রিমি মৃদু চেঁচিয়ে উঠল, “আপনি তবে কীসের ব্যাপারী? রক্তের? অন্ধকারের? চিৎকার আর যন্ত্রণার?ʼʼ
হেসে জানালার দিকে তাকাল হামজা, “এগুলোই বা খারাপ কী? দুনিয়াতে শুধু সুখ থাকলে সুখের কদর থাকবে না। তাই কাউকে না কাউকে এসবের আমদানী করতেই হবে।ʼʼ
-“চুপ্প। চুপ। চুপ করুন, মুখোশধারী পুরুষ!ʼʼ
হামজা আস্তে কোরে ঠোঁটে আঙুল রেখে স্থির চোখে বলল, “চুপ করলাম।ʼʼ
-“আপনি তো এমন না। তবু আমার সামনে এমন নাটক কেন করেন?ʼʼ
-“আমি আসলে কেমন, রিমি? তোমাকে কী বোঝানো হয়েছে আমার ব্যাপারে?ʼʼ
-“আপনি জানোয়ার।ʼʼ
-“এখন কি মানুষদের মতো লাগছে?ʼʼ
রিমি কত কিছু বলতে গিয়েও পারে না। চোখ বুজে এলোমেলো শ্বাস ফেলে শব্দ করে। এরপর আবার চট করে হামজার কলারটা চেপে ধরে, “আমার…আমার খুব কষ্ট হয়, বোঝেন আপনি? বোঝার কথা না। কসাইয়েরা পশু জবাই করার সময় পশুর চোখে তাকিয়েও গলায় ছুরি চালাতে পারে। পেশা তো। তারা পশুর ভেতরের আর্তনাদ বুঝবে কেন?ʼʼ
-“তুমি বোঝো?ʼʼ
-“আপনার তো কষ্টই নেই। বোঝার কী?ʼʼ
-“এই বুঝেছ?ʼʼ
-“তাছাড়া আর কী বুঝিয়েছেন?ʼʼ
হামজা হেসে ফেলল, কেমন যেন হাসিটা! হাসি ঠোঁটে রেখে বলল, “তোমার মতো কাঁদতে বলছো? আমার সন্তানদুটো কোরবানী করার দুঃখে , আমাকে তোমার কাছ থেকে বঞ্চিত করার দুঃখে, আমার বিরুদ্ধে কারও নিন্দাকে মেনে নেবার দুঃখে, আরও কত কত দুঃখে কাঁদতে বলছো?ʼʼ
-“নিন্দা? আপনি নিজেও জানেন, একমাত্র আরমিণ আপনাকে সঠিক চেনে। যদি আরমিণের কাজকর্মে আমি কিছু শিখেও থাকি, তো ভুল শুধরে এতদিনে সঠিকটা শিখেছি। আর দুঃখ, সেটা আছে আপনার? দুঃখ তো মানুষেরা পায়। কসাইদের দুঃখ থাকে না। কান্না পায় আপনার?ʼʼ
-“তা পায় না ঠিকই। তবে…ʼʼ অস্পষ্ট স্বরে বলে, “তোমার প্রধান বিরোধী তবে আমি ছিলাম, আরমিণ! শ্যাহ! দূর্বল প্রতিদ্বন্দী ভেবে চোখের নাগালে রেখে যেন নিশ্চিন্ত ছিলাম। কী কী কেঁড়ে নিতে চাও?ʼʼ
রিমি ঠোঁট বাঁকিয়ে মলিন হাসে। হামজার সামনে মুখ উঁচিয়ে বাবু মেরে বসে। চোখে ছলছল করছে পানি। দাঁতে দাঁত শক্ত। ভ্রু-দুটো কাঁপছে। বুকের ভেতরে বোধহয় কালবৈশাখীর বাতাস বইছে। নিঃশ্বাসের শব্দ সন্ধ্যার স্তব্ধতায় আলোড়ন তুলেছে। রিমিও এবার দৃষ্টি স্থির করল হামজার চোখে। বারবার ঢোক গিলছে, বুকের সাথে শরীরটাও নড়ে নড়ে উঠছে। চঞ্চল চোখে হামজার গোটা মুখে বারবার চোখ বোলাচ্ছিল।
হামজা আচমকা শব্দহীন হেসে উঠল, চোখের পাতা নেমে এলো হাসির সাথে। বলল, “এভাবে তাকিয়ে থেকো না। চোখদুটোকে সামলাও। হামজা ওরকম দুটো গভীর দুঃখের সাগরে তলিয়ে গেলে কারবার সামলাবে কে?ʼʼ
-“কেন? তাকান আমার দিকে। আপনার তো কষ্ট নেই। অনুভূতির অভাবে ফেটে চৌচির জমির মতো আপনি। ʼʼ
হামজা অনড়, নির্বিকার মুখে ও অতল গহ্বরের মতো চোখদুটো মেলে তাকিয়ে রইল।
-“আরমিণ আর কী করেছে আমি জানি না। তবে আপনি এতটাই নির্লিপ্ত যে আমার দেয়া শাস্তিও আপনার নির্লিপ্ততায় প্রতিফলিত হয়ে আমার ওপরেই ফিরে এসেছে। আপনি এখনও অটল। একটু শেখাবেন আমায় এমন কঠোর প্রাণহীন হতে? আমার না ভেতরে খুব তীব্র অনুভূতি আর আবেগ। খুব জ্বালায় আমাকে। আমি আপনার মতো উদ্দেশ্যপ্রবণ হতে চাই। যাকে টলানো অসম্ভব।ʼʼ
হামজা হেসে মাথা নাড়ে দুপাশে। নীরবে ব্যাপারটা অস্বীকার করে নিচু করে চোখ। রিমি জোর করে থুতনি ধরে হামজাকে নিজের দিকে তাকাতে বাধ্য করে। শক্ত কণ্ঠে বলে, “তাকাতে চাচ্ছেন না কেন? তাকান। তাকান আমার দিকে। আমি আপনার নিষ্ঠুরতা দেখতে চাই। আপনি আমার ওপরে ঠিক কতটা উদাসীন ছিলেন, আর কতটা দায়সারা ছিলেন তার হিসেব করতে হবে তো! কারণ আমি আপনার চোখের সেইসব মিথ্যা মুগ্ধতা আর কর্তব্যপরায়ন চাহনিকে ভালোবাসা ধরে নিজেকে সঁপেছিলাম। তাকান… আমার চোখের দিকে।ʼʼ
হামজার চোখের পাতা নড়ে উঠল। রিমি বলল, “বিয়ে তো সবাই করে, মেয়র সাহেব। সংসারও করে যায় দিব্যি। কিন্তু আমি যে বয়সে আপনার বউ হয়ে এসেছি, না ছিল বয়সের মিল, না অনুভূতির। কিশোরী বয়সে এক তরতাজা পুরুষের কর্তব্য আর হাতের বাঁধনের প্রেমে পড়ার অপরাধে কী কী শাস্তি আর দেবেন? দিন। আজ সামনে আছি আমি। আপনার হাতের নাগাল ছেড়ে বেরোবার পথ তো নেই। সবটুকু শাস্তি দিয়ে দিন। দিনে দিনে সইতে পারছি না।ʼʼ
হামজা মুখ খুলতে চাইলেই রিমি হামজার ঠোঁটে আঙুল চাপে, “চুপ।….চুপ চুপ।ʼʼ
কেমন হাঁপানি রোগীর মতো নিঃশ্বাস ফেলল রিমি, “কেন ওভাবে ভালোবাসার ঢং করেছিলেন? আমার তো বয়স কম। আমি আপনার অত গভীর মারপ্যাচ বুঝিনা। আমার চারদিকে প্রেমে পড়ে বেড়ানোর বয়সে প্রায় জোর করে বিয়ে করে আনলেন। বিশাল এক নেতার ঘরের আদুরে, আহ্লাদী বউ হলাম। ও বাড়ি যেতে চাইলে যেতে দেননি। আপনার আশপাশেই পড়ে থাকতে বাধ্য করেছেন। আর তাতে আমার নারীমনের সবটুকু অনুভূতি আপনার ওপর আঁটকে রইল, অন্য কোথাও মনোযোগ যাবার সুযোগ পেল না। বিয়ের পর হাতে গুণে আপনার গন্ধ মিশে থাকা এই রুম থেকে বাইরে বেরিয়েছি।ʼʼ
রিমির স্বর থরথর করে কেঁপে উঠল, “আর কোথায় যাব আমি, হ্যাঁ? আমার গণ্ডি আপনি অবধি। এবার বলুন, সেই পুরুষটার কাছে এমন সব বিশ্বাস ভাঙা আঘাত পেতে আমার কেমন লেগেছে? আর কতটা শাস্তি বাকি আমার? পুতুল বানিয়ে রাখতে ওরকম ভালোবাসতেন? ঘরে আঁটকে দুনিয়ার থেকে আলাদা করে রেখে শুধু আপনার মাঝে বিলীন রাখতে এসব আয়োজন? ঠিক আছে, তা সফল হয়েছে। যে বয়সে মেয়েটা উশৃঙ্খল হয়ে ওঠে, আমি আপনার ঘরণী হয়েছি। সারাদিন পাক্কা গিন্নির মতো সংসার সামলানো আর দিনশেষে স্বামীর ঘরে ফেরার অপেক্ষা। আমার মাথায় এ ছাড়া আর কিছু রইলনা আর। সবটা আপনি, আপনার ঘর-সংসার, আপনার পাঞ্জাবীটা, গামছা, লুঙ্গি, পছন্দের খাবার, পছন্দের সাজ–কী পেলাম? দিনশেষে এক অমানুষ ক্ষমতালোভী কুকুর স্বভাবের পুরুষের জন্য আমার এতকিছু?ʼʼ
হামজা শুধু চেয়ে রইল চুপচাপ। রিমি বলল, “আপনি ঠিক। যতদিন না আরমিণ এ বাড়িতে পা রেখেছে, এসব যে আমি কী করছি, তা-ই জানতাম না। ও আমাকে তুলনা শিখিয়েছে। এসবের হিসেব কষার সূত্র শিখিয়েছে ওর ব্যবহার। কিন্তু ওর কোনো চেষ্টা ছিল না আমাকে শেখানোর। ওর চরিত্রটা আকর্ষণীয়। আমি নিজেই ওকে ফলো করতে লাগলাম। একটু একটু ধারণ করতে থাকলাম ওকে।
ও গোলামিকে ঘৃণা করে, ও যা করে সবের পেছনে একটাই চিন্তা—দিনশেষে যেন অনুভূতির অপচয় না হয়ে যায়। কারও কাছে নত না হয়ে যেতে হয়। আর কেউ যেন এইসব দূর্বল অনুভূতির নাম ধরে ক্ষমা না পেয়ে যায়। আজ যেমন আমি পারছি না–আপনাকে পর্যাপ্ত ঘৃণা করতে! কারণ আমি এক দূর্বল অনুভূতির জালে বন্দি। ও আমাকে স্বামীকে ভালোবাসতে নিষেধ করেনি, ও আমাকে কিছুই বলেনি কখনও। শুধু ওর চালচলনই আমাকে চিনিয়েছে কোন সীমাটা মানুষকে মানুষ আর অমানুষ হিসেবে ভাগ করে…ʼʼ
হামজা হঠাৎ-ই রিমির ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল। খানিক পর একটু আলগা করে বলল, “চুপ! আরমিণকে অথবা আরমিণের ধরণকে জয় সহ্য করতে পারে। আমি পারব না। ওর একফোঁটাও আমি তোমার মাঝে বরদাস্ত করতে পারি না। তুমি আমার বউ। আরমিণের সামান্য একটুও তোমার মাঝে থাকবে না।ʼʼ
-“তো বলছেন চলে এসেছে? তাহলে সেটা কি আপনার জন্য কষ্টকর?ʼʼ
হামজা দাঁতে দাঁত পিষল, “আমার জন্য যন্ত্রণাদায়ক। এই খেলায় ওকে জিততে দেয়ার ভুলটা আমি করব না, রিমি। আমার সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রু ওই মেয়েটা। তুমি বুঝতে পারছো না, ও কী খেলা খেলছে!ʼʼ
থম মেরে গেল হামজা। চুপ করে গেল আচমকা। দুই সেকেন্ড, থেমে রইল, কিছু ভাবলো। এরপর রিমির ঠোঁটে গাঢ় একটা চুমু খেলো। খুব হিংস্র চুমু। রিমির ওপর যেন কঠিন এক আক্রোশ প্রকাশ পেল।
খানিক বাদে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “একটা সত্যি কথা শুনবে রিমি?ʼʼ পেছন ফিরে রিমির দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমি যা করেছ আমার সঙ্গে, আর আমার থেকে তোমার এই মুখ ফিরিয়ে নেয়া আমাকে যে যন্ত্রণাটুকু দিচ্ছে, কসম তোমার জায়গায় অন্য যে কেউ থাকলে তার শরীরের প্রত্যেকটা হাড় ছড়িয়ে আলাদা আলাদা করে দাফন করতাম। কবর হতো ২০৬ টা। আফসোস, আমি জয়ের পর আরও একজনকে ধারণ করে বসেছি ভেতরে।ʼʼ
রিমি একসময় শুধায়, “আপনি যে বললেন—কী খেলা খেলছে, আরমিণ?ʼʼ
হামজা চুপচাপ জানালার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে অদ্ভুত স্বরে বলে, “কঠিন কিছু।ʼʼ
-“কেমন কঠিন?ʼʼ
-“ভয়ানক কঠিন। এর ফল আমি তাকে দিলে নিতে পারবে কিনা, তা নিয়ে বড় চিন্তা হচ্ছে আমার।ʼʼ
—
ওদের ওপর অত্যাচার বেড়েছে। রোজ তিনবেলা করে লোক আসছে বড়ঘরে। অন্তূ দেখল, “কিছু বড় বড় ইস্পাতের বীম ও লোহার খণ্ড সরানো হয়েছে।ʼʼ
জয় অন্তূকে দাঁড় করিয়ে রেখে পাশের কক্ষে যায়। ফিরে আসে পিস্তল হাতে। এগিয়ে গিয়ে বসে মুরসালীনের সামনে। অন্তূর দিকে মুরসালীন একবার তাকায়, তৎক্ষণাৎ চোখ সরায়।
জয় পিস্তলটা পাশে মেঝেতে রেখে মুরসালীনকে জিজ্ঞেস করে, “তোর চাচা কোথায়, মুরসালীন?ʼʼ
মুরসালীন তাকাল জয়ের দিকে, হেসে ফেলল, “এতদিন পরে একথা জিজ্ঞেস করছিস! আমি অধীর অপেক্ষায় ছিলাম তোর এই প্রশ্নের।ʼʼ
জয় বিনিময়ে একই হাসি হাসল, “তাড়া কীসের? এই যে কাতরানি, যন্ত্রণা, না খাওয়া, আঘাত…তোর ছোট্ট ছোট্ট আমানতগুলোর অসহায় আবদার, শুকনো মুখ, তৃষ্ণার্ত চাহনি! এসব দেখলি, মজা পেলি। এতে কোরে আর দু-একবারের বেশি জিজ্ঞেস করতে হবে না। দ্রুত জবাব পাব।ʼʼ
মুরসালীনের মুখ নরকের কূপের মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠল, চোখের মণি লালচে হয়ে উঠল আচমকা। তাকে সচরাচর খুব শান্ত দেখা যায়। আজ আচমকা জয় ও মুরসালীনের সম্মুখীন দৃশ্যটা দেখতে দুই আগ্নেয়-স্ফূলিঙ্গর সংগর্ষের মতো লাগল। দাঁতের মাড়ি চেপে মুরসালীন বলল, “আমার বাপকে মেরেছিস তুই। কিচ্ছু বলিনি।ʼʼ
-“বলিসনি?ʼʼ
-“তোকে কারা কোথায় ঘায়েল করে ছেড়ে দেয়, তার জিম্মা অন্যের ঘাঁড়ে চাপিয়ে হালকা হোস। তুই শালা ভুল বুঝেই শহীদ হয়ে যাবি।ʼʼ
জয় খানিকক্ষণ ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে মুরসালীনের দিকে। তারপর বলে, “আমার নামে একটা শহীদ মিনার তৈরি হলে শহীদ হতে আমার কোনো সমস্যা নেই।ʼʼ
-“আমার ভাইকে মেরেছিস তুই, জয়।ʼʼ
জয় ঘাঁড় নত করে বাহবা নেবার মতো ভঙ্গি করে বলে, “ওহ! নিজের হাতে। গলা কেটে দুই ভাগ করেছি।ʼʼ
মুরসালীনের চোখে রক্তের দানা বাঁধে, দু’পাশে মাথা ঝেড়ে প্রগাঢ় শ্বাস ফেলে, “কিন্তু আমাকে খুঁজতে আমার বোনকে যখন অপহরণ করলি, আমি কেন জানি নিশ্চিন্ত ছিলাম রে, জয়!ʼʼ
জয় ঠোঁট উল্টায়, “কী বাবদে?ʼʼ
মুরসালীন স্লান হাসে জয়ের চোখে চেয়ে, “তুই বেঁচে থাকতে আমার মুমতাহিণার গায়ে আঘাত লাগবে না বোধহয়! এই ভাবনা বাবদে। তুই যখন চলে এলি, মনে আছে–মুমতাহিণা আম্মুর কোলে? ক্যাঁ ক্যাঁ কোরে কাঁদতো সারাদিন খালি…ʼʼ মুরসালীনের কণ্ঠস্বর কেমন অস্তমিত হয়ে এলো, কেঁপে উঠল একটু, ঠোঁট উল্টে মলিন হাসল।
মুরসালীন ওপরের দিকে তাকায়। অন্তূ নিজের বুকের ভেতর এক কঠিন অস্থিরতাবোধ করল। সাধারণ কথাগুলো এত নিষ্ঠুর শুনতে লাগবে কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে শোয়ানো মুমতাহিণার লাশ চোখে ভাসছে। অন্তূ দীর্ঘ করে শ্বাস টানে। জয় নির্লিপ্ত মুখে মেঝের দিকে চেয়ে আছে।
মুরসালীন নিজেকে এক মুহুর্তের মাঝে সামলায়, “ওর লাশও দেখতে পাইনি। বিশ্বাস কর জয়, মুস্তাকিন ভাই থাকলে তোকে কেটে চিড়িয়াখানার পশু দিয়ে খাওয়াতো নিজের হাতে।ʼʼ
জয় মুখ তোলে, উপর-নিচ মাথা নাড়ে “আর তুই? তুই কিছু করবি না?ʼʼ
কিন্তু বলে না—মুমতাহিণাকে এনে গোডাউনে রেখে চারঘন্টা পর সে রাজধানীতে চলে গেছে। ফেরার আগেই মুমতাহিণার দেহ পলাশের ডেরায় পৌঁছেছে।
যেদিন মুমতাহিণার সঙ্গে মুরসালীনের শেষ দেখা হলো, মুরসালীন রাজধানীর উদ্দেশ্যে বেরোচ্ছিল। চুপিচুপি এসে মুরসালীনের পেছনে দাঁড়ায় মুমতাহিণা। বয়স ষোলোতেই রূপ ছিটকে এসেছে! পরনে লম্বা গোল জামা। ওড়না জড়ানো শরীরে, মাথায় ঘোমটা। ফর্সা টকটকে হাতে কালো লোম। ঘন পাপড়িওয়ালা চোখদুটো ঠিক বড় বড় মার্বেলের মতো। তিন ভাই-বোনের চেহারাই দেখতে লাগে ইরানি ইরানি।
মুরসালীন পেছন না ফিরে বলে, “কী?ʼʼ
মুমতাহিণা ওর দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলে। মুরসালীন গম্ভীর হয়, “থাপ্পড় খাবি? আমার ঘরে কী?ʼʼ
-“ভাইয়ু তুই ঢাকা যাচ্ছিস, ঠিক বলেছি?ʼʼ
-“না।ʼʼ
“মিথ্যা বলে বের হবি, রাস্তায় কুত্তার তাড়া খাবি, আবার ফিরে এই আমার কাছেই আসা লাগবে। মনে রাখিস, তোর তো বউ নেই, সেবার জন্য আমার কাছে ধর্না ধরতে হবে।
মাথায় একটা গাট্টা মারে মুরসালীন। মুমতাহিণা চেঁচিয়ে ডাকে, “আম্মা?ʼʼ
-“ছাগলের বাচ্চার মতো ম্যা ম্যা করিস ক্যান সবসময়?ʼʼ
মুমতাহিণা আস্তে কোরে বসে বিছানায়, চঞ্চলতা ভুলে নিভু নিভু স্বরে বলে, “বড় ভাইয়ার খোঁজ পাসনি রে ভাইয়ু?ʼʼ
সুন্দর পুতুলের মতো মুখটা মলিন হয়ে উঠেছে, তা জানে মুরসালীন। রাগ হয় মুরসালীনের। ওই মুখ দেখার সাহস নেই, মুরসালীন তাই তাকায় না। মুরসালীনের কাছে জবাব নেই, তাই কোনো কথাও বলে না। মুমতাহিণার বড় ভাইয়া আর নেই, তা বলার নয় মুমতাহিণাকে।
মুমতাহিণা চট করে হাসে, “এই শোন, ভাইয়ু!ʼʼ
মুরসালীন খেয়াল করে, মুমতাহিণা একদম মুস্তাকিনের মতো হয়েছে। আবেগ লুকোতে পেশাদার পটু। ভ্রু নাচায়, “কী?ʼʼ
মুমতাহিণা উঠে এসে ছোট ভাইয়ের পাশে দাঁড়ায়। ঠোঁট টিপে বলে, “আমার কী মনে হয় জানিস?ʼʼ
-“ইচ্ছে নেই জানার। দূরে থাক।ʼʼ
-“চুপ। বলছি শোন। খ্যাকখ্যাক করবি কেন আমার ওপর? আমি ছোট না?ʼʼ
মুরসালীন হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। এসব বাচ্চামি এড়ানো দুঃসাধ্য। ইচ্ছে করে, মুমতাহিণাকে বুকের সাথে মিশিয়ে ধরতে। ধরে না সে। নিচু হয়ে হাসে।
মুমতাহিণা কাধে কাধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আয়নায় মুরসালীনের চোখে তাকিয়ে বলে, “বড় ভাইয়া একটা মেয়ে ভাগিয়ে নিয়ে বিয়ে করে ফেলেছে। কিন্তু লাজুক লোক তো! আর আম্মার ভয়ে বাড়িতে আসতে পারছে না। বল, আমার আন্দাজ কেমন?ʼʼ
মুরসালীন রেগে ওঠে। বাড়িতে থাকলে এই মেয়ে সারাদিন বড় ভাইয়া বড় ভাইয়া করে কান খায়। মুরসালীনের বুকে আগুন জ্বলে, তা টের পায়? ধমকে ওঠে মুরসালীন, “বের হ আমার রুম থেকে। তোর প্যাঁচাল শুনতে ভাল্লাগছে না।ʼʼ
মুমতাহিণা অভিমান করে সরে দাঁড়ায়, যায় না। যতক্ষণ না মুরসালীন মানিয়ে নেবে, যাবে না। মুরসালীন আচমকা জিজ্ঞেস করে, “জয় আমিরকে মনে আছে তোর, মুমতু?ʼʼ
-“মনে থাকার কথা? কে লোকটা?ʼʼ
মুরসালীন প্রসঙ্গ এড়ায়, “কেন এসেছিস?ʼʼ
মুমতাহিণা বিশাল বিশাল ভরাট দুটো অক্ষিপল্লব মেলে তাকায়। মুরসালীন টের পায় বুকের ভেতর এক তিরতিরে ব্যথা! ওই চোখদুটোকে বড় ভয় মুরসালীনের। এখন আবার পানি জমছে। টলমল করছে। মুশকিল বড়।
মুমতাহিণা চোখের পানি ছাপিয়ে হাসে, “কয়দিনের মনে যাচ্ছিস রে?ʼʼ
-“তা জেনে কী?ʼʼ
-“হিসেব করব, কয়দিন বাড়িয়ে শান্তিতে থাকতে পারব।ʼʼ
মুরসালীন হাসে, “এবার আমিও তোর বড় ভাইয়ার মতো নিরুদ্দেশ হবো। কেমন হবে?ʼʼ
এবার আর বাঁধ মানে না চোখ। টুপ করে গাল বেয়ে যায় মুমতাহিণার। মুরসালীন দেখে তা। বুক মুচড়ে আসে তার। বাপহীন পুঁচকেটাকে মুস্তাকিন কলিজার সবগুলো ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে রাখতো। মুরসালীন তুলনামূলক রুক্ষ্ণ। তার সাথে ভালোবাসার চেয়ে ঝগড়া বেশি।
মুমতাহিণা হামলে পড়ে ভাইয়ের বুকে, “আসিস না আর। তুই না থাকলে সারাদিন আমাকে কেউ ধমকায় না, খাটায় না, সন্ধ্যার পর বাদাম কিনে এনে দেয় না, ঝগড়া করার লোক থাকে না, স্কুলে একা যেতে হয়। কত আরাম। তুই থাকলেই যত ঝামেলা।ʼʼ
মুরসালীন মাথায় হাত রাখলে তা ছিটকে সরিয়ে দেয়, “সরা হাত। হাত রাখছিস কেন আবার মাথায়?ʼʼ
মুমতাহিণার চেয়ে কমপক্ষে দশ বছরের ছোট। অথচ মানামানি নেই সেসব। চুপ করে থাকে দুজন। মুমতাহিণার ফুঁপানির মৃদু আওয়াজ মন ভরে শোনে মুরসালীন। বাড়িতে শুধু আম্মার সাথে একা থাকে। রাজধানীতে মুরসালীনের ঘুম হয় না তা ভেবে।
মুমতাহিণা খানিক বাদে আস্তে কোরে বলে, “বড় ভাইয়ার খোঁজে যাচ্ছিস, ভাইয়ু। তাই না?ʼʼ
মুরসালীন চোখ বোজে। গাঢ় শ্বাস নেয়। কণ্ঠনালি ঠেলে ডাহা মিথ্যা আশ্বাসটুকু বের করে, “হ্যাঁ। তোর ঘ্যানঘ্যানানি শুনতে শুনতে কানের পোকা মরে যাচ্ছে। এবার ইনশাআল্লাহ তোর বড় ভাইয়াকে নিয়ে আসব, যা।ʼ
-“তোকে দরকার নেই। শুধু বড় ভাইয়ার সঙ্গ চাই।ʼʼ
বের হবার সময় মুরসালীনের আম্মা মরিয়ম বেগম দোয়া-দরুদ পড়ে ফুঁক দেন ছেলের শরীরে। রাস্তায় আয়াতুল কুরসী, দরুদ শরীফ পাঠ করতে বলেন মনে মনে।
মুমতাহিণা ধমক দেয়, “শোন বেদুইন। নামাজ পড়বি ঠিকমতো। তোকে ভার্সিটিত পড়িয়ে কাফের বানিয়েছে, আম্মা। পোশাকের কী ছিরি! সাহেব হয়েছে।ʼʼ
মুরসালীন গাট্টা মারে মাথায় একটা।
বাঁশের চ্যাগারে ঘেরা বাড়ির সামনের পথটুকু পেরিয়ে যায় মুরসালীন। পেছন থেকে মুমতাহিণা মাথায় ওড়না তুলতে তুলতে দৌঁড়ে যায়, “এই শোন, ভাইয়ু! শোন, শোন।ʼʼ
মুরসালীন পেছন ফেরে। মুমতাহিণা মুখ নামিয়ে দাঁড়ায়। মুরসালীন হাসে, “কিছু লাগবে না তোর, তাই তো?ʼʼ
মুমতাহিণা চোখ তুলে হাসে। দুই ভাই-বোন একে অপরের চোখে তাকিয়ে সমানতালে হাসে। মুমতাহিণা মুরসালীনের হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরে রাখে। ভারী শ্বাস ফেলে দুজনই। কত কিছু বলতে চায় দুজন, বলা হয় না কারোরই। কেবল চুপচাপ চেয়ে থাকে।
এক সময় মুমতাহিণা হাসি সামলে বলে, “ফেরার পথে একটা ঢাকাই শাড়ি আনিস তো।ʼʼ
মরিয়ম বেগম পেছষ থেকে শাসন করেন, “খবরদার! ওসব কিচ্ছু না। শাড়ি পরা লাগবে ক্যান, হ্যাঁ? বেশি স্পর্ধা?ʼʼ
ধার্মিক পরিবার সৈয়দ পরিবার। সেখানে মেয়েদের বেলেহাজ হয়ে চলার চল নেই। মরিয়ম বেগম রাগ করেন।
মুরসালীন গম্ভীর হয়, “পারব না আনতে।ʼʼ
মুমতাহিণা হাসে, “তোর ঘাঁড় পারবে। যা বিদায় হ তো এবার। আর আসিস না তাড়াতাড়ি।ʼʼ
অন্তূ স্তব্ধ হয়ে শোনে সেসব। জয় ওভাবেই বসে আছে। কোনো হেলদোল নেই। না আছে মুখে অভিব্যক্তি। অন্তূর মনে হয়—জয় বুঝি লোহার খণ্ডগুলোরই এক টুকরো।
মুরসালীন হাসে, “ঢাকাই শাড়িটা এখনও আমার ফ্ল্যাটে পড়ে আছে। পড়ার মেয়েটা পালিয়েছে আমাকে রেখে। প্রথমে ভাই গেল তারপর বোনটাও। আমি একা আছি। মেরে ফেল আমায়। ও, আমার পরিবারে আর আছে আম্মা। তার খোঁজ চাই, জয়? সে ছাড়া আর কেউ নেই।ʼʼ
বাগানের রাস্তার পিছনের লোহার গেটে করাঘাতের হালকা আওয়াজ ভেসে আসছে। রাত বোধহয় দুটো পার। কেউ এসেছে! করাঘাতের আওয়াজটা কেমন যেন শোনাচ্ছে। গা ছমছম করে ওঠে। মৃদু হলদে আলোয় বিশাল ঘরটা গুমোট। কতগুলো দেহ ছড়িয়ে আছে। যেন জীর্ণ-শীর্ণ, ময়লা সাদা কাপড়ের স্তূপ।
চলবে…
#অবরুদ্ধ_নিশীথ
#তেজস্মিতা_মুর্তজা
৬৭. (বর্ধিতাংশ)
করাঘাত গাঢ় হচ্ছে। জয় উঠে যায়। পিস্তলটা পড়ে থাকে মেঝেতে। সেই ফাঁকে অন্তূ আব্দুল আহাদকে বলে, “কতদিন আগে আঁটক হয়েছ তোমরা, মনে আছে?ʼʼ
জবাবটা আব্দুল আহাদ দিতে পারে না। ওরা এতটাই দূর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে! এছাড়া ওদের সেই হিসেব নেই-ও!
মুরসালীন জবাব দিলো, “এখানে সময় আবদ্ধ। আর এই অবস্থায় দিন মনে রাখা অসম্ভব। তবে আমার একটা হিসেব আছে। মাস দেড়-দুয়েকের মতো হবে। কম-বেশি হতে পারে।ʼʼ
অন্তূ তাকায়। চোখাচোখি হলে দুজন চোখ নামায়। অন্তূ ঠোঁটে ঠোঁট গুজে নিয়ে আস্তে কোরে বলে, “মুরসালীন মহান! কয়েকদিন আগে ঘটনাক্রমে আমার আনসারী মোল্লার সঙ্গে কথা হয়েছে।ʼʼ
মুরসালীন ভ্রু কুঁচকে ফেলল, “আপনার সঙ্গে?ʼʼ
-“অবাক হচ্ছেন কেন?ʼʼ
মুরসালীন চোখ নামায়, “কী বলেছেন উনি?ʼʼ
-“জিন্নাহ আমির আপনাদের হাতে বন্দি।ʼʼ
-“এটা আনসারী ভাইজান বলেছেন?ʼʼ
-“আমি বলছি।ʼʼ
পাশ থেকে এমদাদ বলল, “এত বিশ্বাসের সাথে কীভাবে বলছেন?ʼʼ
অন্তূ আলতো হাসল, “আমার মনেহয় আমার আন্দাজশক্তি ভালো।ʼʼ
মুরসালীন জিজ্ঞেস করল, “আনসারী ভাই কী বলেছেন আপনাকে? তার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হলো কী করে?ʼʼ
-“আপনার অনুমতি পেলে উনি জিন্নাহ আমিরকে ছেড়ে দেবেন। তার বদলে যদি এটা নিশ্চিত হয় যে আপনাদের মুক্ত করে এরা, তবে এই লেনদেনটা করবেন উনি।ʼʼ
মুরসালীন সন্দিহান হলো, “আপনি তো এখানে আসার সুযোগ পান না। আজ যদি না আসতে পারতেন, আমাকে খবরটা দিতেন কীভাবে?ʼʼ
-“দিতে হতোই যেকোনোভাবে! আর সেজন্য একটা তামাশা করে হলেও আসতে হতো।ʼʼ
-“আমাদের ব্যবস্থা হবে ইনশাআল্লাহ। আর না হলেও দুঃখ নেই। আমি বেঁচে থাকা অথবা মৃত্যু কোনোটা নিয়েই আশাবাদী নই। আপনি কেন করছেন, কী করছেন, সেটা আর জানতে চাইলাম না। কিন্তু আপনি আমাদের জন্য নিজেকে বিপদে ফেলবেন না।ʼʼ
অন্তূ হাসল, “বিপদ আবার বিপদে পড়বে কী? বিপদ আমাকে এতই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে নিয়েছে, আমি নিজেই আজ স্বয়ং বিপদ হয়ে গেছি।ʼʼ
মুরসালীন একবার তাকাল অন্তূর দিকে। অন্তূ সন্দেহীন গলায় জিজ্ঞেস করে, “জিন্নাহ আমির কি বেঁচে আছে আপনাদের হেফাজতে?ʼʼ
জবাবটা দেবার সময় পেল না মুরসালীন। জয়ের সঙ্গে চারজন ঢুকল। আজ চয়ন নেই। দোলন সাহেব, বাপ্পী, কামরুল। সঙ্গে আছে রবিউল। পেশায় সে মেকার। আসলে দালাল, রাজনীতির দালাল। দোলন সাহেব অন্তূকে দেখে ভ্রু কুঁচকালেন। তা দেখল জয়। মেয়ে মানুষ কেন বারবার এইসব কারবারে থাকবে? আগের দিনও জয়ের বউকে এখানে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। জয়কে আস্তে কোরে বললেন, “তোমার স্ত্রী এখানে কী করছে, জয়? দৃষ্টিকটু লাগে ব্যাপারটা, বুঝেছ? তাকে এখানে আনা কেন?ʼʼ
জয় জবাব দিলো না।
বাপ্পী মণ্ডল ঢুকেই গজরাতে গজরাতে মুরসালীনের দিকে এগিয়ে যায়। ঢাকায় এক সম্মেলন ও মিছিলে ছাত্রদলের লাঠিঘাতে তার দুলাভাইয়ের মৃত্যু হয়। সে জানতে পেরেছে, সেই ছাত্রদলের লিডিংয়ে মুরসালীন ছিল। মুরসালীনকে বোঝা যায় না। সে যে আসলে কী চায়, কোন দলকে সমর্থন অথবা বিরুদ্ধাচারণ করে, অথবা করেই কিনা!
জয় এসে বসল আবার মুরসালীনের সামনে। দোলন সাহেব বললেন, “শেষ একটা চেষ্টা করব মুরসালীন? একটা স্টেটমেন্ট দেবে? নয়ত দায়িত্বটা সরাসরি আইনের হাতে হস্তান্তর করাই শ্রেয় হবে।ʼʼ
মুরসালীন হ্যাঁ-না কিচ্ছু বলল না। ওরা যে স্বীকারক্তি চাইছে, তা বেঁচে থাকতে দেবে না মুরসালীন।
দোলন সাহেব বললেন, “বাংলাদেশের রাজনীতিতে দল হিসেবে কোনটাকে সমর্থন করতে পছন্দ করবে তুমি?ʼʼ
অকপট জবাব দিলো মুরসালীন, “দলহীনতাকে। দল শব্দটাই বাংলাদেশের কাল, স্যার। কোনো দলই এই বাংলার জন্য শুধুই ধ্বংসাত্বক ছাড়া আর কিছু নয়। আর আমি তাই এমন এক দুর্যোগ চাই, যাতে করে বাংলাদেশের প্রধান, আলোচিত, বিশিষ্ট দলগুলো সমূলে উপড়ে যাক। তাদের কোনো চিহ্ন এই বাংলার মাটিতে না থাকুক। শুধু আমরা সাধারণ মানুষ থাকব। আমাদের দেশে আমরা থাকব। সেখানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হোক, অথবা কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা হবে, সাম্যবাদের জয়গান চলবে, সমাজতন্ত্রে ছায়ায় আমরা বাঙালি মানুষের মতো বেঁচে থাকতে পারব এক জীবন। আবার এতেও সেই একই হাল হবে কিনা বাংলার জানি না, তবু আশাবাদী আমি।ʼʼ
দোলন সাহেব অবাক হবার মতো অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন, “তুমি কমিউনিস্ট, মুরসালীন?ʼʼ
-“না তো।ʼʼ
দোলন সাহেব হাসলেন, “তুমি কি খেলছো, মুরসালীন?আমি তোমাকে বুঝতে পারি না।ʼʼ
-“আমিও না, স্যার। শুধু এটুকু জানি, ক্ষমতার লোভে সাধারণ মানুষ, শিশু, নারী, নিরপরাধীদের ওপর অপবাদ এবং তার জের ধরে এই যে মৃত্যুদণ্ড, কারাবরণের হিড়িক চলছে, এটা আমি নিতে পারি না। আর তা অন্তত কমাতে আমি সব দলকে হাতের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। অথচ কারও প্রতিই আমার অনুরাগ নেই। কারণ আমি জানি, দেশের জন্য কেউ-ই উপকারী নয়।ʼʼ
ধীরে মাথা নাড়লেন দোলন সাহেব, “বুঝলাম, বামপন্থী রাজনীতিকেও সাপোর্ট করো, তুমি। তোমাকে যদি ফাঁসি দেয়া হয়, তো আসলে কোন অপরাধে দেয়া হবে? প্রত্যেকটা অপরাধে একটা করে ফাঁসির রায় শুনবে তুমি। কিন্তু জীবন তোমার একটা।ʼʼ
-“এই সৌভাগ্যকে আমি আমার জীবনে স্বাগত জানাই, স্যার। আমি নিজেকে এতদিন কিছুই মনে করতাম না। কিন্তু এখন যখন দেখছি আমার কার্যক্রম বর্তমান শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর পীড়ার কারণ হয়েছে, এবং মৃত্যুদণ্ডের মতো বীরত্বপূর্ণ দণ্ডের শাস্তির দিকে এগোচ্ছি আমি, এবার মনে হচ্ছে আমি সত্যিই কিছু করতে পেরেছি। কারণ এই দুনিয়ায় অধিকাংশ মৃত্যুদণ্ড বীরদের এবং কারাবরণ কথা বলা পাখিদের হয়েছে।ʼʼ
দোলন সাহেব কিছু বলতে নিলে জয় উনাকে থামালেন, “চুপ চুপ চুপ চুপ! চুপ থাকেন। ওই যে কিছু ফ্যান আছে না, সুইচ দিলেই ঘ্যারঘ্যারঘ্যার করতে করতে চালু হয়, আপনাদের এই ফ্যাকফ্যাকানি কানে ওইরকমভাবে ঢুকতেছে। এত রাতে আমি এইখানে আসতে বলিনাই আপনাদের।ʼʼ
বাপ্পী এগিয়ে এসে মুরসালীনের মুখের ক্ষতর ওপর আঙুল চেপে ধরে মুখ উচিয়ে ধরে বলে, “শুয়োরের বাচ্চা। বল, বল আমার দুলাভাইরে তুই মারিস নাই?ʼʼ
-“বেশ কয়েকটা ক্ষ্যাপা শুয়োর বধ করেছি। কাউকেই পার্সোনালি চিনি না। হতেই পারে তার মধ্যে আপনার দুলাভাই থাকতে পারে।ʼʼ
-“তোর অত কথা শুনবার চাই নাই। যেটুকু জিগাইছি, জবাব দে।ʼʼ
-“এরকম আপনার মতো আরও অনেকের চোখের বিষ আমি। স্বয়ং দলীয় নেতাদের অবধি। কত ক্ষ্যাপা শুয়োরদের বিরুদ্ধে বলেছি, কার্যক্রম চালিয়েছি, আর্টিক্যাল লিখেছি, ছাত্রদের উৎসাহিত করেছি, মিছিল, মিটিং কত কী! অত মনে নেই।ʼʼ
বাপ্পী পশুর মতো গর্জে উঠে এমদাদ ও তৌফিককে দুটো লাত্থি মারল। থেতলা হয়ে গেল তৌফিকের মুখের চোয়াল। এমদাদের কান দিয়ে পুঁজ বা রক্তের মতো তরল বেরিয়ে এলো।
জয় চুপচাপ দেখে সেসব। পিস্তলটা তার বাম পাশে মেঝেতে পড়ে আছে। তার পাশে অন্তূ আব্দুল আহাদকে ধরে বসে আছে। তার নারীসুলভ দুটো দূর্বল হাতে ওদের রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা।
বাপ্পী মুরসালীনের মাথাটা সজোরে দেয়ালের সাথে বাড়ি মারে। মাথার ওপরের চটা ফেটে রক্ত চুইয়ে পড়ল। মুরসালীন অজ্ঞান হলো না ঠিকই, কিন্তু অচেতনের মতো পড়ে রইল।
অন্তূর হাতটা নিষপিষ করে ওঠে। চোখ বুজে ফেলে সে। তার দেহে এক ধরণের শিহরণ জাগছে। কীসব অদম্য ইচ্ছারা জাগছে।
জয় একটা লোহার খণ্ডের ওপর বসা ছিল। কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা বাপ্পীর পা বরাবর একটা লাত্থি মারল। বাপ্পী ধুপ করে মেঝের ওপর উল্টে পড়ে যায়, নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো, কনুই ছিঁলে গেল।
জয় মুরসালীনকে জিজ্ঞেস করে, “জিন্নাহ কি বেঁচে আছে মুরসালীন?ʼʼ
মুরসালীন জবাব দেয় না। বাপ্পী উঠে এসে আবারও মুরসালীনকে ধরে, জয়ের দিকে রক্তচোখে তাকিয়ে বলে, -“তুই কী করতেছিস? এইরকম মাগী মার্কা প্রশ্নে এই খানকির বাচ্চার মুখ খুলান যাইবো? লাগাইতে অইবো না? কুত্তাচোদাডারে মাইরা ফেলিস নাই ক্যাই আইজ পন্তক? আর তোরে আমি পরে দেখুমনে।ʼʼ
কামরুল টেনে হিঁচড়ে মুরসালীনের পাশ থেকে দুটো বাচ্চাকে উঠিয়ে নিলো। আদিম উল্লাসে মেতে উঠল ওরা জীবিত ছোট ছোট দেহগুলো নিয়ে। উদ্দেশ্য মুরসালীনকে উত্তেজিত এবং দূর্বল করা। মুরসালীন নিজের শরীরের ব্যথায় আরও শক্তিশালী হয়। কিন্তু বাচ্চদের আঘাতে ওকে অস্থির দেখা যায়।
জয় জিজ্ঞেস করে, “জিন্নাহকে কোথায় রেখেছিস তোরা? তোদের সংগঠনের আর সব কোথায়?ʼʼ
তার কণ্ঠস্বর শান্ত। কোনো তাড়া নেই, উত্তেজনা নেই। অন্তূর মনে হলো, সে নরকের কোনো এক বিভাগে বন্দিনী। মৃদু হলদেটে আলোয়, গুমটে গন্ধে এক নারকীয় অবস্থানে বসে থেকে অন্তূর ভেতরটা কেমন উল্টে-পাল্টে উঠছিল। তার মনে হচ্ছিল সে নিজের ভেতর থেকে হারাচ্ছে।
মুরসালীন বলে, “জিন্নাহকে ফেরত দেব, তার বদলে আমায় কী দিবি?ʼʼ
-“আগে ফেরত পাই সহি-সালামত! তারপর যদি মনে কয়, তো কিছু প্রতিদান পাবি। না দিলেও ঋণ নাই। ঋণ আছে তোর আমার কাছে। পুরানা ঋণ। যা তোরে আশিবার খুন করলেও পরিশোধ হবে না। কিন্তু খুন একবারই করতে পারব। অর্থাৎ তোর কাছে আমারই আরও ঊনআশিবার পাওনা থাকবে।ʼʼ
রক্তাক্ত মুখে হাসে মুরসালীন, “মঞ্জুর। যাইহোক, জিন্নাহকে ফেরত দিলে তুই ওদের ছেড়ে দিবি। এই কথায় একটা সওদা করতে পারি।
-“এরম কোনো প্রস্তাব দিছি আমি তোরে?ʼʼ
-“কেউ একটা দিলেই হয়। আমি দিলাম। আর তুই যা শোধের কথা বলছিস না? আমার ক্ষতির পরিমাপ করলে তোকে আশি দুই গুণো একশো ষাটবার খুন করলেও ঋণ থেকে যাবে। অথচ তোর জান একটাই। আমি বলব, তুই হিসেবে কাঁচা, চোখে অন্ধ আর বোঝার ভুলে ডুবে মরা মৃতদেহ।ʼʼ
-“ভুল বোঝার মধ্যে একটা আনন্দ আছে।ʼʼ
-“রাখ তোর পাগলের প্রলাপ।ʼʼ
-“জিন্নাহ কোথায় আছে?ʼʼ
মুরসালীন জবাব দিলো না।
জয় ধৈর্যহারা হয়ে উঠছিল। গাঢ় শ্বাস ফেলে বলল, “দুই-আড়াই বছর ধরে ধৈর্য ধরতেছি, মুরসালীন। আমার ধৈর্য ধরার রেকর্ডে এইটাই সবচাইতে দীর্ঘ। একটু কদর কর। খালি ক, জিন্নাহ কি বেঁচে আছে?ʼʼ
-“বেঁচে যদি না থাকে, তাহলে কী?
জয় হাসল, “তয় আর সময় অপচয় করবাম ক্যালা? অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আমি শয়তানের সম্বন্ধি। সময় কাজে লাগাই।ʼʼ
মুরসালীনের অভিব্যক্তি নির্লিপ্ত, সে গম্ভীর মুখে বলে, “আর ও যদি বেঁচে থাকে এবং ওকে যদি ফেরত দেই। তুই ওদের মুক্ত করাতে পারবি হামজা ভাইয়ের হাত থেকে?ʼʼ
মুরসালীনের পায়ের ক্ষততে ডান পা চেপে ধরল জয়। চামড়ার স্যান্ডেলের শক্ত নিচের তলার আঘাতে ক্ষত থেতলে উঠল। জয় অধৈর্য গলায় বলে, “যদি বেঁচে থাকে? না নাহ না! যদি না। ক, বাঁইচে আছে কি-নাই! এইটা আগে কনফার্ম হই! মরে গেলে এত নাটক মারাবো কোন দুঃখে? গলির মাথায় চাইপা ধইরা পাগলে চোদে নাই আমারে। জীবিত আছে না মেরে দিছিস, ওইডাই জানতে চাইতেছি খালি।ʼʼ
আবার জয় দ্রুত মাথা নাড়ল দু’দিকে, “তো চল। তোর কথাই রইল।ʼʼ নিজেকে বলে জয়, “সেকরিফাইজ, জয় সেকরিফাইজ! তুই না ভালো লোক।ʼʼ
মুরসালীনকে বলে, “জিন্নাহ বেঁচে থাকলে ওর বদলে তোর এই ছানাপোনাদের আজাদ করে দেব, যাহ! তোহ, জিন্নাহ বেঁচে আছে তো, না?ʼʼ
-“নেই।ʼʼ
জয় বাচ্চাদের মতো ভ্রু কুঁচকে তাকাল, ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, “নেই? বলিস কী রে? পরিশ্রম করলাম যে এত্ত! যাঌ, ভোদাই সেজে গেলাম রে আগেই না জিগাইয়া!ʼʼ
হতাশ শ্বাস ফেলল সে। মুরসালীন আর কিচ্ছু বলার সুযোগ পেল না।
কামরুল ও রবিউল জয়ের কাছে দুজন পূর্ণ মনোনয়ন পেয়ে গেছে, যেন এবার। এমদাদের অর্ধ-অচেতন দেহটাকে লাত্থিতে ভরিয়ে তুলল। জয় লৌহখণ্ডের ওপর বসে ঝুঁকে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে চুপচাপ।
কামরুলের হাতে বাচ্চারা ছিল কয়েকটা। ওদের গাল চেপে ধরল। শব্দ করে কেঁদে উঠল ছোট ছোট প্রাণগুলো। খালিপেট, পিপাসার্ত গলার কান্না গায়ে কাঁটা দেয় বড়।
দোলন সাহেব একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন শুধু জয়ের দিকে। মুরসালীনের দাঁত ভেঙে গেছে। ঠোঁটের কিনারা দিয়ে মাড়ি থেকে বেরোনো রক্ত ভেসে আসছে।
কামরুল এক বাচ্চাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো মেঝের ওপর। বয়স সাত-আট বছর হবে বোধহয়! ওইটুকু বাচ্চার ওপর কামরুলের বড় ক্ষোভ। ওরা রাজাকারদের উত্তরসূরী। বড় হয়ে সরকারবিরোধী হবে। ধর্মের কথা বলে। কামরুলের শান্তি হতো–ওদের টেনে টেনে ছিঁড়তে পারলে। তাতেও যদি মুরসালীন, এমদাদ, তৌফিক ওদের একটু যন্ত্রণা হয়!
বাচ্চাটার পড়ে গিয়ে ঠোঁট কাটলো, মুখের চামড়া ছিঁলে গেল। হাঁটুতে আঘাত পাওয়ায় উঠতে পারছিল না। হাঁটু চেপে ধরে কেঁদে ফেলল। অথচ আশ্চর্য, সেই কান্নার আওয়াজ নেই। আওয়াজ করে কাঁদছে না ভয়ে সে। মুখে-চোখে কাতর যন্ত্রণা, কিন্তু কান্নায় আওয়াজ নেই।
অন্তূ চুপচাপ দেখে সেসব। চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে তাকায়। তার হাতের মুঠোয় আব্দুল আহাদের জীর্ণ হাত। হাতদুটো কাঁপছে, অন্তূ টের পায়।
কামরুল হাতে বাচ্চাটিকে দুটো কঠিন থাপ্পর মারল। কচি মুখের চামড়ার নিচে রক্ত জমে যায়। মুরসালীন চোখ বুজে মুখ ফেরায়। কামরুলের খুব আনন্দ হয় এবার।
কিন্তু কামরুল এবার বিশাল ভুল করে ফেলল একটা।ওদের মাথা থেকে সাদা পাঁচকলির টুপিগুলো খুলে ছুঁড়ে মারল দূরে। অন্তূ দেখল। দীর্ঘশ্বাস টেনে নিলো ভেতরে
পকেট থেকে ছোট্ট একটা ছুরি করে রবিউল কামরুলের হাতে দেয়। দাঁত বের করে হাসে। দাঁতগুলো লাল, কালশিটে ধরণের স্পট পড়ে গেছে।
কামরুল খুব মজা পাচ্ছ। বাজারে গেলে বাচ্চারা খেলনার আবদার করলে, মা যখন খেলনা কিনে হাতে দেয়, সেইসময় বাচ্চাদের মুখে খেলনা পাবার তৃপ্তিখানা কামরুলের মুখে। এতকিছুর পরেও মুরসালীনের চুপ থাকাটাকে নির্লিপ্ততা মনে হচ্ছে। যা খুবই হতাশাজনক। কামরুলের উচিত এমন কিছু করা, যাতে মুরসালীনের চোখে-মুখে কাকুতি ফুটে ওঠে।
সে ছুরিখানা বাচ্চাটার গলায় ঠেকিয়ে চারদিকে সবার দিকে তাকিয়ে হাসল। উপস্থিত সব বাচ্চার মুখে এক করুণ আতঙ্ক দেখা দিলো। এটা খুবই মজার বিষয়। যেন তাকে অনুষ্ঠানে গান গাইতে বলা হয়েছে। মাইক হাতে সে একটু লজ্জা পাচ্ছে, সবার আরেকটু উৎসাহ চাচ্ছে। সবার মুখে সেই সুখ, শুধু দোলন সাহেব তখনও জয় আর মুরসালীনকে দেখছেন।
মুরসালীনকে ডাকে কামরুল, “ওই চেংরা! দেখ তো রে, আয় বাঁচায়ে নিয়া যা। মাগীর পুত, এইরম বন্দি থাইকাও ব্যবসা কইরবার চাও? এই জঙ্গিগুলানরে ছাইড়া দিলে আমাগোরে লোক ছাড়বা? ল, মুক্ত কইরা দিই তোর পাখিগুলারে।ʼʼ
এক ঝটকায় জয়ের পাশ থেকে পিস্তল তুলে নেয় অন্তূ। তাক করে ধরে কামরুলের দিকে। জয় চমকে তাকায়। সে অন্যমনস্ক ছিল।
অন্তূর চোখের মণি জ্বলছে। ধিকধিক করে জ্বলছে। বুকের ওঠানামা প্রবল। অন্তূ ট্রেগারে আঙুল রেখে কেমন মন্ত্রপুতের মতো গলায় বলে, “ছেড়ে দে। ছাড, ছাড়। তোর ছুরির চেয়ে পিস্তলের গুলি দ্রুত চলবে। আল্লাহর কসম এখানে চারটা লাশ ফেলব আমি। ছেড়ে দে ওকে।ʼʼ
জয় অন্তূর সামনে দাড়ায়, “ঘরওয়ালি! মাথা ঠান্ডা করো। অল ইজ ওয়েল। রিল্যাক্স, কিচ্ছু হয় নাই। মজার খেলা হচ্ছে, দেখো, এনজয় করো। আবার এইসব ডেঞ্জারাস চিন্তাভাবনা ক্যান?ʼʼ
অন্তূ জয়ের নাগাল পেরিয়ে কয়েক কদম পিছিয়ে যায়, পাগলের মতো দাঁতে দাঁত আঁটকে হিষ হিষ করে ওঠে, “জানোয়ারের বাচ্চা! তুই সরে যা সামনে থেকে। নয়ত আজ তোর বুকটা আগে ঝাঁজরা করে তারপর বাকি বুলেটগুলো ওদের জন্য খরচ করব।ʼʼ
অন্তূকে ক্ষ্যাপাটে বাঘিনীর মতো লাগছিল। অনেকটা মানসিক বিকারগ্রস্থ পাগলিনীর মতো। সাপের মতো হিষহিষ করে, বিক্ষিপ্ত নিঃশাসে বুক দুলছে।
জয় একটু থমকায়, ভ্রু কুঁচকায়, তবুও এই অবস্থায়ও হেসে ওঠে, “কিন্তু তোর তো হাত কাঁচা, শালির মেয়ে। গুলি জীবনেও নিশানায় লাগবে না, বড়জোর অ-জায়গায় লেগে আমার সবর্নাশ হবার চান্স আছে। আর নয়ত গোডাউনের ক্ষতি হবে। পিস্তল দে। আমার হাতে পিস্তল। খালি খালি মানুষ মেরে কী লাভ? তার চেয়ে বড় কথা, পিস্তলে তো বুলেট নাই।ʼʼ
অন্তূ কী করল! এক মুহুর্তের মাঝে পিস্তলের তাক ডানদিকে ঘুরিয়ে ঠিক দেয়াল বরাবর শ্যুট করল। পিচ্ছ্ করে একটা শব্দ হয়, সাইলেন্সরের বদৌলত। গুলি ছুটে গিয়ে ইটের গাঁথুনিতে ঠুকল। অন্তূ চরম এক ধাক্কা খায়। পিস্তলের পেছনের বেগের টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাবার মতো অবস্থা হয়। হাতটা ঝিনঝিন করছে তখনও। রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে গেছে যেন।
অন্তূ জয়ের দিকে তাকায়, “বুলেটহীন পিস্তল নিয়ে এখানে আসেননি আপনি।ʼʼ
গোটা ঘর নিস্তব্ধ। কেউ নিঃশ্বাসও ফেলছে না। সবার চোখ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসার জো। অন্তূর বিদ্রোহী শ্বাসের আওয়াজ কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে বদ্ধঘরে। কয়েক সেকেন্ডের মাঝে ঘটনাটা ঘটে গেল।
কামরুল ছুরিটা ভালোভাবে বাচ্চাটার গলায় ধরে সতর্ক করে অন্তূকে, “এই এই আপনে পিস্তল নামান। নইলে এক মুহুর্তের মইধ্যে গলাডা দুইভাগ কইরালামু, কইলাম। আর লাভ অইবো না। পিস্তল নামান, ছাইড়া দিতাছি।ʼʼ
-“প্রথমত তুই মরবি তো এমনিতেও, আর এই পিস্তলের গুলিতেই। দ্বিতীয়ত, তোর ছুরির চেয়ে আমার পিস্তলের গুলি দ্রুত চলবে। আর শুয়োরের বাচ্চা, তৃতীয়ত, যদি ওকে মারিসও, তার পরের মুহুর্তে হলেও তুইও মরবি। লাভ কী? ছেড়ে দে ওকে। ছাড়!ʼʼ
গোটা ঘরে প্রতিধ্বনিত হয় অন্তূর ‘ছাড়ʼ কথার গর্জনটা।জয় চুপচাপ তাকিয়ে দেখে এই অন্তূকে। মাথার ওড়না পড়ে গেছে, খেয়াল নেই। চুলের বড় খোঁপাটা অগোছালো। জয়ের যেন ভেতরে অস্বস্তি হয়। একসময় যে মেয়েটার মুখ দেখেনি কেউ কখনও, তাকে সে কোথায় নামিয়ে এনেছে! অন্তূর শরীর ঘেমে গেছে, চোখদুটো লাল। নাকের পাটা শক্ত। জয় অপেক্ষা করে অঘটনের। এইটুকুই বাকি ছিল–অস্ত্র হাতে ওঠেনি আজকের আগে অন্তূর হাতে। আজ সেটুকুও হয়ে গেল। বাকিটা সে জানে অন্তূকে।
আজ জয় ভাবে এক মুহুর্ত। সেদিন অন্তূ পলাশকে মারতে ছুরি হাতে নিতে পারেনি। পিছিয়ে এসে জয়কে ফিরিয়ে দিয়েছিল। কেন? সেদিন পেছনে এবং সাথে, পক্ষে দাঁড়ানো জয় ছিল, তাই? আপাতপক্ষে আজ জয় নেই তার সাথে। আজ সে একা। এই অবরুদ্ধ এক নিশীথে বড়ঘরে তার পক্ষে কেউ নেই, তাই কি সে একাই মোকাবেলা করতে যথেষ্ট, সচেষ্ট? তাহলে হিসেবটা কী দাঁড়াল? হামজা কি ঠিকই বলে?
নারী কারও অবলম্বনে যেমন দূর্বল, তেমনই একবার কেবল সে সেই অবলম্বিত খুঁটিহীন হয়ে পড়লে একাই সর্বোচ্চ ধ্বংসাত্বক! তাহলে কি নারীর তৈরি অনিষ্ট সঙ্গহীন নারী থেকেই সৃষ্টি হয়? নারী তার পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গ পেলে ভীষণ নারীসুলভ, একা হয়ে পড়লে অসীম সর্বনাশা!
কামরুলের মুখ শুকিয়ে যায়। বাচ্চাটাকে ছাড়তে চাইলেও ছাড়তে পারে না। কেউ অন্তূকে গিয়ে ধরতেও পারে না।মাঝখানে জয় আমির দাঁড়িয়ে।
কামরুলের মনে হয় ছেলেটাকে বাঁচানোর লক্ষ্যে জয় আমিরের বউ তাকে গুলি করবে না। এই আশায় কামরুল একটা ভুল করল— সে ছুরিটাকে শক্ত করে চাপল বাচ্চার গলায়। কচি চামড়ায় চিড় লাগে ছুরির ধারের। বাচ্চাটা কেমন করুণ সুরে মিনতি করে কেঁদে ওঠে হু হু করে।
আবারও ভোঁতা গুলি চলার আওয়াজ। গুলিটা লাগে না কামরুলের গায়ে। ডান হাতের বাহুর আড়াই ইঞ্চি ফাঁক গলিয়ে পেছনে এক লৌহখণ্ডে ঠেকে। কিন্তু পরমুহুর্তেই আবারও। কামরুলের নসিব খারাপ। তার মস্তিষ্ক তাকে সরে যাবার নির্দেশ দেবার আগেই পরের গুলিটা তার বক্ষপিঞ্জরের নিচে একদম কিনারায় লাগল। অন্তূর হাত খুবই কাঁচা। আর দুই ইঞ্চি হলেই এটাও মিস যেত। গেল না।
কামরুল ধপ করে পড়ে গেল মেঝেতে। কিছুক্ষণ জ্ঞানও রইল। রক্তের ঝিরঝিরে স্রোত নামলো মেঝেতে। গলাকাটা মুরগীর মতো ছটফট করল কিছুক্ষণ দেহটা। আর বেশিক্ষণ চেতনা রাখতে পারল না কামরুলর দেহ।
পরের দেহটা রবিউলের। আলগোছে পড়ে গেল। বিকট আওয়াজ বের হলো মুখ দিয়ে। তারপর আরেকটা গুলি চলল। সেটা শূন্যে লাগল। কিন্ত পরের গুলিটা বাপ্পী মণ্ডলের ঠ্যাঙ ফুঁড়ে চলে যায়। বাপ্পী গা শিউরে ওঠা স্বরে কোঁকিয়ে উঠে বসে পড়ে। ঠ্যাংয়ের হাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট এপার-ওপার হয়ে। ফাঁক হয়ে গেছে হাড়ের জোড়াইতে। তার আর্তনাদ কঠিন হলো। কানে সহ্য করা যাচ্ছিল না।
অন্তূর হাত অবশ হয়ে আসে। পিস্তলটা পড়ে যায় হাত থেকে। হাতে আর জোর নেই, হাত নাড়ানোর শক্তি নেই। স্নায়ু কাজ করছে না দুই হাতের। ঘরটা নিস্তব্ধ। তিনটা দেহ লুটিয়ে আছে মেঝেতে। বাপ্পী তখনও চেতনায় আছে, করুণ আর্তনাদে ঘরটা নরকের কক্ষ হয়ে উঠল। দোলন সাহেব চুপচাপ বসে রইলেন। খুবই নাটকীয় দৃশ্য, ট্র্যাজেডি নাটক যেন। অথচ লোকে জানে না জীবনের চেয়ে বেশি নাটকীয়তা নাটকে থাকে না।
জয় আস্তে কোরে বসে আবার লোহার খণ্ডের ওপর। মুরসালীন চোখ বুজে হেলান দেয় দেয়ালের সাথে। তার শরীর ঝিমিয়ে আসছে। জয়কেও দেখতে ক্লান্ত লাগে। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে ঝিম ধরে সে।
চলবে…
#অবরুদ্ধ_নিশীথ
#তেজস্মিতা_মুর্তজা
৬৮. (প্রথমাংশ)
○
চারদিন টানা বৃষ্টি। ঝুম ঝুম করে বৃষ্টি হচ্ছে। পথঘাট কাঁদায় মাখা। করতোয়া নদীর পানি উঠে এসে দিনাজপুরে বন্যা আসবে এবার বুঝি! দেশের দুর্যোগের সাথে প্রকৃতির দুর্যোগ যোগ হলে জমে যাবে দুর্যোগের খেলাটা।
বৃষ্টির ছিটা আসছে। মুর্শিদা আটা মাখা হাতে জানালাটা আঁটকে দিলেন। জয়নব লাফিয়ে উঠল, “আম্মা এইরকম কইরো না তো। বইয়ের এমন এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আছি, এই সময়ই জানালা আটকাইতে হইলো তোমার?ʼʼ
-“চুপ্প! থাপড়াইয়ে দাঁত ফেলে দেব। ধিঙি মেয়ে। এই তোর বুদ্ধিসুদ্ধি হবি না?ʼʼ
-“বুদ্ধি তো আছেই আমার।ʼʼ
-“বুদ্ধির চোটে আমার ঘরবাড়ি ভরে আছে। মুখে মুখে তর্ক? আটা হাতে করে জানালা আটকাইতে আইছি, আর তুমি এইখানে বসে থাকার পরেও হুশ হয় না? বইয়ে কী পড়িস সারাদিন? দ্যাশ জাহান্নাম হয়ে গেছে, আর… তুই বইয়ে কি দেখিস?ʼʼ
জয়নব উঠে বসল। আর তর্ক করল না। মেঘের জন্য দুপুরটাকে বিকেলের মতো লাগছে। জানালা আটকে দেওয়ায় ঘর পুরো অন্ধকার হয়ে গেল।
তার শাড়িটা ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু বাজারের সব দোকান ছাই হয়ে গেছে। মানুষের পেটে ভাত নেই, শাড়ি কী জিনিস!
আপাতত বইটা রেখে দিলো। আম্মা গেলে আবার নিয়ে বসা যাবে। কিন্তু মুর্শিদা গেলেন না। উনি বসলেন জয়নবের পাশে। মেয়ের চুল খুলে এলিয়ে দিলেন পিঠে।
-“আম্মা তোমার হাতে আটা। আটা লাগাইয়ো না চুলে।ʼʼ
-“শুকায়ে গেছে আটা। চুলে লাগবে নাকি?ʼʼ
বিলি কেটে দিতে লাগলেন চুলে। জয়নব ঘাঁড় পেছনে হেলিয়ে বসে রইল। বিশাল বিশাল চুল তার। নারকেলের তেল প্রায় আধপোয়া করে একেবারেই লাগে তার চুলে। জয়নবের বয়স এখন আঠারো। তার আকদ হয়ে আছে দুই বছর হলো। কিন্তু এই নারকীয় পরিস্থিতিতে জলিল আমির অনুষ্ঠান সারতে পারছিলেন না। আমির বাড়ির মেয়ের বিয়ে পানসে ভাবে দেয়া যায় না। গাঁয়ের লোক ওই দুটো দিন আমির বাড়িতে পেট ভরে খাবার হকদার।
জাভেদ জয়নবের এক বছরের ছোট। জামিল আর জয়নাল জমজ। তাদের ছোট জেবা। তার বয়স তেরো। সব পিঠাপিঠি। জামিল ঘুমাচ্ছে এই অসময়। জেবাও গিয়ে মেজো ভাইয়ের পাশে শুয়ে পড়েছে। সারারাত চিন্তায় ঘুম আসার জো নেই।
মুর্শিদা কেমন উদাস স্বরে বললেন, “আমাদের মনেহয় আমির নিবাস ছেড়ে দেওয়া লাগবে রে, জয়নব!ʼʼ
জয়নব একবার তাকায় মায়ের দিকে। এরপর ঘরে বাঁধানো পঞ্জিকার দিকে তাকায়। আজ বঙ্গাব্দ ১৩৭৮ এর বৈশাখের ১৩ তারিখ। খ্রিস্টাব্দ ১৯৭১ এর ২৬-ই এপ্রিল।
-“জাভেদরে ক্যান পাঠাইলা, আম্মা? আব্বা তো বলছিল, সুযোগ পাইলে নিজেই আসবে দেখা করতে।ʼʼ
ধুক করে উঠল মুর্শিদার বুকটা। তিনি ভুলে থাকতে চাইছেন সব। বললেন, “বলবি না তোর বাপের কথা। মরণের পথে ভাসায়ে রেখে উনি গেছেন যুদ্ধ করতে।ʼʼ
সন্ধ্যার পর জয়নাল এলো ভিজতে ভিজতে, “আম্মা। কিছু খাবার-দাবার আছে নাকি?ʼʼ
তার সাথে তিনজন জোয়ান জোয়ান ব্যাটাছেলে। মুর্শিদা আৎকে উঠে শুধান, “এরা কারা রে, জয়নাল? ক্যান আনছিস বাসায় তুলে? তুই কি পাগল হইছিস? ক্যান আসছে ওরা?ʼʼ
-“আম্মা, বিপ্লবী ওরা, বিপ্লবী। আমারে বলছে, বন্দুক চালাইতে দিবে, শেখাবে। কিন্তু ওরা কয়দিন কিছু খায় নাই। বন্দুক চালাইতে ম্যালা শক্তি লাগে, আম্মা। আগে সবাইরে কিছু খাইতে দ্যান।ʼʼ
মুর্শিদা কান মলে ধরলেন জয়নালের, “জানোয়ার। বন্দুক চালানো শিখে কী করবি? তোর বাপ-চাচারা ওইসব জানে, আজ আমারে সবাইরে বাণের জলের ভাসায়ে গেছে মিলিটারি মারতে, তোর বড় ভাই গেছে, আবার তুই..ʼʼ
-“আম্মা ছাড়েন ছাড়েন। ও আম্মা, শোনেন না!ʼʼ উত্তেজনায় জয়নালের গলা ধরে এলো, “ওরা বলতেছে আব্বা আর ভাইরে নাকি আটকায়ে রাখছে শয়তানরা। এরা আমারে সাহায্য করবে দূইজনরে ছাড়ায়ে আনতে। আম্মা, আব্বারে ছাড়ায়ে আনতে আমারে বন্দুক চালানো শেখাই লাগবে। দ্যান খাইতে। জলদি দ্যান। উত্তেজনায় কথা জড়াচ্ছিল জয়নালের।ʼʼ
মুর্শিদার হাত-পা কাঁপতে লাগল। তিনি হায় হায় করা শুরু করলেন। তার শরীর অবশ লাগছে। যে ভয় তিনি পাচ্ছিলেন, তা ঘটে গেছে। বন্দি হয়ে গেছে তার স্বামী ছেলে।
জয়নব জেবাকে ডেকে তুলল। জেবা হুড়মুড়িয়ে উঠে বলে, “কী হইছে আপা? কী হইছে? মিলিটারি আসছে? আগুন দিছে বাড়িতে?ʼʼ
“চুপ। চুপ কর। এই নে তোয়ালে। দৌড়ে গিয়ে তোর খালেদ ভাইরে ডেকে আনবি।ʼʼ
ঠোঁট চেপে হেসে উঠল জেবা, “ক্যান আপা? খালেদ ভাইরে খুব দেখতে মন চাইতেছে নাকি?ʼʼ
-“এক চড় মারব, বেয়াদব। যা বলছি কর।ʼʼ
জেবা তোয়ালে মাথায় দিয়ে সদর দরজার বারান্দায় উঠল। হ্যারিকেনের আলো ধরল জয়নব, “জলদি যা না রে।ʼʼ
-“যাচ্ছি যাচ্ছি। এত জলদি কী? না দেখে থাকতে পারো না?ʼʼ
-“খুব পেকেছিস? এমন মারব না!ʼʼ
একবার পেছন ফিরে দুষ্টু হাসে জেবা বোনের দিকে চেয়ে। সন্ধ্যার আঁধারে বেরিয়ে যায় বৃষ্টির ভেতর হবু দুলাভাইকে ডাকতে। আংটি বদল হয়ে আছে জয়নব আপার খালেদ ভাইয়ের সাথে। খালেদ ভাইটা খুব ভালো।
মুর্শিদার হাত চলছে না। তিনি জয়নবকে বললেন, “তোর ছোট চাচি আর দাদিরে ডাক তো। আমার কেমন ভয় ভয় করতেছে। ওই লোকগুলারে খাইতে দিক ওরা এসে।ʼʼ
লোকগুলোকে জয়নব খেতে দিলো। লজ্জায় হাত পা ভেঙে আসছে তার। ভয়ও করছে। জেবা নিশ্চয়ই গিয়ে গল্প জুড়েছে খালেদের বোনের সাথে। জয়নব ভেবে রাখল, ফিরলে পিঠের ওপর দুম দুম করে দুটো কিল বসাবে।
তিনজন খেলো। এরপর জয়নালকে নিয়ে চলে গেল জলিল আমির ও জাভেদের খোঁজে। বাপ-ভাইকে আঁটকে রাখা হয়েছে। নিশ্চয়ই অত্যাচার করা হচ্ছে! জয়নালের শরীরের রক্ত টগবগ করছে। জাভেদ ভাই আর আব্বার গায়ের সবটুকু যন্ত্রণা সে ওই জানোয়ার মিলিটারিদের দেবে। পণ করল মনে মনে। ওদের হাড্ডি ভেঙে এনে আমির বাড়ির ফটকে ঝোলাবে সে।
যাবার আগে একবার দৌড়ে জয়নবের কাছে এলো, “আপা, আমি যাচ্ছি। রামদা-টা বের করে দে তো। জলদি দে।ʼʼ
জয়নব অসহায়ের মতো বলে, “তুই-ও যাচ্ছিস? বাড়িতে কে থাকবে রে?ʼʼ
জয়নালের চোখে অগ্নিঝরা উত্তেজনা, সে বলল, “খালেদ ভাই আসতেছে তো। শোন আপা, পিছু পিছু আয়। ফটক আটকে যা। কণ্ঠ না চিনলে খুলবি না। বাড়িতে আগুন লাগানোর ভয় দেখাইলেও না, খবরদার। আব্বা, চাচারা বিপ্লব করছে। আমাদের বিপদ কিন্তু বেশি। আব্বা, চাচার খোঁজে আসবে ওরা।ʼʼ
জয়নব একবার পিছু ডাকে। জয়নাল বিরক্ত হয়, “সময় আছে নাকি? আবার ডাকিস ক্যান? ফিরে আসতেছিই তো আমি।ʼʼ
ঝারি মারল, অথচ পারল না যেতে। আবার ফিরে আসলো, “কী হইছে?ʼʼ
জয়নব কিছু বলে না, শুধু তাকিয়ে থাকে জলন্ত চোখে, জয়নালের গালে হাত বোলায়, দৃঢ় স্বরে বলে, “আব্বা আর জাভেদরে না নিয়ে ফিরবি না। দরকার পড়লে ওই পশুগুলার বুক ঝাজরা করে ফেলবি। যা, জলদি যা জয়নাল। যদি তোর শরীরে আঘাত লাগে, তার দ্বিগুন দিয়ে আসবি। জয় বাংলা।ʼʼ
জয়নালের বুক ফুলে ওঠে, দৃঢ়তার হাসি হেসে বোনের দিকে চেয়ে হাত মুঠো করে ধরে মাথার ওপর তুলে বলে, “জয় বাংলা। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।ʼʼ
মুর্শিদাকে বলে, “আম্মা চিন্তা কইরো না। কোন শুয়োরের বাচ্চা আব্বারে ধরছে, দেখব আমি। আমি আব্বা আর ভাইরে না নিয়ে ফিরব না। ইনশাআল্লাহ।ʼʼ
মুর্শিদা কপালে একটা চুমু খেয়ে বললেন, “আমার বুক খালি করিস না রে জয়নাল। আমি তোরে হাশরে বাঁধাবো বলে দিলাম। আমার জয়নালরে ফিরায়ে নিয়ে আসবি আমার কাছে, কথা দিয়ে যা।ʼʼ
লুঙ্গিতে কাছা মারতে মারতে অন্ধকারে বেরিয়ে যায় জয়নাল আমির অচেনা লোকগুলোর সাথে।
মাঝরাত হয়। খালেদ আসেনি। জেবাও ফেরেনি। জয়নাল অথবা জলিল আমির বা জাভেদ কেউ আসেনি। জয়নব নামাজ পড়ে আম্মার সাথে। দাদির ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে। বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে ছোটচাচির এই ঘরে আসার কথা। জামিল শুধু পায়চারী করছে। মুর্শিদা জোর করে জামিলকে তিনটে রুটি খেতে দিলেন। কোনোমতো ঠেকিয়ে রেখেছেন ওকে বাইরে যাওয়া থেকে। তারপর থেকে ফুঁসছে, ছটফট করছে ঘরের ভেতর।
গোটা পাড়া প্রায় খালি হয়ে গেছে। যে যার মতো নিরাপদের খোঁজে গেছে। খবর এসেছিল দিনাজপুরের এদিকে মিলিটারি হামলা হবে দু একদিনের মাঝেই।
শুনশান চারদিক। শুধু বৃষ্টির শব্দ। অবরুদ্ধ এক দুর্যোগের রাত। পৃথিবীর কোথাও যেন প্রাণ নেই, আলো নেই, আছে শুধু বর্বরদের ভারী বুটের গটগট আওয়াজ আর হাতের অস্ত্র থেকে ছুটে যাওয়া বুলেটের ঝংকারধ্বনি। ঝরছে রক্তের বৃষ্টি, লাল টকটকে বৃষ্টির পানির দানা ঝমঝম করে ঝরছে। সেই ঝমঝম রব ছাপিয়েও যেন কানে ছুটে আসে মানুষের হাহাকার, আর্তনাদ, গুলির আওয়াজ আর নিঃশব্দ নৃশংসতার ভোঁতা গোঙানি।
আমির নিবাসের ফটকে বিকট আওয়াজ হলো। ফটকটা কি কেউ ভেঙে ফেলল? মুর্শিদা কাঁদছেন। কিন্তু মুখটা শক্ত। সময় যত যাচ্ছে, বুকের উত্তাপ বাড়ছে। তার ছেলেরা কেন বাড়ি ফেরেনি। স্বামী কেন এসে দরজা খটখটায়নি? বুকের ভেতর আগুন জ্বলছে।
জয়নব নিঃশ্বাস আঁটকে থাকল ক্ষণকাল। এরপর দৌড়ে বড় বারান্দা গলি পেরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। দুটো বটি আর লোহার শিক নিলো। ফিরতে গিয়ে আবার ঘুরে পাটার ওপর থেকে শিলটা নিয়ে ঘরে এলো। মায়ের হাতে ধরিয়ে দিলো শিলটা। নিজের হাতে রাখল বটি, অপর হাতে শিক।
শব্দ শুনে জামিল খাওয়া ছেড়ে উঠে গেছে। এক দৌড়ে দোতলার সিড়ি ভেঙে উঠোনের কোণ থেকে শাবল তুলে নিলো সে। ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছেকিন্তু কেউ তো নেই! অন্ধকারে চোখ ঘোলা। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মাঝেমাঝে। জামিল ফটকের সামনের দিকে গেল। আমির নিবাসের লোহার ফটক গাছের গুড়ি দিয়ে ভাঙা হয়েছে। দু ভাগ হয়ে আছে দু’দিকে।
জয়নব দোতলার বারান্দায় দাঁড়ায়। অস্থির হাতে কোমড়ে শাড়ির আচল বাঁধে। জামিলকে দেখার চেষ্টা করে। খট করে আওয়াজ ভেসে এলো। জয়নব সতর্ক হয়। কিন্তু এরপর কিছুক্ষণ নিষ্ঠুর স্তব্ধতা। তা ভাঙল ছোটচাচির প্রকৃতি-চেড়া চিৎকার দিয়ে। জয়নবের শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। এক দৌড়ে নিচে নেমে সদরঘরের বাইরে পা বাড়ায়। মুর্শিদা পিছু নিলেন।
ছোটচাচির ঘর সদর ঘরের পরে পাকা উঠান পেরিয়ে ছোট বাংলোতে। তার দরজা আটকানো। ছোটচাচি পাগলের মতো মিনতি করছেন কারও কাছে। দুটো থাপ্পরও খেলেন বোধহয়।
জামিল তখন বিশাল শাবল নিয়ে এসে দাঁড়াল। শরীরে যেন কিছু ভর করেছে তার। শাবলের কয়েক আঘাতে শাল কাঠের দরজা ভেঙে খণ্ড-খণ্ড হয়ে গেল। গা কেঁপে ওঠা দৃশ্য।
কিন্তু জয়নবের গা কাঁপল। পরমূহুর্তে পা তার পরপরই হাত চলল। ছোটচাচির শরীরের ওপর চেপে থাকা দুটো জানোয়ারকে জয়নব বটির দুই কোপ মারল। একজনের মাথা আলাদা হয়ে ঝুলে পড়ল ঘাঁড়ের সাথে, আরেকজনের কাধ থেকে ডান হাতটা আলাদা হয়ে গেল। ছোটচাচির নগ্ন শরীর। ব্লাউজের ছোট্ট এক টুকরো হাতার কাছে দেখা যাচ্ছে কেবল। পেটিকোটটা ছিড়ে খণ্ড খণ্ড। শরীরে আর কিছু নেই।
জামিল মুখে হাত চেপে নগ্ন চাচির ওপর থেকে নজর ফিরিয়ে শাবল শক্ত করে ধরে। পশু দুটোর ওপর শাবল চালায় দক্ষ হাতে। মাঠে মাটি কুপিয়ে অভ্যস্ত হাত জামিল আমিরের। মাটির মতোই যত্ন করে কুপিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে দেহদুটো।
মুর্শিদা ডুকরে উঠলেন। ছোটচাচির দুধের বাচ্চা মাসুমকে আঁছড়ে ফেলা হয়েছে। তখনই বোধহয় ছোটচাচি চিৎকারটা অত জোরে করেছেন, যে পুরো বাড়িতে আওয়াজ গেছে। মেঝেতে তার রক্তাক্ত দেহটা পড়ে আছে। জয়নব একটানে বিছানার চাদর তুলে ছোটচাচির শরীরের ওপর বিছিয়ে দেয়। চাচি বোধহয় জ্ঞান হারালেন। কিন্তু দাদি কই?
আর্তনাদের সময় পাওয়া গেল না। দোতলায় সারি সারি পায়ের আওয়াজ। ব্যাপারটার পরিস্কার হলো এবার। ফটক ভেঙে ঢুকে একদল ছোটচাচির কাছে এসেছে। আর পেছনের রাস্তা দিয়ে আরেক দল দোতলায় উঠে অন্দরে ঢুকে পড়েছে। কাউকে দোতলার অন্দরে না পেয়ে নেমে আসছে।
জামিল চিৎকার করে বলে, “আপা, আগে আসিস না। ওখানেই থাক।ʼʼ
মুর্শিদা ছোট জা-কে রেখে শাশুড়িকে খুঁজলেন। অন্ধকার। হারিকেনটা পড়ে ভেঙে গেছে।
ওরা মোট সাতজন। জামিল দুটোকে আঘাত করতে পারল। মরল না একটাও। এরপর তাকে ধরে ফেলা হলো। শাবলটা কেড়ে নেয়া হলো আগে। প্রথম ছুরির আঘাতটা জামিলের মেরুদণ্ডের ডান পাশে লাগল। জয়নব বটি নিয়ে এগিয়ে এসে কোপটা ঠিক ছুরিওয়ালার হাতের ওপর বসায়। হাতটা কেটে পড়ে গেল না। ঝুলে রইল চামড়ার সাথে।
এরপর! তিনজনের হাতে বন্দি হলো জয়নব। তার সামনে জামিলের দেহটাকে ছিন্নভিন্ন করা হলো। মুর্শিদার তলপেটে একটা লাত্থি মারা হলে মুর্শিদা চিৎকার করে লুটিয়ে পড়লেন মেঝেতে।
জামিল শেষবার আম্মাকে ডাকল কয়েকবার। আম্মা হুশ হারিয়েছে। কাঁদার সুযোগটাও পেল না আম্মা জামিলের জন্য। জয়নব গলা চিড়ে কাঁদছিল। জামিল আর নড়ছে না। বৃষ্টির ছিটে আসা পানির সাথে ওর গরম রক্ত তিরতির করে ধুয়ে চলে যাচ্ছে। জামিল শুয়ে আছে।
দুজন জয়নবকে চেপে ধরে রাখল। দুজন উঠে গেল আবারও দোতলায়। জয়নব নিচে দাঁড়িয়ে শুনতে পায়, লোহার বাক্স ভাঙা হচ্ছে। লুটপাট হচ্ছে আমির নিবাস।
জয়নব তখনও একবার ফটকের পানে চায়। আব্বা আসবে না? জাভেদ কোথায়? বাঘটা এখন থাকলে কী করতো এদের? খালিদ এলো না। জয়নবের অভিমান হয়। লোকটার সাথে দেখা হলো না জয়নবের। জয়নব কি আর ফিরবে আমির নিবাসে? ফেরার কথা তো নেই! লোকটার সাথে দেখাই হলো না!
চলবে…
#অবরুদ্ধ_নিশীথ
#তেজস্মিতা_মুর্তজা
৬৮.(বর্ধিতাংশ )
রাত বোধহয় তিনটা বাজছিল। বৃষ্টি থামেনি। ভিজতে ভিজতে এসে দাঁড়ালেন জলিল আমির ফটকের সামনে। ফটক ভাঙা। সঙ্গে সঙ্গে কোমড় থেকে রাইফেলটা বের করে রি-লোড করে নিয়ে শক্ত করে জাভেদের হাত চেপে ধরে ভেতরে ঢুকলেন। কেউ কাঁদছে গুনগুন করে।
সেই রাতে তিনি বৃদ্ধা মা ও ছোট ভাইয়ের শিশু ছেলে ও স্ত্রীর লাশ পেলেন। বড় বারান্দায় সন্তানের লাশ পড়ে ছিল। জামিল আমিরের লাশ আগে আগে জাভেদ দেখেছিল।
তিনি জানতে পারলেন, বাড়িতে তাদের মিছেমিছি আঁটক হবার গল্প শুনিয়ে তার সন্তান ও স্ত্রীদেরকে ফাঁসানো হয়েছে একটি পরিকল্পিত চক্রে। তাঁরা দুজন ঘন্টাখানেক আগেও ফেরার পথে দুটো মিলিটারীর আস্তানায় কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে এলেন।
জয়নালকে ওরা নিয়ে গেছে। জয়নবকে তারপর। আমির নিবাসে লুটপাট হয়েছে। জেবাও আর খালেদকে নিয়ে ফেরেনি।
জাভেদের শরীরে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে বৃষ্টির পানি তার বুককে ঠান্ডা না করে বরং উত্তপ্ত করছে। দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। জামিলের রক্ত বৃষ্টির পানির সাথে নালির পানির মতো ভেসে ভেসে উঠোনের স্রোতে মিশছে। সেই রক্ত হাতে তুলে জাভেদ আমির বুকের শার্টে মাখালো। কান্নাটুকু বৃষ্টির পানির সাথে ধুয়ে গেল অন্ধকারে।
মাকে কেবল একবার জিজ্ঞেস করল, “খালেদ ভাই আসে নাই, আম্মা?ʼʼ
মুর্শিদা দু’পাশে মাথা নাড়েন। হাঁটু গেঁড়ে বসে রইলেন জলিল আমিদ জামিলের লাশের সামনে।
-“আব্বা! ওঠো।ʼʼ
কী ছিল জাভেদের কণ্ঠে কে জানে! জলিল আমির রাইফেলটা কাধে করে উঠে দাঁড়ান। আশ্চর্য! তার পা টলছে। তিনি বুঝলেন, মুক্তিযোদ্ধা হবার আগে তিনি সন্তানের বাপ!
কিন্তু জাভেদের ভেতর তো সন্তানপ্রীতি নেই। ভাইকে চোখের সামনে রক্তাক্ত দেখা, বোনের অনিশ্চিত পরিণতি তার বুকের ভেতরে তুফান তুলেছে। জাভেদ একবার চাচির ঘরে উঁকি দেয়। তাকে বলতে হয়নি, সে আন্দাজ করে নিয়েছে চাচির সাথে কী ঘটেছে। তার কলিজা মুচড়ে ওঠে। জয়নবের মুখটা মনে পড়ছে।
মুর্শিদার পায়ে হাত রেখে বলে জাভেদ, “বিদায় দ্যান, আম্মা। ফিরব নয় মরব। এর বেশি কিছু না। জয় বাংলা।ʼʼ
জলিল আমির আবার একবার পেছন ফিরে তাকান। মুর্শিদার কান্নার শব্দ বাড়ছে। মায়ের মৃতদেহটার আরেকবার তাকালেন তিনি। স্ত্রীর কান্নাকে উপেক্ষা করে বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি।
খালেদদের বাড়ির ছাই আগুনে ভিজে পিন্ড হয়ে গেছে। জাভেদের শরীর কাঁপছে। ঠান্ডায় অথবা উত্তেজনায়। তার দুই বোন ও ভাই কোথায়? খালেদ ভাইও কি পুড়ে মরে গেছে? সে তো বাড়িতে থাকে না। তার খোঁজে শয়তানেরা রোজ আসে বাড়ি বয়ে।
—
দিনাজপুর সেক্টর-৭ এর অন্তর্ভুক্ত। এই এপ্রিলেই সেক্টর-৭ এর কমান্ডার নিযুক্ত হয়েছেন নাজমুল হক। দিনাজপুর হিলি সীমান্তের কাছে। ভারতের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল। এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকেই পাকিস্তানি বাহিনী উঠেপড়ে লেগেছিল দিনাজপুর দখলের জন্য। একের পর অসংখ্য মানুষ হ-ত্যা করে ফিরছিল।
১৯-এপ্রিলের পর তাদের কঠিন এক হামলায় দিনাজপুরের মুক্তিযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। তারা সীমান্তের দিকেই আশ্রয় নিতে শুরু করল। কিন্তু সকলে বাঁচতে পারেনি। বেশ কয়েকজনকে প্রাণ দিতে হলো। বাড়িতে জানানো হয়নি সেসব শহীদদের মাঝে জাভেদের চাচাও আছে। জাভেদের চাচি ও শিশু চাচাতো ভাই মরে যাওয়ায় সেই কৈফিয়ত দিতে হয়নি। গোটা পুরো পরিবার একেবারে মরার এই এক সুবিধা।
চাচা মরেছে চাচির প্রায় সপ্তাহখানেক আগে। এর মাঝে আর জাভেদ ও জলিল আমির বাড়ি ফেরেননি। চাচি প্রতীক্ষায় ছিল স্বামীর। স্বামীর মৃত্যুর খবর পাওয়ার আগেই ধ-র্ষিতা হয়ে জীবন দিলো।
২১-শে এপ্রিলের পর পর হিলি বন্দরসহ প্রায় দিনাজপুরটাই পাক হানাদার বাহিনীর দখলে এলো। লোকজন পালিয়ে যেতে থাকল। শুধু যেতে পারেনি আমির পরিবারের লোকেরা। গতরাতে ২৬-ই এপ্রিল তারা না পালানো ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ফল পেয়ে গেছে।
—
জয়নবকে ২৮-ই এপ্রিল রাতে পালাক্রমে চারজন সামরিক বাহিনীর সদস্যরা ধ-র্ষণ করল। সে তখন রক্তাক্ত। ব্লাউজের এক হাতা তখনও ছিঁড়ে ডান বাহুতে আঁটকে আছে। পেটিকোটে র-ক্ত। শাড়িটা হাতের কাছে কোথাও নেই। এসবে তার কোনো দুঃখ লাগছে না। তার শুধু দুঃখ হলো চারদিকে তাকিয়ে। কোথাও একটু কিছু নেই, যা দিয়ে সে ছটফটে প্রাণপাখিকে খাঁচা থেকে মুক্ত করতে পারে। শাড়িটা কাছে থাকলেও হতো। শাড়ি নেই।
জয়নবের চুল বিশাল। গত পরশু আম্মা বেঁধে দিয়েছিলেন বেণী করে। বেণীর আগা থেকে ফিতে খসে গেছে। অর্ধেকটা বেণী আছে এখনও। রক্তাক্ত দূর্বল হাতদুটো দিয়ে জয়নব শক্ত করে বেণী পাকাতে শুরু করল। খোলা চুলের চেয়ে বেণী পাকানো চুল গলায় বেশি শক্ত করে ফাঁস লাগাতে পারবে।
কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হলো না। তার চুলগুলো কেটে দেয়া হলো। তাকে মরতে দেবে না হানাদার বাহিনী। বেঁচে থেকে গর্ভধারণ করতে হবে তাকে। পাকিস্তানীদের বীর্য থেকে জন্মানো এক খাঁটি সন্তানের মা হতে হবে তাকে।
জয়নবকে চিকিৎসাও করানো হবে।
কিন্তু পরদিন সকালের পর এক লোক এলো জয়নবের কাছে। লোকটাকে সে চেনে। আনোয়ার খন্দকার। জামিলকে মেরে পরশু রাতে জয়নবকে যখন ধরে আনা হচ্ছিল, লুটপাটকারীদের মধ্যে আনোয়ার নেতৃত্বে ছিল। সে পাশের পাড়ার মাতব্বরের চাচাতো ভাই। আমির পরিবারকে একটুও পছন্দ করে না। করা উচিতও না। একবার এক নতুন বউয়ের ঘরে ঢুকে পড়ার দায়ে জলিল আমির গাছের সাথে বেঁধে খুব পিটিয়েছিলেন আনোয়ার খন্দকারকে।
পঞ্চমবারের মতো ধ-র্ষিত জয়নব আনোয়ারের কাছে হলো।
কিন্তু এরপর আর জয়নব একটুও আত্মহত্যার চেষ্টা করল না। দরকার নেই। সে বুঝল, সে চেষ্টা করেও আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না। খুব র-ক্তক্ষরণ হচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে মেঝে। শরীরে খামছির দাগ কত। সেসব জায়গাও জ্বলছে। জয়নব মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। তার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। আব্বা আর জাভেদকে দেখা হয়নি দুটো সপ্তাহ! কিন্ত এ অবস্থায় দেখা করার কোনো ইচ্ছে নেই জয়নবের। সে অপবিত্রা। এই অবস্থায় অন্তত আব্বা আর খালেদের সাথে সাক্ষাৎ করা যায় না! কী বিদঘুটে লাঞ্ছনার ব্যাপার!
খানিক পর পাশের কক্ষ থেকে বিকট চিৎকারের আওয়াজ এলো। কাউকে মারা হচ্ছে। সপাৎ সপাৎ শব্দের সাথে আর্তনাদগুলো নারকীয় লাগছিল। কিন্তু জয়নবের মনে হচ্ছে কণ্ঠস্বরটা তার চেনা। মৃদু স্বর। কণ্ঠে প্রাণ নেই।
জয়নব চমকে উঠল। খালেদের আর্তনাদ। তার ধারণা সত্যি হলো। বিকেলের দিকে তার কক্ষে আরও কিছু নারী, খালেদসহ কিছু বন্দি ও লুটের মাল এনে রাখা হলো। হারিকেন, মোমবাতি ইত্যাদি জ্বালানো হলো। বৃষ্টির কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন জায়গাটির।
সেই আগুনের আলোতে জয়নব অবাক হয়ে দেখল শেষবার–এটা কেমন জায়গা! সে কোথায়? তার বিশ্বাস হতে চাইল না যে সে আসলেই এই জায়গায়!
খালেদের জ্ঞান নেই। প্রিয়তমার অবস্থা সে দেখল না। জয়নব কিন্তু দেখল শেষবার হবু স্বামীকে। সে আশায় আশায় জেবাকে খুঁজল। খালেদকে এখানে আনা হয়েছে তাহলে জেবা কোথায়? জয়নব জানতে পারল না জেবার তেরো বছর বয়সী দেহটাকে সেই বর্ষণের রাতেই ছিঁড়ে-ছুটে খেয়ে ফেলেছে তারই মাতৃভূমি বাংলাদেশের কিছু ক্ষুধার্তরা। এরপর খালেদদের বাড়িতে আগুন দিয়ে খালেদকে ভাত খাওয়া অবস্থায় ডেকে এনে ক্যাম্পে জমা দিয়ে গেছে মিলিটারীদের হাতে। খালেদের অপরাধ ছিল কঠোর। সে মিলিটারীদের এক কমান্ডারকে কুপিয়ে মেরেছে। কিন্তু তার মূল অপরাধ হলো, সে মুক্তিযোদ্ধাদের খবর আনা-নেওয়ার দূ। তার কাছে দিনাজপুরের সকল মুক্তিবাহিনীর খবরাখবর আছে। তিনটে দিন ধরে মেরেও খালেদের দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি প্রেমের ওপর কলঙ্ক লাগানো যায়নি। খালেদ বিশ্বাসঘাতকতার মতো সুবিধাজনক কাজটা করল না কোনোভাবেই। বোকা খালেদ মৃত্যুকে বেছে নিলো।
খালেদের কপাল বেয়ে তিরতির করে র-ক্ত পড়ছে। মেঝেতে পড়ে বাতাসে জমাট বেঁধে যাচ্ছে।
শেষ সময়ে জয়নবের খুব জয়নাল আর জাভেদের কথা মনে পড়ছিল। আব্বার মুখটা ভেসে উঠছিল। ইশ! আব্বা কি জানে, জয়নব কোথায়? জয়নাল তো ক্ষ্যাপা! সে যখন এসব জানবে, কী করবে? পাগল হয়ে যাবে বোধহয়!
—
চারদিন পর পয়লা মে তারিখের পর জলিল আমির জানতে পারলেন–জয়নালকে কারা বের করে নিয়ে গেছে আমির নিবাস থেকে। জয়নালকে উনারা পেলেন নদীর চরের এপারে জঙ্গলের ধারে অচেতন অবস্থায়। জয়নাল চারদিনের না খাওয়া অবস্থায় প্রায় অচেতন।
তাকে আমির নিবাস থেকে বের করে এনেছিল–কিছু দেশোদ্রোহী, সুবিধাভোগী বাঙালি। যুদ্ধটা যাদের কাছে বড়লোক হবার একটা সূবর্ণ-সুযোগ মাত্র। এরাও কিন্তু একেকজন মুক্তিযোদ্ধা। ২৫-ই মার্চের পর বাঙালির ভেতরে যে আগুন জ্বললো, তারপর এপ্রিলের শুরুতে মুক্তিবাহিনী যে মুক্তিকামনা নিয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধে নেমেছিল, তারা কিন্তু সেজন্য নামেনি। তাদের কেউ নেমেছিল লোভ-লালসায়, কেউ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে, কেউ বা ক্ষমতা ও যশ, খ্যাতি লাভ করতে, আর কেউ যুবক বয়সের আবেগী রক্তের ছটফটানিতে।
সে হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যোগদান করলেও ভেতরের মিরজাফরের সৈন্য-সত্ত্বাটা কিন্তু বহাল ছিল। এই যোদ্ধাদের সাথেই কাধে কাধ মিলিয়ে দুই সপ্তাহ আগে জলিল আমির মিলিটারীদের বুক তাক করে গুলি ছুঁড়েছেন। তারা তার পরিবারের জন্য যম হলো।
জয়নালের সুস্থ হতে একদিন লাগল। তার ভেতরের জেদ তাকে অসুস্থ থাকতে দিলো না। তাকে কেন মেরে ফেলতে গিয়েও মারা হয়নি তা বোঝা গেল না।
রাতে তারা আনোয়ার খন্দকারসহ গোটা বংশের বাড়িতে আগুন দিলো। আনোয়ারকে জয়নাল আমির নিজ হাতে জবাই করেছিল। এটা তার প্রথম খু-ন। বাড়ির মহিলারা খুব চেঁচাচ্ছিল। জাভেদের ভেতরে তখন কীসের যে হিংস্রতা চাপল। জয়নবের মুখটা তাকে তাড়া করছে। জয়নবকে সে শেষবার দেখেছে দুই সপ্তাহ আগে আব্বার সাথে যুদ্ধে বেরিয়ে যাবার সময়। জয়নব দৌড়ে এসে বাহুতে একটা তাবিজ বেঁধে দিয়েছিল।
জাভেদ আমির বাড়ির মহিলাদেরকে বাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে দিয়ে আব্বাকে ইশারা করল বাড়িতে আগুন দিতে।
মহিলারা গোটা অঞ্চলে ছড়িয়ে দিলো–আমির পরিবারের মানুষেরা রাজাকার। ওরা মুক্তিযোদ্ধার বেশ ধরে মিলিটারীদের কাজ করছে। ওরা মূলত মিলিটারী মারার নাম করে রাতের অন্ধকারে বাঙালিদের বাড়িঘর জ্বালাচ্ছে, মানুষ হ-ত্যা করছে। তার প্রমাণ তারা নিজে।
তিন বাপ-ব্যাটাকে পালিয়ে বেড়াতে হলো। তারা আর কোনো মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগ দিতে পারল না। গোটা অঞ্চল জানে তারা আমির বংশীয়। আর অধিকাংশ জমিদারেরা পাকিস্তানিদের সঙ্গ দিয়েছে। সুতরাং আমির পরিবারের রাজাকার হবার ব্যাপারটি খুবই বিশ্বাসযোগ্য হলো সবার কাছে।
এই হতাশা যেমন জাভেদ ও জলিল আমিরকে ব্যথিত করছিল, তেমনই উল্টো প্রভাব ফেলেছিল জয়নালের ওপর। জয়নালের ভেতরে পাগলাটে বিদ্রোহের জন্ম দিলো বরং। ছোটবেলা থেকে একরোখা, জেদি জয়নাল সহ্য করতে পারল না এত বড় অপবাদের গ্লানি। তার শুধু মনে হলো–যে মুক্তিযুদ্ধের দায়ে চাচা, ভাই, দুটো বোন, দাদি, চাচি, শিশু চাচাতো ভাইকে এত নির্মমভাবে হারালো, তার প্রতিদানে সে নেহাত কম পায়নি। তার বুক ফুলে উঠতো এত ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া এই কঠিন পরিচয়টিতে। জয়নাল সেটাকে গ্রহণ করল সাদরে। এত ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া এই পরিচয়টি সে আর কখনও নিজের থেকে আলাদা হতে দেয়নি–সে রাজাকার।
কোনোদিন আর জয়নাল নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা বা স্বাধীনতাকামী বলেনি। এক শব্দে সে নিজের পরিচয় দিয়েছে, ‘আমি রাজাকার।ʼ কোনোদিন নিজের সাফাই না গাওয়া পরবর্তীকালের সন্ত্রাস জয়নাল আমির স্পষ্টভাবে জানল না, তার বংশে পরবর্তীতে আরেকটা জয়নাল আমির জন্মাবে। জয়নালেরা বারবার জন্মায়। কেউ জানে না তাদের।
সে বাপ-ভাইয়ের সঙ্গ ছাড়ল। বাপ-ভাই বুকে কষ্ট চেপে লুকিয়ে মিলিটারী মারতে যায়। জয়নাল যায় না। সে আর মিলিটারী মারবে না। সে মারবে তাদের, যাদেরকে মারার ফলে সে-ও তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। ধীরে ধীরে তার হাত পাকাপোক্ত হলো। রাতের বেলা দেশোদ্রোহীদের মারে, দিনে পালিয়ে থাকে। কেউ কেউ তাকে চিনেও ফেলে। সে দেশের মানুষদের মেরে মেরে বের হচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে। তাতে একটা উপকার হলো। তার নামের শেষে রাজাকার শব্দটি খুবই শক্তপোক্তভাবে গেঁথে গেল।
জাভেদ কিন্তু বছরের মাঝামাঝিতে এসে দোটানায় পড়ল। সে জয়নালের মতোন অত জেদি নয়। তার ভেতরে দেশের জন্য বড্ড ব্যথা। কিন্তু সে বিশ্লেষণধর্মী মানুষ। সবাই যখন উন্মত্তের মতোন মিলিটারী মারতে ব্যস্ত, তাদের একটাই লক্ষ দৃশ্যমান দুশমনদের পূর্ব পাকিস্তানের জমিন থেকে বিদায় করতে হবে। এটা স্বাভাবিক। তৎকালীন পরিস্থিতি শুধুই মানুষের বর্তমান দেখার ওপর কাজ করে। কিন্তু পরিণতি, ফলাফল, গভীরতা সম্বন্ধে চিন্তা করতে মস্তিষ্ক সেই উত্তাল সময়ে কাউকেই নির্দেশ দেয় না।
গোটা বাঙালির হালও তাই। জলিল আমিরের হাল আরও তাই। তিনি এক দেবতার পুঁজো করেন। দেবতার নাম মুজিব। স্বাধীনতার ডাক দেওয়া দেবতার ভাষণ তিনি নিজকানে শুনেছেন রেসকোর্সে দাঁড়িয়ে। তিনি কেবল মুক্তি চান, তিনি বাঁচতে চান। এবারের এই সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
কিন্তু জাভেদ ভাবতে লাগল অন্যভাবে। ১৯৭০ সনের নির্বাচনে যখন আওয়ামী লীগ জয়লাভ করল, জাভেদের নিঃশ্বাস আঁটকে এসেছিল খুশিতে। কিন্তু একদল মোল্লা শ্রেণী সেটার অন্যরকম ব্যাখ্যা তৈরি করেছিল। তারা বলল, এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে জেতাতে ভারত থেকে মানুষ এসে ভোট দিয়ে গেছে। এই সহায়তার মূল উদ্দেশ্য কী? এই সহায়তার মূল উদ্দেশ্য কি পাকিস্তানকে দেশ থেকে তাড়িয়ে নিজেরা বাংলাদেশকে শাসন করা নয়? পাকিস্তান যদি ওদের শত্রু না হতো, তাহলেও কি ওরা বাঙালিকে এভাবেই তথাকথিত সহায়তা করতো? পাকিস্তানের ওপর নিজেদের একটা প্রতিশোধ নেবার সুযোগ হিসেবেই কি তারা এই সহায়তাটি পরিচালনা করছে না? এর বদলে তারা কী চায়?
মানুষ ক্ষেপে গেল মোল্লাদের ওপর। জাভেদের ইচ্ছে হয়েছিল ওদেরকে গিয়ে কুপিয়ে আসতে। দিনাজপুর, হাকিমপুরের কওমী মাদ্রাসার পরিচালক ও ধর্মীয় নেতারা এসব কথা বলতে শুরু করেছিল। তারা বলল, স্বাধীনতা আসলে কী? এক দেশ থেকে মুক্তি লাভ করে অন্য দেশের হাতে নিজেকে গোলামির উদ্দেশ্যে সঁপে দেবার নাম স্বাধীনতা? তাহলে এই স্বাধীনতা আমাদের কাম্য নয়।
জাভেদ মন ভরে তাদের ঘেন্না করে আসছে একটা বছর যাবৎ প্রায়। তার ঘেন্না হয় এটা ভাবলে যে, এরা তারই ধর্মের মোল্লা সম্প্রদায়। ধর্মও এদের ভেতরে দেশপ্রেম জাগায়নি। তারা ধর্মের নামে পাকিস্তানকে সমর্থন করে। ছিঃ! তারা স্বাধীনতা চায় না।
কিন্তু তাদের সাথে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা জাভেদকে কেমন যেন গভীর থেকে ভাবাতে শুরু করল। আচ্ছা, দুনিয়ার চলমান পরিস্থিতি ঠিক কেমন? কোথায় এর শেষ আর কোথায় বা শুরু? এত জটিল কেন সব? তারা কী করছে? স্বাধীনতা আসলে কী? তারা কি আসলেও স্বাধীন হবে? মোল্লারা কী বলে? ঠিক বলে না ভুল বলে? আবার যারা বলছে, স্বাধীনতা আসবে না পাকিস্তানিদের বিতারিত করলেও। তারা কারা? অধিকাংশ মুসলমান। যুদ্ধের ময়দানে জাভেদ তাদেরকে র-ক্তে জড়ানো ধুলোর ওপরে লুটিয়ে পড়ে এক সৃষ্টিকর্তার নামে সেজদা করতে দেখেছে।
তাহলে এটা কী? এই মুসলমানেরাই বলছে তারা স্বাধীন হবে না পাকিস্তান গেলে। শুধু পাকিস্তানকে সরিয়ে লাভ নেই। আবার এরাই তো ঝাঁপিয়ে পড়ছে যুদ্ধে। তাহলে এরা আসলে জাতিকে বলতে চাইছেটা কী? কোনো অগ্রিম বার্তা দিতে চাইছে না তো? যা তারা এখন বুঝতে পারছে না, পরে বুঝবে কিন্তু লাভ হবে না! আসলে দেশপ্রেমিক কারা, আর দেশোদ্রোহী কারা? পার্শ্বদেশ কেন সহায়তা করছে আমাদের? বিনা-স্বার্থে? তাই আবার হয়! মোল্লারা মূলত কেন ওদের সহায়তাকে ভালো চোখে দেখে না?
এসব ভেবে শেষ করার ফুরসৎ জাভেদ আমির পেয়েছিল না। তার আগেই জয়নাল খবর দিলো জয়নব ও খালেদকে পাকিস্তানিরা যে ঘাটিতে তুলে নিয়ে গেছিল, তা হাকিমপুরের মাদ্রাসা। পাকিস্তানিরা ওখানে দিনাজপুরকে কবজা করার লক্ষ্যে বিশাল ঘাঁটি গেড়েছে।
হাকিমপুর হিলি স্থলবন্দের কাছে। সহজ হিসেব। তারা যখন হিলি বন্দর দখল করেছে, তখন মোল্লাদের মাদ্রাসা মোল্লারা ছেড়ে দিয়েছে পাকিস্তানিদের জন্য। ওই মাদ্রাসাতেই এখন বাঙালি হ-ত্যা, নারী ধ-র্ষণ, লু-টপাটের মাল ভাগাভাগির কাজ চলে।
জাভেদের পূর্বেকার সব ভাবনা চুড়মার হয়ে গেল এই লহমায়। সে আবারও সৈয়দ পরিবার-বিদ্বেষী হলো। সৈয়দ পরিবার চালায় ওই মাদ্রাসা।
সৈয়দ পরিবারের নাম-চিহ্ন মিটিয়ে দিতে জয়নাল ও সে তৈরি হয়ে গেল। জয়নাল খুব শান্ত তখন। তাকে আর মোটেও মুক্তিযোদ্ধা লাগে না। তার ভেতরে মুক্তিযোদ্ধাদের মতো সেই তেজ, রক্ত টগবগ করা আগুন, চোখে মুক্তির নেশা এসব কিচ্ছু নেই। আছে এক অদ্ভুত শীতলতা।
জাভেদ অবাক হয়ে গেল–জয়নাল এক দেশোদ্রোহী বাহিনীর সহায়তা নিয়েছে সৈয়দ পরিবারে হামলা করতে। সেই বাহিনী না এদেশের না ওদেশের। তারা কেবল বিশৃঙ্খলার, উন্মাদ রাহাজানি আর র-ক্তার-ক্তির।
যা করলে অঞ্চলজুড়ে অস্থির, অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি হয়, তা করতে সদা প্রস্তুত সেই বাহিনীকে নিয়ে গিয়ে জয়নাল সৈয়দ পরিবারের অসুস্থ কর্তা বৃদ্ধ সৈয়দ আব্দুল বাশার নিয়াজী সাহেবকে গলা টিপে হ-ত্যা করল। সেই বাহিনী সৈয়দ পরিবারের কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে আমোদেও মেতে উঠল। জয়নাল কিচ্ছু বলল না। সে এগিয়েও গেল না। জয়নবের সাথে যা হয়েছে, তা সৈয়দ পরিবারের মহিলাদের সাথেও হলো। জয়নাল এতে কোনো ভুল দেখল না।
সেই বাহিনীর চাহিদা মেটাতে সে সৈয়দ পরিবারের শেষ সম্বলটুকু অবধি ছিনতাই করে নিয়ে এসে ওদের মাঝে বিলিয়ে দিলো। একটা পয়সা অথবা গহনাও রাখল না নিজের জন্য। তার বয়স সবে তখন আঠারো হবে।
আফসোসে তার মুখ কালো তখন। সৈয়দ পরিবারের বিশাল গোষ্ঠীশুদ্ধ পুরুষ জনতা তখন বাড়িতে নেই। জয়নাল মোল্লাদের পুরো বংশকে নির্বংশ করতে গেছিল। অসুস্থ বৃদ্ধ ও বাড়ির মহিলা ছাড়া কাউকে পেল না।
নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে দিনাজপুরের যোদ্ধারা বিশাল এক আগ্রাসনের মাধ্যমে বদ্ধ পরিকর হলো–মিলিটারীকে দিনাজপুরের মাটি থেকে উৎখাত করতে। তখন আর তারা কে রাজাকার, কে প্রকৃত যোদ্ধা তা হিসেব করেনি। সেক্ষেত্রে জলিল আমির সক্রিয় ছিলেন তাদের সাথেই। মুক্তাবাহিনী সেই উত্তাল সময়ে উনাকে তেমন গ্রাহ্য না করলেও ফেলে দিলেন না।
স্বাধীনতাকামী জলিল আমির সেসব কিচ্ছুতে মনোযোগ না দিয়ে কেবল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে গেলেন। দিনাজপুর হানাদারমুক্ত হলো ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তারিখে। এর মাঝে জলিল আমির চিরতরে নিজের ডান পায়ের চলাচল ক্ষমতা হারালেন। তার চলার সঙ্গী হলো লাঠি অথবা স্ক্রাচ।
কিন্তু এই চূড়ান্ত লড়াইয়ে দেখা গেল না তার দুই ছেলেকে। তিনি তাঁর পা হারানোর সুবাদে মুক্তিযোদ্ধার নাম পেলেও জাভেদ পেল দেশোদ্রোহী পরিচিতি। আর জয়নাল বলাবাহুল্যভাবেই একজন বিখ্যাত রাজাকার দিনাজপুরের।
আমির পরিবার ও সৈয়দ পরিবারের মাঝের এই দুশমনী তৈরির শুরুটা কোথাও একটা আচমকাই অদ্ভুতভাবে হলো বটে, কিন্তু এর শেষ নেই বোধহয়!
জয়নাল প্রকৃতপক্ষেই এক ত্রাসের সম্রাট হয়ে উঠল। তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন জাভেদ আমির। সে খুব খুশি খুশি বেরিয়ে গেল সুশীল সমাজ থেকে। তার খারাপ হতে একটুও কার্পণ্য নেই।
জাভেদ আমির কেমন পাগল পাগল হয়ে গেল। সে শুধু ভাবে আর ভাবে।
তখন দেশে লুটপাট চলছে। ক্ষমতার লুটপাট। কে কার ওপর দিয়ে কোন পদে বহাল হতে পারে। সবাই তখন প্রমাণ দিতে ব্যস্ত–কে কতটুকু অবদান রেখেছে স্বাধীনতায়, তাকে সেইটুকু মেপে হিসেব করে ক্ষমতা দিয়ে দেয়া হোক। কেউ তার প্রতিদান না নিয়ে ঘরে ফিরতে নারাজ।
জাভেদ ভাবনায় পড়ল, এরা কি তাহলে যুদ্ধ করেছে স্বাধীনতার জন্য নাকি প্রতিদানের আশায়? সে দেখল, ভারতও চমৎকার সহজ উপায়ে বাংলাদেশকে গ্রাস করে ফেলেছে। মুজিব তাতে সম্মতির হাসি হাসছেন। জাভেদের মস্তিষ্কে দিনদিন অস্বাভাবিক রকমের সব দর্শন খেলে যেতে লাগল। মোল্লারা কী বলতো! গুণীজনেরা কী বলে গেছেন! বছর যত যায় দেশের নেতারা তত রঙের রূপ দেখাতে থাকে। জাভেদের চোখের অনিন্দ্য সুপারহিরোরা কেমন সুপারভিলেন হয়ে উঠছিল।
জাভেদ খুব অল্প সময়ে বুঝে ফেলল, স্বাধীনতা একটি কল্পিত তত্ত্ব মাত্র। এর বাস্তবতা নেই। স্বাধীনতা কল্পনাতেই সুন্দর। বাঙালি আজও করুণ সুরে কাদে, খিদেয় পেটে পাথর বাঁধতে যায়, আজও নারীর সম্মান যায় কিন্তু বিচার হয় না, ক্ষমতার লড়াইয়ে দেশে অরাজকতা স্পষ্ট দেখা যায়। অথচ হানাদার গেছে বছর তিনেক প্রায় আগে। ক্যালেন্ডারের পাতায় এটা ১৯৭৪। তাহলে স্বাধীনতা আসলে কী?
এখন প্বার্শদেশ দেশের সম্পদে ঠিক সেভাবেই ভাগ বসায় যেমন ভাগ বাপের দুটো সন্তান বাপের সম্পত্তিতে পায়। বাংলাদেশের সম্পত্তি ও সার্বভৌমত্বে ভারতের সমান নয় বরং বেশি অধিকার। এসব কথা মোল্লারা বেশি বলে। তাই তাদের কল্লাটা বেশি যায়। তারা দেশোদ্রোহী। তারা দেশের নেতাদের বিরুদ্ধে কথা বলে। এরা আগে যেমন দেশের স্বাধীনতায় নারাজ ছিল, এখনও আছে। এই যে এখন কত সুন্দর স্বাধীনতা আমাদের! আগে পাকিস্তানীরা ক্ষমতায় ছিল, এখন দেশের সন্তান। অথচ ওরা বোঝে না, এরা খুশি না।
সব ঠিক লাগলেও জাভেদের ভেতর থেকে জয়নব ও খালেদের স্মরণ যায়নি। সে ঠিক মনে রেখেছে, মোল্লাদের মাদ্রাসায় এরা দুজন নৃশংসভাবে বলি হয়েছিল। জাভেদ দোটানায় দিশেহারা হয়ে উঠছিল দিনদিন। সে চুল-দাড়ি কামায় না, হাসে না, বসে থাকে বাগানের শেষে একটা চেয়ার পেতে। ঘন্টার পর ঘন্টা কেবল চুরুট টেনে চলে যায় তার দিন, মাস, বছর।
জলিল আমির জোর-জবরদস্তি করেও ১৯৮৫ সনের আগে জাভেদের বিয়ে দিতে পারলেন না। পাটোয়ারী বাড়ির একমাত্র মেয়ে হুমায়িরা পাটোয়ারীর সঙ্গে জাভেদ আমিরের বিয়ে হলো। জাভেদ আমিরের বয়স তখন একত্রিশ।
জয়নাল আমির রাজধানীতে ত্রাস গড়েছে। দিনাজপুরে এলেও সে আমির নিবাসে পা রাখে না। সে থাকে নিজের তৈরি বাসভবনে।
১৯৮৭ সনের ২৯-জুন জাভেদ আমিরের ছেলের জন্ম হলো। আশ্চর্যজনকভাবে প্রায় যুগখানেক পর আমির নিবাসে পা রাখলেন জয়নাল আমির। সাথে এক গাড়ি উপঢৌকন। তার ভাতিজা জন্মেছে। লোকে বলল–দেখতে জয়নাল আমিরের মতো। জাভেদ আমিরের চেহারায় সেই ধার নেই, যা তার সন্তানের চেহারায় দেখা গেল। কিন্তু তা জয়নাল আমিরের চেহারায় আছে।
জয়নাল আমির নাম রাখলেন ভাতিজার–জুনিয়র জয়নাল। কঠোর জয়নাল আমিরের ভেতরে শিশু ভাতিজার জন্য কীসের এক পাগলাটে স্নেহ যে জন্মালো। জুনিয়র জয়নালের নাম সংক্ষিপ্ত হলো। আমির পরিবারের পরবর্তী একমাত্র বংশধরের নাম হলো–জয় আমির। পুরোনো জমিদার বাড়ির শিশু উত্তরাধিকরীর আকিকাতে কতকগুলো গরু-মহিষ জবাই করলে জলিল আমির।
জয় আমিরের জীবনের শুরুটা ঠিক ততটাই অভিজাত্য ও যত্নের সাথে হলো যতটা অগোছালো ও ছন্নছাড়া তার পরিণতি পরবর্তীকালে হয়েছিল।
চলবে…