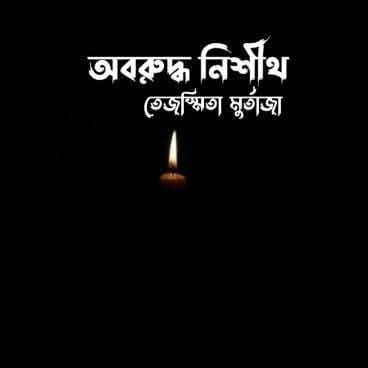#অবরুদ্ধ_নিশীথ
#তেজস্মিতা_মুর্তজা
পরিশিষ্ট.
৩০ জুন ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের সূর্য-ওঠা সকালে মাহেজাবিণ বসার কক্ষ থেকে উঠে আব্বুর রুমে যায়। বহুদিন বন্ধ পড়ে থাকা ধুলো জমা আলমারীটি খোলা হলো সেদিন। একটি গোল কোরে মোড়ানো কাগজ মাহেজাবিণ বের এনে সিস্টারের হাতে দেয়।
হাতটা একটু শিউরে ওঠে সিস্টারের। মোড়ানো কাগজটি ভারী। ভেতরে কিছু একটা। মোড়ক খুলতেই আরেকটি ছোট্ট কাগজ জড়ানো ভারী বস্তুটি হাতে আসে। একটি হাতঘড়ি। সেটার চকচকে প্লাটিনামের গোলক-প্রান্তে ভোরের আলো পড়ে তা চিকচিক করে ওঠে। ওটার ডায়ালের সাথে মুড়ে থাকা চিরকুটটি খুলে পড়েন সিস্টার—
উকিল ম্যাডাম,
চিহ্ন না দেখা গেলে শালার মানুষ নিজের গায়ের জন্মদাগ ভুলে যায়, আমারে কী মনে রাখবে? এই আমার চিহ্ন রইল। রেখে দিয়েন আপনার কাছে। নয়ত আমাকে মনে রাখার মতো কেউ হয়ত থাকবে না দুনিয়ায়। কেউ মনে না রাখলে এই দুনিয়া দিব্যি একটা আস্ত জয় আমিরকে ভুলে যাবে। এইটা ঠিক না।
বড় সাহেব দিছিল এইটা আমার পঁচিশতম জন্মদিনে, ২০১২-তে, পঁচাত্তরতমতেও যেন থাকে; আপনার কাছে। ততদিন আমি থাকব না। ওহ, হাহ্! এইটা সেই ঘড়ি, যেইটা আমার হাতে ছিল সেইদিন, যেইদিন আপনার সাথে ভার্সিটির মাঠে আমার প্রথম দেখা। আবার এইদিনও, যেইদিন আপনার নামে আমি একটা বলি চড়াইতে আসছি। এই শালা ঘড়ি আমার জন্যে কুফা আর আস্ত একখান বেইমান। থাকে আমার হাতে, অথচ শালার কাঁটা টিকটিক করে আপনার নামে। তো ওইটা আপনার কাছেই থাকুক।
•
সিস্টার সাতবার পড়লেন লেখাটুকু। হাতটা শিরশির করছে বোধহয়। এলোমেলো নজর তুলে তাকালেন মাহেজাবিণের দিকে। মাহেজাবিণ মৃদু হেসে ভ্রু নাচায়। ঘড়িখানা দেখতে ইশারা করে। জয় আমির হাতঘড়ির ক্ষেত্রে খুব সৌখিন ছিল।সব অক্ষত থাকলে নিশ্চয়ই আজও পাটোয়ারী বাড়িতে তার কক্ষের আলমারীতে নামী-দামী ব্রান্ডের বেশ কয়েকটা ঘড়ি তোলা আছে। সেইকো-অ্যাসট্রোন, পাটেক ফিলিপ, ক্যাসিও…
সিস্টার ঘড়িখানা হাতে তুলে নেন। বেশ ভারী। অডেমার্স পিগুয়েট ব্রান্ডের রয়্যাল অ্যক মডেলের হাতঘড়ি ওটা। দাম কমবেশি লাখখানেক হবার কথা। এক অন্ধকার সমুদ্র অথবা কালচে স্যাফায়ার (নীলমণি) রত্ন-রঙা ঘড়ির ডায়ালটিতে সিস্টারের চোখ ধাঁধায়। ওটার ডায়ালের যে গম্ভীর রঙ, তার আনুষ্ঠানিক নাম মূলত ‘ব্লু গ্রাঁন্দ ট্যাপিসেরি। সেই চকচকে ডায়ালে জয় আমিরের চিহ্নরূপে লেপ্টে আছে পুরোনো কবেকার শুকনো লাল তরলের ছাপ। একটা বলি চড়ানোর দিনের পরিহিত ঘড়ি যে! রক্তটুকু জয় আমিরের, এটা সিস্টার জানেন। কারণ সেই রক্তে হাত ছুঁইয়ে উনার মনে হচ্ছে এই রক্ত খুব চেনা, বহুপুরোনো জানা-শোনা।
উনাকে চোখের ছটফটানি দেখে মাহেজাবিণ হাসে, “কেমন লাগছে আপনার বহুল আকাঙ্ক্ষিত, অদেখা পাপীর চিহ্ন ছুঁয়ে? আরও কিছু আছে। চাই?ʼʼ
মাহেজাবিণ উঠে যায়। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে সেন্টার টেবিলের ওপর কিছু ধাতব পৌরুষ-অলংকার রাখে। দুটো ব্ল্যাক টাংস্টেনের আংটি, একটি রূপোর তৈরি রিস্টলেট, একটি প্লাটিনাম ধাতুর তৈরি শিকল আকৃতির চিকন ফিগারো-চেইন। তার লকেটটির আকৃতি J অক্ষর। প্রতিটা বস্তুতে রক্তের ঘ্রাণ ও আবছা ছাপ লেগে থাকা জিনিসগুলো হাতে ছুঁয়ে সিস্টারের মনে হলো তিনি এবার সচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন জয় আমিরের রক্তাক্ত নিথর দেহখানা, গুলি বুক ফুঁড়ে বেরোনোর পর রক্তে চেইন ও রিস্টলেট ভিজে ওঠার দৃশ্যটি। হামজার হাহাকার আর আরমিণের স্তব্ধতা।
এরপর জয় আমিরের রেখে যাওয়া বড় কাগজখানা সেদিন ভোর সকালে সিস্টার ক্যাথারিনের চোখের নোনাজলে ভিজেছিল। একটি A4 আকারের কাগজ, তার দু’পাশ ভর্তি লেখা। চিঠি নয়, পত্র, দরখাস্ত, কোনো সংবাদ অথবা ইচ্ছেপত্র নয় ওটা। কেবল একটি কাগজ, যার এপাশ-ওপাশ লেপ্টানো রক্তের ছোপ ছোপ দাগে, আর পৃষ্ঠাখানা ভরে কীসব লেখা!
চোখের অঘটন টের পেয়ে তিনি দ্রুত তা আঙুল বুলিয়ে মোছার চেষ্টা করেন। লাভ হলো না। ততক্ষণে সিস্টারের চোখের সবটুকু পানি পৃষ্ঠাখানা শুষে ভিজে উঠেছে। এতৈ কাগজের তৃষ্ণা মিটেছে কিনা বলা যায় না। কিন্তু সিস্টারের তৃষ্ণা বাড়ল। সেই তৃষ্ণা মেটানোর প্রথম ধাপে তিনি জানতে চাইলেন, মাহেজাবিণের ২০১৫ থেকে ২০১৮ অবধি আসার যাত্রা সম্বন্ধে কৌতূহল গাঢ়। একের পর এক প্রশ্ন করছিলেন।
–
অনার্স শেষ বর্ষে থেকে মাহেজাবিণকে পড়াশোনায় মনোযোগী হতে হয়েছিল পুরোদমে। এ সময়টাতে নিরাপত্তা দেবার জন্য কবীর চুপিসারে সর্বদা প্রস্তুত ছিল বাহিনী নিয়ে। এটার পেছনে তুলিরও হাত ছিল। সে শ্বশুরবাড়ি থেকে মায়ের বাড়ি আসার মতো তখন নাইয়রে আসে মাহেজাবিণের কাছে, সেই নারীকে নিরাপত্তা না দিলে সে কবীরের ঘর নাও করতে পারে। কিন্তু এটা মাহেজাবিণের পছন্দ ছিল না। এখানে একটা ঋণ জমা হবার ব্যাপার রয়ে যায়। কারও কাছে ঋণী হলে মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়, এক্ষেত্রে বিনয়ী হতে হয়, আর বিনয় কেবলই মানুষকে সত্য থেকে পিছপা করে। তবু কবীর পিছু ছাড়েনি।
এছাড়াও সে নিরাপত্তা পেয়েছিল মুরসালীনের শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে, মরিয়মের খাতিরে। মরিয়মকে মুরসালীন যাদের কাছে রেখে যাত্রায় বেরিয়েছিল, তারা মরিয়মের দেখভাল করা নারীটির নিরাপত্তা দিতে সদা-প্রস্তুত। যেটা খুব সক্রিয় কিন্তু আড়ালে। তারা নীরবে রোজ আমজাদ সাহেবের বাড়ি তো অবশ্যই সঙ্গে মাহেজাবিণের বাইরে চলাচলের সময়টা পেছনে থেকেছে বরাবর। আরও ছিলেন মানসিক সঙ্গের জন্য দোলন সাহেব।
২০১৬ এর শুরুর দিকে মাহেজাবিণের অনুরোধে দোলন সাহেব রূপকথার কেইসটি হাতে নেন। দিনশেষে রূপকথা কেবলই এক শিকার। ততদিনে অবশ্য রূপকথার ভেতর থেকে মুক্তির সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ফুরিয়ে গেছিল। কিন্তু দোলন সাহেবের প্রচেষ্টায় সে খালাস পেল বাংলাদেশের আইনি বন্দিশালা নামক উন্মাদখানা থেকে।
তাকে নিতে আসার জন্য কেউ নেই জেনে বেরোবার পর সে পেয়েছিল এক অনাকাঙ্ক্ষিত নারীকে। যাকে সে কারাগারে বসে দিনের দিন একটাবার দেখা করতে আসা মানুষদের কাতারে চেয়েছে। মাহেজাবিণ রূপকথাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল আমজাদ সাহেবের বানিয়ে রেখে যাওয়া ছোট্ট আশ্রয়কেন্দ্রে।
এতগুলো মানুষের পেট চালানোর জন্য আমজাদ সাহেবের সামান্য জমি বিক্রির পয়সা নেহাত তুচ্ছ। জয় আমিরের রেখে যাওয়া পয়সা বলতে কিছু আছে, তা কখনও মাহেজাবিণের খেয়ালে থাকেনি। কিন্তু সে ভাবী, আম্মু ও মরিয়মকে ঠিকই আলাদা করে জিজ্ঞেস করেছিল, “আপনারা চাইলে জয় আমিরের রেখে যাওয়া এই টাকা নিজেদের জন্য খরচ করতে পারেন। অনুমতি পেলে আপনাদের খরচে ওই অর্থ ব্যয় হবে।ʼʼ
মার্জিয়া কিছুদিন কথা বলেনি তার সাথে। সেই দিনগুলোতে মাহেজাবিণ খুব ছটফট করে একদিন গিয়ে ভাবীর কাছে বসে জিজ্ঞেস করে, “কথা বলেন না কেন আমার সাথে? ঠিকমতো খান না, অরিবাকে আমার কাছে আসতে দেন না। কী করেছি আমি? কোনো ভুল করলে শাস্তি দেন, তবু এভাবে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন না।ʼʼ
মার্জিয়া হেসে ফেলে, “আমার মতোন মেয়েলোকের সাধ্যি কোথায় অন্তূ, তোমার থেকে মুখ ফিরায়ে থাকার? তোমার ঘাঁড়ে খাচ্ছি, পরতেছি।ʼʼ
হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলার দৃশ্য খুব ভয়ানক হয়। সেই দৃশ্যই দেখা গেল মার্জিয়ার মুখে—
“ভাবো তো, অন্তূ! কতবড় বোঝা আমি আর আমার এতিম মেয়ে এই দুনিয়ার? তুমি বলছিলা, আমার আর সন্তানের ভার নিবা। পারতেছ না। তুমি আমার আর আমার মেয়ের পেট চালাইতে সেই লোকের পয়সায় নির্ভর করতে চাও, যে আমার সোহাগ কাড়ছে আমার কাছে। আমার পেটের মেয়েরে এতিম বানাইছে। বলো, এর চাইতে লজ্জার কিছু হইতে আছে? বলো তো অন্তূ? দুনিয়ার ওপর কোনো মা-মেয়ে কতটা ভারী হইলে স্বামী আর বাপের খুনীর পয়সা খাওয়ার কথা ওঠে? বলো!ʼʼ
মাহেজাবিণের হাতদুটো চেপে ধরে অঝোরে কেঁদে ফেলল মার্জিয়া, “এত খাই আমরা? তোমার যাতে ভার না হয়, আমি না দর্জির কাজ করি অন্তূ? তুমি ক্যান একটাবার ভাবলা না এই কথা আমার সামনে উচ্চারণ করা ঠিক হবে না তোমার? আমি জানি আমি অকাল বিধবা, আমার স্বামী নাই, একটা দুধের মেয়ে। তাই বলে তুমি আমার স্বামীর খুনের রক্তমাখা পয়সা আমার জন্য বরাদ্দ করতে চাইবা, অন্তূ? আমার তো বাপের বাড়ি সচ্ছল না অন্তূ। তাই আমি চাইলেও ওদের কাছে যাইতে পারব না….ʼʼ
মাহেজাবিণ সহ্য করতে না পেরে ধমকে উঠল, “চুপ করুন, আপনি। কথা বলার সুযোগই দিচ্ছেন না। পাগল হয়েছেন? আমাকে কি পাথর লাগে আপনাদের? অমানুষ, জানোয়ার ভাবতে ভালো লাগে সবার? সবাই কী মনে করেন নিজেদেরকে? এক আপনাদের ব্যথা আছে, শোক আছে, ঘেন্না আছে, অভিযোগ আছে—আর আমি গাছ? গাছেরও তো ব্যথা থাকে। আপনারা কেউ সেটাও ভাবেন না আমায়।ʼʼ
মাহেজাবিণের চোখ ছলছল করে। কিন্তু জল গড়ানোর অনুমতি নেই বলে গাল শুকনো রয়ে যায়।
-“ওটা আমার দেনমোহরের টাকা। আসামী হিসেবে ওটা অন্তত স্বামী হিসেবে দিয়ে গেছে আমার আসামী। আমি এই যে এই অপদার্থ জীবনটাকে সেই নরকের অতিথির কাছে বিক্রি করেছিলাম বাপ আর সমাজের দায়ে, সেই টাকা ওটা। ওটা অবশ্যই জয় আমিরের দেয়া টাকা, কিন্তু ওতে অধিকার শুধু আমার।ʼʼ
-“তাহলে তুমি ক্যান আজ পর্যন্ত ওই টাকা থেকে এক আনা পয়সা খরচা করো নাই নিজের জন্যে? অসুখে যে মরবা কখন জানি, এক পয়সাও কেন নিজের জন্যে ভাঙো নাই? তাইলে আমার মেয়ে আর আমার জন্য ওই টাকার প্রশ্ন উঠাইলা ক্যান?ʼʼ
মাহেজাবিণের কাছে জবাব নেই। সে চুপচাপ উঠে চলে এসেছিল মার্জিয়াকে শান্তিমতো কাঁদতে দিয়ে।
মার্জিয়ার মতোন রাবেয়া কথা বন্ধ করেননি, শুধু চুপচাপ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলেছিলেন, “তোর বাপের পয়সা আমার জন্যে যথেষ্ট হচ্ছে না, অন্তূ? খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে আমার খরচা?ʼʼ
মাহেজাবিণ লজ্জায় আর তাকাতে পারেনি আম্মুর দিকে। আর মরিয়ম বলেছিলেন, “আমি তো জয়ের জিম্মায় আসি নাই। আইছি আমজাদ ভাইজানের মেয়ের আশ্রয়ে।ʼʼ
সুতরাং জয় আমিরের সঁপে যাওয়া সম্পত্তির দলিল, নগদ অর্থের চেইকবই প্রভৃতি রাবেয়ার কক্ষের আলামারীতে ধুলোয় ভারী হতে লাগল।
জমি বিক্রির টাকা থেকে সামান্য কিছু নিজের পড়ালেখার জন্য রেখে বাকিটা সবার চিকিৎসা, পোশাক, খাবারে লেগে যেতে লাগল। কিন্তু নিজের মারাত্মক অসুস্থতাকে এড়িয়ে যেতে মাহেজাবিণ দক্ষ। অরিবাকে একটি সুন্দর জীবন দেবার প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হতে লাগল। তার দুধের দাম, যাবতীয় খরচায় সে হিমশিম খেতে লাগল। পরনের ছেঁড়া জামাটা কেউ দেখার আগেই রাতে সেলাই করে নেয়া রোজকার কর্ম হয়ে দাঁড়াল।
তার তখন শুধু একজন ফিজিওলজিস্ট নয় সঙ্গে সাইকোলজিস্ট নিয়মিতভাবে প্রয়োজন। সারাদিন যেমন-তেমন, রাতগুলো ভয়াবহ। মানসিক অসুস্থতা চরমে পৌঁছাতে লাগল। মাঝেমধ্যেই মানসিক যন্ত্রণা আত্মহত্যার লোভ দেখাতে অবধি ছাড়েনি তাকে। চেহারার লাবণ্য, মুখের হাসি, শরীরের সুস্থতা বিলীন হয়ে গেল। শুধু চলতে লাগল তার জীবন-যুদ্ধ ও পড়ালেখা।
মার্জিয়া সেলাই মেশিনে পা চালাতে চালাতে তাকে ডেকে প্রায়শই বলতো, “তুমি জানো তুমি পাগল? অন্যভাবে এইটারে বলে বদ্ধ উন্মাদ। নাইলে এমনে মানুষ বাঁচে? এতটা পারে?ʼʼ
-“আপনার কথা বলুন। আপনি যুবতী নারী, ভাবী। ছোট্ট একটি মেয়ে আপনার। বিয়ে করতে রাজী হোন। আমি ব্যবস্থা করব। এই জীবন এভাবে যাবে না।ʼʼ
-“তুমি কী চাও? আমি সব ভুলে অন্যকারও সাথে সুখী হবো?স্বপ্নের মতো সহজ সব? আর আমার মেয়ে অন্যলোকের ঘরের বোঝা হবে?ʼʼ
-“ওকে আমি রাখব।ʼʼ
-“বাপহীন জীবন আমার মেয়ে জীবন পাওয়ার আগেই পাইছে, অন্তূ। মা-হীন জীবন আমি তাকে দেব না। তুমি কী বলো, মনে আছে? নিজে যেমন বিয়ে বলতে একবার, একজন, একজনম বোঝো, তোমার নাকি এক জীবনে, এক নারীত্বে এক পুরুষই সই—আমাকেও তা-ই বুঝতে দাও! তাও তো তোমার স্বামী ছিল পাপীদের সর্দার, আর আমার কিনা এক নাজুক শিকার। এ কথা আর কোনোদিন বোলো না আমাকে।ʼʼ
এ পর্যায়ে সিস্টার ক্যাথারিন এক টুকরো হেসে বলেছিলেন, “আমি তোমার গল্পে বহুবার ঘুরে মাঝেমধ্যেই এক জায়গায় ঠেকেছি, মাহেজাবিণ। সতী নারী, তুমি। অথচ বিধাতা তোমার সতীত্বের কী কঠোর পরীক্ষা নিলেন বলো তো! সত্বী নারীকে তিনি পতি দিলেন পাপী। এত পাপ তোমার পতি করেছে, অথচ তার একচুল হক তুমি নষ্ট করোনি তার অজান্তেও! জয় আমিরের হাতের বৈবাহিক রেখা খারাপ ছিল না, বলো! একটাবার সেই খুনী হাতদুটো দেখলে আরও ভালো বুঝতাম! সে কী করে সতী পেল?ʼʼ
“সে সতী পায়নি, মাদাম। সতীত্ব লুট করে তবে গ্রহণ করেছিল আমায়। আমি যখন তার হয়েছি, আর সতী ছিলাম না।ʼʼ
-“গর্দভ, তুমি। চুপ করে শোনো আমার কথা। হিন্দু পুরাণ পড়েছ?ʼʼ
-“না।ʼʼ
-“সেখানে বলা আছে—সতী নারীর চোখের জলের অভিশাপে রাজ্য পুড়ে ছাই হয়। বুঝলে?ʼʼ
মাহেজাবিণ চুপ করে রয়। সে কি সত্যিই সতী নারী? সেচ্ছায় একটুও অসতী সে হতে পারে না কখনও? আরও এমন ঘটনা আছে, সিস্টার সেসব শুনলে আরও বেশি করে এসব বলবেন।
সেসবের মাঝে মাহেজাবিণের কাছে একদিন সংবাদ এসেছিল, পরাগ আজগরের ফাঁসির রায় দিয়েছে। পরাগ একটাবার তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। মাহেজাবিণ গেল না। পরপুরুষের সঙ্গে অকারণে দেখা করার প্রশ্ন ওঠে না। তবে খারাপ লাগল কিছুটা। কিন্তু রূপকথা অনুরোধ করলেও সে যায়নি। তার কাছে তখনও জীবন্ত-যন্ত্রণা–পলাশের রূফটপের সেই সন্ধ্যারাত। যেখানে তাকে অসৎ হাত ছুঁয়ে দিয়েছিল, আর পরাগ আড়ালে তার প্রতিনিধিত্ব করেছিল।
মাহেজাবিণের পড়ালেখার পরিকল্পনা আমজাদ সাহেব ঠিক করে রেখে গেছিলেন। মাহেজাবিণের ইচ্ছে ছিল কোনো স্বনামধন্য সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবিতে অনার্স শেষ করে মাস্টার্স অফ ল করার, উচ্চতর শিক্ষাসমেত উকিল হবার। আমজাদ সাহেব আপত্তি করলেন। মাহেজাবিণকে নিজ জেলায় হাবিপ্রবিতে সমাজবিজ্ঞানে অনার্স করাতে মনস্থির করলেন তিনি। এরপর অনার্স শেষে দুই বছর মেয়াদী এলএলবি কোর্স শেষ করে বার কাউন্সিল পরীক্ষায় বসানোর পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলো। কিন্তু মাহেজাবিণের বরাবরই মনে হয়েছে এটা তার জন্য খুব বড় কোনো ক্যারিয়ার হবে না।
তবে সে হিসেবেই পড়ালেখা চলতে লাগল তার।
আমজাদ সাহেবের মৃত্যুবার্ষিকী ২৭-নভেম্বর তারিখে। ২০১৬ এর সেই তারিখটিতে রাবেয়া খুব জেদ ধরেছিলেন স্বামী ও পুত্রের কবর জেয়ারতে যেতে। মাহেজাবিণের সাহসে কুলায় না বিষয়টা। সে শেষবার যেবার উন্মাদের মতোন ছুটে আব্বুর কবরে চলে গেছিল, তাকে ধরে এনেছিল জয় আমির। আজ মাকে নিয়ে গেলে নাজানি মায়ের চেয়ে সে বেশি বেসামাল হয়। সঙ্গে তাই ভাবীকে নিয়েছিল। এটাও ভুল সিদ্ধান্ত হলো। দুজন আরও বেশি বেকায়দা হয়ে পড়ল। তার একটা কারণ আছে, অন্তূর কাছে রোজ আমজাদ সাহেব আসছেন, কথা বলছেন, সময় দিচ্ছেন। রাবেয়া ও মার্জিয়া তো তা পায় না।
মার্জিয়াকে সামলানো গেলেও রাবেয়ার কী হলো কে জানে! বহুক্ষণ যাবৎ নিথর হয়ে গোরস্থানের ফটক চেপে ধরে অপলক চেয়ে ছিলেন স্বামী-সন্তানের কবরের দিকে। এরপর একদম শান্ত-শীতল বাড়ি ফিরলেন।
বাড়ি ফিরে রাবেয়া স্ট্রোক করলেন। ঠিক যে সময়ে আমজাদ সাহেবের স্ট্রোক হয়েছিল, রাত্রির সেই তৃতীয় প্রহরে আরেকটি কালরাত্রি নামল মাহেজাবিণের জীবনে। বাড়িতে পুরুষ বলতে কেউ নেই, কিন্তু ঠিক গেইট খুলে মরিয়ম কয়েকটি যুবক ও পুরুষকে ভেতরে নিয়ে এলেন, খুব স্বাভাবিকভাবে। সেদিন মাহেজাবিণ জানতে পারল তাদের বাড়িটা দিনরাত নিরাপত্তায় ঘেরা, যেন তার অনিষ্ট করতে কেউ এ-মুখো না হতে পারে।
রাবেয়াকে নিয়ে ছয়দিন একাধারে হাসপাতালে কাটানোর পর ডাক্তার রাতে বলে গেলেন, ‘কাল-পরশু রিলিজ করা যেতে পারে। সি ইজ আউট অফ ডেঞ্জার।ʼ কথাটা বলা ঠিক হলো না। কারণ ওই কথা শুনেই সেই রাতের শেষে ফজরের ওয়াক্তে রাবেয়ার মস্তিষ্ক বড় স্ট্রোকটা হাসপাতালে অবস্থাকালে ঘটালো। শিরা ছিঁড়ে সরাসরি রক্তপাত। মাহেজাবিণ সেবার প্রথমবার মনস্থির করেছিল জয় আমিরের পয়সা খরচা করার। দরকার পড়লে সেই অপারেশনে সে সব টাকা খরচা করে দেবে এই নিয়ত করার পর ডাক্তারেরা ঘাঁড় নাড়লেন। মানে কী?
মাহেজাবিণ বুঝতে চায় না সেই ঘাঁড় নাড়ার মানে। জীবনকে সে এত সেচ্ছাচারিত্ব কোনোভাবেই করতে দিতে পারে না। জীবন পেয়েছে কী তাকে? ডাক্তারদের কাজ কী? একবার ঘাঁড় নেড়েছে, আব্বু পালিয়েছে তাতে। আবার সেই ঘাঁড় নাড়ানি!
সেই সকাল পেরিয়ে সন্ধ্যা হবার আগেই রাবেয়ার জবান বন্ধ হয়ে গেল। তখন মাহেজাবিণ আছরের ওয়াক্তে যোহরের কাজা আদায় করছে হাসপাতালের নোংরা বারান্দার কোণে। মরিয়ম গিয়ে আলগোছে তুলে আনেন মাহেজাবিণকে। মাহেজাবিণ এসে দেখে, আম্মু কাঁদছে। বাপ-মায়ের ওপর সমস্ত বিশ্বাস সেদিন মাহেজাবিণের ফুরিয়ে গেল। এরা একেকটা চূড়ান্ত পর্যায়ের বেইমান। খুব মায়ায় পালে, তারপর সংকটে রেখে হাসপাতালে শুয়ে কাছে ডেকে নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে কাঁদে। এই কান্নার একটা বিশেষত্ব আছে। এই কান্নার পর চোখ বুজে ফেলে এরা। তারপর হাজার কিছুতেও আর চোখ খোলে না। কোনোভাবেই না।
মাহেজাবিণ একেক কদম পেছায়, তার ক্ষোভ ফেটে পড়ে, “না আম্মু। তোমার মুখে-চোখে আব্বুর ভাব দেখছি। আমি এবার আর বোকা হবো না। তুমি হাজার ডাকলেও আমি তোমার কাছে বসব না। তুমি শেষ বিদায় চাইতে কাছে ডাকবে, আর আমি তোমার কাছে বসে তা দেব-নেব? পাগল না আমি।ʼʼ
কিন্তু পরক্ষণেই মাহেজাবিণ হুড়মুড় করে গিয়ে বসে মায়ের কাছে, “এই এই শোনো আম্মু! কেন জন্ম দিয়েছিলে আমায়? বলো আজ। বলো বলো। আজ শুনি। কেন জন্ম দিয়েছিলে? চোখের সামনে বাপ চলে যাবে, ভাই যাবে, সন্তান যাবে অকালে, এক পাপী স্বামী সে পালাবে কৌশলে, তারপর তুমি…
এইসব চোখ বড় বড় করে দেখব, আমি সব দেখব, শুধু দেখব তোমাদের তামাশা এই জন্য জন্ম দিয়েছিলে তো? অস্বীকার করলাম। আমি আমার এই অভিশপ্ত জনমকেই অস্বীকার করলাম। এই জীবন আমি মানি না। আমি এত বড় আয়ু চাইনি। নাকি তোমরা সবাই নিজেদের আয়ু কেটে কেটে আমাকে দিয়ে দিয়ে যাচ্ছ যাতে বেঁচে থাকি আর দেখি, এ সাজার জনম না ফুরুক আমার! কীসের সাজা, আম্মা? তুমি বলো। জন্ম তো তুমি দিয়েছ, জন্মে কোনো পাপ থাকলে তোমার জানার কথা। বলে দাও আজ। আমার রইল কী? কী নিয়ে বাঁচার জন্য জন্ম দিলে, আবার সেই জন্মে বাঁচার জন্য রেখে যাচ্ছ, বলো।ʼʼ
রাবেয়া জিহ্বা নাড়লেন, কথা বেরোলো না। তাই তিনি অন্তূর সামনে হাতদুটো জোড় করে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ছলছলে ভেজা চোখদুটোয় ঠোঁট নেড়ে শেষবার অন্তূকে কত কী বলার আঁকুতি যে সেখানে! কিন্তু বলা হলো না বলে শুধু থুতনিটা থরথর করে কাঁপল তাঁর। মাহেজাবিণ সহ্য করতে না পেরে আম্মুর শিথিল দেহটা তুলে বুকের সাথে জাপটে মিশিয়ে ধরে।
-“যেও না, আম্মু। আমার আর কেউ নেই এই দুনিয়ায় বিশ্বাস করো। বাপ, ভাই, সন্তান, স্বামী, আশ্রয় কিচ্ছু নেই। আমার মাথায় তেল দেবার জন্য একটা তোমার মতো সরলাকে খুব দরকার পড়বে, কোথায় পাব, কোথায় যাব? একজন চলে গেছে আমাকে রাস্তা পার হওয়া না শিখিয়ে, তুমিও যাচ্ছ… কেউ বললে না, চল অন্তূ, সঙ্গে চল। এত খারাপ না আমি। বিশ্বাস করো। কেউ তো সঙ্গে থাকো! কেউ তো থাকো, কেউ তো থাকো আমার। এত বড় দুনিয়ায় আমি একা বিলীন হয়ে যাব, আম্মু। আমার গর্ভের এক টুকরো ধন ওরা ছিঁড়ে নিয়েছে। যার গর্ভে আমি ছিলাম, সে আমার মায়া ছিঁড়ে চলে যাচ্ছে….আমার অপরাধ কী?ʼʼ
ততক্ষণে কেউ মাহেজাবিণকে বলেনি, তার অভিযোগ শোনার বদলে তার আম্মু অনেকক্ষণ আগেই তার বুকে মিশে থাকার নাম কোরে চুপিসারে পালিয়েছে।
১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মানো মাহেজাবিণ আরমিণ অন্তূ তার বয়স প্রায় চব্বিশ হতে না হতেই সকল রক্তের সম্পর্ক থেকে মুক্ত হলো সেইবছর। চারটিখানি কথা নয়। একটি মেয়ে, যার জীবনে নিজের বলতে কিচ্ছুই না থাকার এই মহান প্রাপ্তি অর্জনের সাধ্যি সবার থাকে না।
সেই বছরই অনার্স শেষ করে ২০১৭-তে তাকে ভর্তি হতে হলো–ল কোর্সে। তখন থেকেই দোলন সাহেবের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও আলোচনায় থাকতে লাগল। ল-তে ভর্তি হবার কালে মাহেজাবিণ চব্বিশ বর্ষীয়া এক সর্বহারা বিধবা নারী। তখন থেকে তার পরণে শোভা পেতে লাগল টিন্ট ব্লু রঙের শাড়ি। যা সাদারই নীল-সংস্করণ মাহেজাবিণের জন্য। সরাসরি সাদা নয়, সাদাকে ধোঁকা দিতে সে বরং বেছে নিলো টিন্ট-ব্লু। এবং ল ভর্তি হবার সাথে সাথেই সে হয়ে উঠল পেশাগত নারী, খুব শীঘ্রই হতে যাওয়া অ্যাডভোকেট মাহেজাবিণ আমির।
দোলন সাহেবের সহকারীর ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হলো সে। মামলা সংক্রান্ত নথি পর্যবেক্ষণ, মক্কেলদের সঙ্গে টুকটাক আলোচনা, ঘটনা শোনা ও নিজে চিন্তা করা, দোলন সাহেবের প্রতিক্রিয়া ও চলন খেয়াল করা ইত্যাদির সাথে সাথে কোর্টে শুনানিতে হাজির হওয়া, আদালতের প্রক্রিয়া, বিচারকদের বক্তব্য, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত অনুধাবণ, দেশ সমাজের পরিস্থিতি নিজের মধ্যে পর্যালোচনার এ পর্যায়ে সে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল অবশেষে নিজের স্বপ্ন ও গন্তব্যের পথে। সাথে আইনি গবেষণা, কেইস স্টাডি, দোলন সাহেবের দেয়া ফাইল সলভ করার চেষ্টা তার নারকীয় রাতগুলোর ঢাল হতে লাগল একটু একটু করে।
এ সময় আব্বু তাকে সর্বক্ষণ দেখে। সেই মেহেদি রাঙা দাড়ি-গোফের মাঝখানে গম্ভীর এক টুকরো হাসিমাখা মুখ ও উজ্জ্বল চোখদুটো হবু অ্যাডভোকেট মাহেজাবিণ আমিরের সমস্ত কার্যক্রম অনুসরণ করে। মাহেজাবিণ টের পায়। এক মুহূর্তও সে নিজেকে একা ভাবতে পারে না। সর্বক্ষণ চারপাশে আব্বুর অস্তিত্ব ও গন্ধে বিভোর মাহেজাবিণ সব ভুলে কেবল গন্তব্যের পথে ছুটতে লাগল। একটি কোচিং সেন্টারে তাকে শিক্ষকের কাজ করে সামান্য আয়ও করা শুরু করতে হলো। অন্তিকের মেয়েটা বড় হচ্ছিল। তাকে একটি সুন্দর জীবন দেবার দায় যে তার!
এলএলবি প্রথম বর্ষ শেষ করে ২০১৮ তে দ্বিতীয় বর্ষে উন্নীত হবার পর পুরোনো বিপদ হাতছানি দিতে লাগল তাকে। এতদিন তার কাছে জয় আমিরের আরও দুটি আমানত ছিল। একটি কুড়াল ও জয় আমিরের নিজের ব্যবহৃত পিস্তলটি—সেমি-অটোমেটিক গ্রান্ড পাওয়ার K-100। পিস্তলটি যখন তার কাছে আসে, ওটার ম্যাগাজিন ছিল খালি। তাই দোলন সাহেব মাহেজাবিণকে দুটো 9mm প্যারাবুলাম ক্যালিবারের বুলেট দিয়েছিলেন। সেটা বাড়িতেই থেকেছে। কখনও সঙ্গী করে বাইরে বের হওয়া হয়নি।
২০১৮-তে সেই কাঙ্ক্ষিত নির্বাচনের হিড়িক লাগল, যেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হামজা রক্ত ও নীতিহীনতায় হাত ও প্রবৃত্তি ডুবিয়েছিল। সেই নির্বাচনী বছর এলো, কিন্তু হামজা ততদিনে হুইল চেয়ারে লেপ্টে থাকা এক শ্বাস গ্রহণকারী মরদেহ। এই বছরগুলোতে নেহাত কমবার হামজার ওপর হামলা হয়নি। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছু করা যায়নি। প্রায় আড়াইটা বছর মাহেজাবিণকেও ধরে বধ করার কম প্রচেষ্টা বাপ্পী ও তার দলবল চালায়নি। মাহেজাবিণও হাতে আসেনি তাদের। তাই নির্বাচনের আগে আবারও পুরোনো সেই ক্ষতগুলো দগদগ করে উঠল।
এর যথাযথ কারণ আছে। বাপ্পীর কাকাকে হামজা কতটা যত্নসহকারে খুন করার পরেও তার কোনো উল্লেখযোগ্য শাস্তি হয়নি। জয়ের বউ কামরুলকে খুন করার পরেও তারও কোনো শাস্তি না হয়ে বরং আইন পড়ছে। অথচ মাঝখান থেকে কাকা চলে যাওয়ায় তাদের দলছুট হয়েছে, নতুন ও প্রতিপক্ষরা নির্বাচনে অংশ নেবার জন্য প্রস্তুত, অথচ কাকা নেই। জয়ের বউ ও হামজাকে শেষ করা খুবই দরকারী মনে হলো এ পর্যায়ে। ওই দুটো তাদের গলার কাঁটার মতো বিঁধে ছিল বিগত দিনগুলোতে।
-
ক্যারেন্ডার বলছে–২০১৮ এর ফেব্রুয়ারি চলে।
হামজার বই পড়ার অভ্যাসটা রয়ে গেছে তখনও। বিগত দিনগুলোতে চিকিৎসার পেছনে বেশ দৌড়েও কেবল উন্নতির মাঝে হাত ও মুখ সচল হয়েছে। পা দুটো চলাচল হলেও মেরুদণ্ড যেখানে অচল, নিজ থেকে হাঁটাচলা অসম্ভব।
রিমি রাতের জন্য হালকা খাবার রান্না করে নিয়ে সেদিন রুমে এলো রাত এগারোটায়। হামজা বিছানার হেডবোর্ডে হেলান দিয়ে ছাদ দেখছে। বইটা পাশে পড়ে আছে। চোখের চশমা খোলেনি। রিমি চুপচাপ গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়। শীত ভালোই। তবু তার খারাপ লাগল না ঠান্ডা হাওয়া, গা শিনশিনে বাতাস। বারান্দা থেকে ঘাঁড় ফেরালে আধশোয়া হামজাকে দেখা যায়। স্বাস্থ আর আগের মতো বলবান, সুঠাম নেই। শরীর শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে এসেছে মেডিসিন-ড্রাগ ও থেরাপির প্রভাবে। চোখের নিচে কয়লার কালি, কোটরের খুব ভেতরে অসুস্থ, ফ্যাকাশে লাল চোখদুটো। আজ খুব একটা চাতুর্য দেখা যায় না। শান্তভাব চিরায়তভাবে রয়ে গেছে। দেখলে কখনও কখনও মৃত লাগে। যেন কৃত্রিম উপায়ে একটি প্রাণরসহীন ফলকে তাজা রাখার চেষ্টা।
খুব একটা কথা হয় না লোকটার সঙ্গে সারাদিনে। রিমি যে কীসের দূরত্ব বজায় রাখতে শিখেছে তা সেও জানে না। একটি মৃত বাড়ি, প্রাণহীন, লাশেদের স্মৃতির ইটে গাঁথা বাড়িটির ভিত। রিমি প্রতিক্ষণে দেয়ালের গা থেকে ছিটকে আসা আর্তনাদ শুনতে পেয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে। বিভ্রম তৈরি হয় সারাক্ষণ। সে তরুকে দেখে, জয়কে দেখে হাত-পা না ধুয়ে ঘামমাখা শরীরে টেবিলটায় খেতে বসতে, আরমিণকে দেখে রান্নাঘরে রান্না করতে। ভ্রুণটিকে রিমি নিজহাতে পাটোয়ারী বাড়ির বাগানেরর এক কোণে দাফন করেছে। রোজ সেখানে দুটো ঘণ্টা সে কাটায়। কিন্তু যখন সেখান থেকে উঠে সে। চলে আসে, সে টের পায় তার পেছন পেছন জয় আমিরের সন্তানও উঠে সঙ্গে আসছে। সে আজ বড় হয়ে গেছে। তার বয়স আড়াই বছর। সে রিমির সাথে সাথে ভুরভুর করে ঘুরে বেড়ায় সারা বাড়ি। বাপের বন্ধ কক্ষটা দেখে। সেখানে তার বাপের যুগ কাল কেটেছে, হয়ত দরজা খোলা পেলে গিয়ে দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো অভিভূত চোখে দেখতো। ওই কক্ষে তার মায়ের গন্ধও মিশে আছে। কিন্তু মা এই বাড়িতে কখনোই আসে না। কেবল তার পরিচয়টুকু সঙ্গে করে ছুটে বেড়াচ্ছে বিক্ষিপ্ত ফোটনের ন্যায়। এতসব বিভ্রমের ভিড়ে হামজাকে আলাদা করে দেবার মতো সময় রিমির হাতে থাকে না।
বহুদিন সে রাতে ঘুমায়নি। চোখের পাতা মিলিত করা খুব দুঃসাধ্য! বিরাট একটি মৃত বাড়িতে মৃত একটি পাপীর জীবিত লাশের পাশে ঘুমানো যায় না। তবু চুপচাপ শ্বাস আঁটকে ঘুমের ভান করার অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু দু’দিন আগে শেষরাতের দিকে তার সেই ভান ভেঙে হামজা ডেকে বলল,
-“এখানে পড়ে আছো কেন?ʼʼ
-“তো কোথায় যাব?ʼʼ
-“যাওয়ার জায়গা নেই বলে পড়ে আছো?ʼʼ
-“না। এটাই আমার ভাগ্য।ʼʼ
-“ভাগ্য বলতে কিছু হয় না, রিমি। চলে যাও।ʼʼ
-“কোথায় যাব?ʼʼ
-“দুনিয়াটা অনেক বড়।ʼʼ
-“আমার দুনিয়া খুব ছোট। তার বাইরে আমার কিছু নেই।ʼʼ
-“সে ছিল যখন আমি তোমায় ধরে রেখেছিলাম। আজ তুমি মুক্ত। তবু এখানে জোর করে পড়ে থেকো না। রিমি, তুমি কি করুণা করছো আমার ওপর?ʼʼ
–“জোর করে পড়ে আছি কে বলল? আপনি সুস্থ হোন, চলে যাব।ʼʼ
-“এটা যদি ভালোবাসা হয় তো ঠকে যাবে তুমি।ʼʼ
-“আর কী ঠকবো?ʼʼ
-“আমি সুস্থ হলে আবার পাপ করব। এবার আগের বারের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে সেসব পাপ।ʼʼ
-“তাহলে তো আমার উচিত নয় আপনার সেবা করা।ʼʼ
হামজা হেসে ফেলল, “সেটাই তো বলছি। ছেড়ে দাও।ʼʼ
-“পাপ করতেই জন্মেছেন?ʼʼ
-“আমি জানি না, রিমি। আমার জন্ম সম্বন্ধে আমার জানা-শোনা নেই। কেন জন্মেছি তা জানতে হলে জন্ম কোথায় এবং কাদের ঘরে নিয়েছি তা জানা জরুরী ছিল।ʼʼ
রিমির কঠোরতা অথবা নির্লিপ্ততা এখানে ফুরোয়। সে শাড়ির আঁচল ঠিক করে বুকে তুলে নিয়ে উঠে বসে।
-“আর কেন পাপ করবেন? কী কারণে, কোন উদ্দেশ্যে?ʼʼ
-“আমি কয়েকটা খুন করব, রিমি। একটু বিশৃঙ্খলা করব সমাজে আর আইনকে খুব নোংরাভাবে ভেঙে দেবার চেষ্টা করব।ʼʼ
-“পাগল হয়েছেন আপনি?ʼʼ
-“না। আমার মস্তিষ্ক এখনও ঠিক আছে।ʼʼ
-“আইন তো ভেঙেছেনই। আইন কবে মেনেছেন আপনি?ʼʼ
‘“না। আইনত বৈধ কাজ আমি করিনি ঠিকই, তবে আইনের ওপর আমার কখনোই বিদ্বেষ ছিল না।ʼʼ
-“এখন কেন জন্মেছে? আইন জয় আমিরকে মেরেছে তাই?ʼʼ
হামজা একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর অদ্ভুত-অলৌকিক সুরে বলল, “এইমাত্র জয় এসেছিল আমার শিয়রে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, একটু দুষ্টু হাসল, কয়েকবার ‘ভাই’ বলে ডাকল, কিন্তু আমি উঠলাম না, চোখ খুললাম না। ও যখন আস্তে কোরে রুম থেকে বেরিয়ে গেল আমি তখন চোখ খুলে তোমায় ডাকলাম।ʼʼ
রিমির গা শিউরে উঠল, শিরশির করে উঠল শরীর। হামজার বিশ্বাস স্বপ্নে যেদিন জয় এসে ডাকবে তাকে, তারপরদিন সে মারা যাবে। জয়ের সাথে মিলিত হবে আবার। সেই দিনের অপেক্ষায় সে অধীর। যদি তা-ই হয় তাহলে সুস্থ হয়ে আবার পাপ করার কথা বলছে কেন? কারণ সেই পাপগুলোও হবে জয়কে হত্যার প্রতিশোধমূলক। আর তারপর সে জয়ের ডাকে সারা দেবে। এজন্য আগে থেকেই রিমিকে চলে যেতে বলছে। রিমি দম আটকে বসে রইল অনেকক্ষণ। হামজা শুয়ে পড়ল আবার। রিমি বুঝতে পারে দিনদিন হামজার মানসিক অবস্থার ব্যাপক বিপর্যয় ঘটছে। তার মস্তিষ্ক আজও তার এত এত হারানো মেনে নিতে পারেনি। ক্ষমতা, সম্মান, হাতের মুঠোয় সমাজ ও জনতা, জয়…
রোজকার মতো আজও আনমনে, অপ্রকৃতস্থের মতোন ছাদের দিকে চেয়ে আছে। অধিকাংশ সময় এটাই তার কাজ। কোনো এক শূন্যে এমন নিথর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে, মৃত অথবা জীবিত শনাক্ত করা যায় না। রিমির অন্তরাত্মা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে তখন। রিমি বারান্দা থেকে ফিরে হামজাকে খাইয়ে, ওষুধ দিয়ে নিজেও শুয়ে পড়ল।
রাত দুটোর দিকে আচমকা জানালার কাঁচ ফুঁড়ে কিছু মেঝেতে পড়ে সেটাও ঝনঝন করে ভেঙে গেল। এক টুকরো কাঁচ ছুট্টে এসে হামজার শরীরে লেখে জখম তৈরি হলো। এরকম পরপর কয়েকটা আওয়াজ হলো। মেঝেতে তখন দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। রিমি উঠতে চাইলে হামজা ঝাপটে ধরে রাখে তাকে। আগলে নেয় নিজের আড়ালে। রিমি অস্থির হয়ে মৃদু কাঁপতে লাগল।
হামজা বলল, ককটেল ছুঁড়েছে। অ্যালকোহলে লাগা আগুন, নিভে যাবে খানিক পর। উঠো না। যেই থাকুক বাইরে, তারা চাইছে আমরা মেঝের মাঝ বরাবর যাই। আক্রমণ সহজ হোক।
রিমি কম্পিত কণ্ঠে বলল, কারা, কারা করছে এমন?
এ ধরণের কাজ করতে পারে, এমন লোকের তো অভাব রাখিনি আমি, রিমি। শান্ত হও, কিছু হবে না। আমি আছি।
রিমির বলতে ইচ্ছে করল, আপনি অসুস্থ। আপনাকে সামলাতে আমাকে লাগবে, আপনি কী করবেন? কাউকে প্রয়োজন এখন।
বলল না। তখনই সে টের পেল হামজার বুক থেকে তিরতির কোরে রক্ত ঝরছে। সে আবারও আৎকে উঠল। নিচতলার সিঁড়ি সংলগ্ন ফটকেও আওয়াজ হলো। অর্থাৎ আততায়ীরা ভেতরে ঢোকার প্রচেষ্টায় ত্রুটি করছে না। রিমি অস্থির হয়ে হামজার বুকে হাত চেপে ধরল, তার হাত ভিজে উঠল।
আপনি কি কিছুই করবেন না? রক্ত পড়ছে তো। বাইরে কারা থাকতে পারে?
কবীর হামজার কাছে আসে না। আজ অবধি হামজার সামনৃ আসেনি সে। মাঝেমধ্যে রিমির ডাকে আসে, রিমির সঙ্গে কথা বলে ফিরে যায়। হামজাকে চোখের দেখাটুকু অবধি দেখার প্রবণতা তার নেই। তবু রিমি তাকেই কল করল। কিন্তু কবীর তার ছেলেদেরকে নিয়ে পাটোয়ারী বাড়িতে পৌঁছানোর আগেই প্রায় ঘণ্টাখানেকের তাণ্ডব শেষ করে বাপ্পী লোকজন নিয়ে চলে যায়। খুব কৌশলে। বহুদিন আগেই তারা পাটোয়ারী বাড়ির দূর্গঘেরা উঁচু সুরক্ষিত প্রাচীর টপকে ভেতরে আসার ব্যবস্থা করে নিয়েছে।
সেই ঘটনা মাহেজাবিণ জানল না। পরদিন বিকেলের পর দোলন সাহেবের কাছ থেকে ফেরার পথে সন্ধ্যা নেমে এলো। দোলন সাহেবের বাসা থেকে বাঁশেরহাট ফেরার পথে মাঝে সুইহারী খ্রিষ্ট আশ্রম পড়ে। তার আগেই মাহেজাবিণ টের পেল তার চেনা-অচেনা কয়েকজন লোক তাকে অনুসরণ করছে। এটা প্রথম নয়। বিগত দিনগুলোতে বাইরে বেরোবার পর সে কখনোই আশা রাখেনি আবার জীবিত হালে বাড়ি ফিরবে। বহুবার জানের ঝুঁকি তাকে ছুঁয়েও পাশ কাটিয়ে গেছে। সেদিন সেটা তীব্র হলো।
মাহেজাবিণ এখন রাস্তা পাড় হতে শিখেছে। কারণ আব্বু নেই এখন তার হাতটা ধরে রাস্তা পাড় করবার জন্য, কিন্তু তার পথ ফুরোয়নি। তা বরং দূর্গম হয়েছে।
রাস্তা পাড় হয়ে দ্রুত রিক্সা তো ধরল সে, কিন্তু লোকগুলো এসে রিক্সাওয়ালাকে থামিয়ে বলল, যাত্রী নামায়ে দ্যান, মামা। ওয় আর যাইতো না।
রিক্সাওয়ালা একটু ইতস্তত করেছিল বটে, কিন্তু সে সচেতন নাগরিক। যারা তাকে কথাটা বলছে, তাদের কথা শোনাটাই বুদ্ধিমানের বৈশিষ্ট্য। মাহেজাবিণ নিজে থেকেই নেমে দ্রুত পা চালাতে লাগল। এক পর্যায়ে সে দৌড়াতে লাগল। শীতের সন্ধ্যা, তবু বোরকার নিচে শরীর ঘেমে চুপচুপে হয়ে উঠল। কিন্তু পেছনের লোকগুলো তাকে বেশিদূর দৌঁড়াতে দেবে না বলে একখানা চাপ্পর ঠিক ডান পা তাক করে ছুঁড়ল। পায়ের কব্জার ওপরের এক দলা মাংসপেশি আলগা করে নিয়ে চাপ্পর পড়ে যায় মাটিতে, সাথে মাহেজাবিণও। আশপাশটা ফাঁকা, কেউ থাকলেও তাকে রক্ষা করতে আসার বেকুবি কেউ করবে না। জনগন বরাবরই সচেতন। মাহেজাবিণের সাথে সেদিন ভয়াবহ কিছু ঘটার ছিল।
মাহেজাবিণ রক্তাক্ত পা নিয়ে আবার দৌঁড়ায়। বিশেষ লাভ হবার নয়। তাকে ধরে ফেলল বাপ্পী। বাপ্পী সেই কালেই হামজার কাছে জয়ের বউকে আবদার করেছিল। অর্থাৎ শুধু জানের বদলে জান নয়, তারা আরও কিছু চায়। মাহেজাবিণ আবার মাটিতে পড়ে গেলে বাপ্পী এলোপাথারি মুখে, বুকে, মাথায় লাত্থি মারতে লাগল। মাহেজাবিণের ঠোট-মুখ ফেটে রক্ত ছুটে এলো। তার নেকাব আবারও সেদিন খুলে ফেলা হলো এলোমেলো আঘাতে বোরকা ছিঁড়ে গেল খানিকটা। বাপ্পী মাহেজাবিণের গলার ওপর পাড়া মেরে উঠে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।
মাহেজাবিণ অস্ত্রহীন, ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় প্রায় অজ্ঞান হবার আগে তার চেতনা তাকে সতর্ক করে। আজ তার সত্যি সত্যি ইজ্জত হারা হওয়া লাগতে পারে। তার কীভাবে নিজেকে তুলে নিয়ে তাদের হটিয়ে রক্তাক্ত শরীরটা কোনোরকম টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল সুইহারী চার্চের আশ্রমে। সে জেনে প্রবেশ করেনি সেখানে, কিন্তু ঢুকে পড়েছিল একটি আশ্রয়কেন্দ্রে। আর কিছু মনে নেই তার।
যখন তার আবার চেতনা ফিরল, সে চোখের সামনে দেখতে পেল একজন ব্রতী খ্রিষ্টান সিস্টারকে। সিস্টার মেরি ক্যাথারিন। প্রায় মাসখানেক মাহেজাবিণ সেখানে সিস্টার ক্যাথারিনের সেবায় থেকেছে। একসামে এক লক্ষের অধিক প্রশ্ন ও কৌতূহল ক্যাথারিন জমিয়েছিলেন এক অজ্ঞাত যুবতী নারীকে নিয়ে। মাহেজাবিণ জবাব দেয়নি। সে বলছিল বলবে কখনও। সিস্টার ক্যাথারিনকে সে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিল।
এর মাঝে হামজা অসংখ্য সংবাদ পাঠায় তার কাছে। হামজারর আন্দাজশক্তি তার চূড়ান্ত অসুস্থতারও ঊর্ধ্বে। সে নিজের ওপর হওয়া হামলার সেই রাতেই আন্দাজ করেছিল এরপর আরমিণের পালা। এরপর সে পরদিন জানতে পারল আরমিণ নিখোঁজ। মাহেজাবিণ গোটা একমাস পুরো চেনা জগত থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছে। মার্জিয়া কেঁদে কেঁদে পাগল হয়েছে। কোনো খবর নেই, জানা নেই মাহেজাবিণ কোথায়! তখনও মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত, জয় আমিরের বলাৎকার স্ত্রী। সে নিখোঁজ। কোন চিল-শকুনে টেনে ছিঁড়ে খেয়েছে! ওই হদিস আর পাওয়া যায়!
রিমি সেবার প্রথম পাটোয়ারী বাড়ির সীমানা ছেঁড়ে বেরিয়ে বারবার আমজাদ সাহেবের কুটুরিতে যাতায়াত করেছে। রূপকথার সঙ্গে কথা বলে চলে আসতে হয়েছে। রূপকথার দৃঢ় বিশ্বাস সকলকে বিশ্বাস জুগিয়েছে, মাহেজাবিণ ফিরে আসবে। ওই মেয়ে ফুরোতে পারে না। তার জীবন যেসব ঝড়ে টালমাতাল হয়েও আজও বহমান, সে হুট করে এভাবে ফুরিয়ে যাবে না।
হামজা ওই মাসখানেকের সময়টাতে আরমিণের খোঁজে চরম ব্যস্ত হয়েছিল। কেননা বাপ্পীর ধারণা হামজাকে জয়ের বউ এবং জয়ের বউকে হামজা–দুজন দুজনকে টিকিয়ে রেখেছে। দুজন মিলে এমপিকে ধ্বংস করে ছেড়েছে। দুজন এক। সুতরাং দুজন চিরবিরোধী দুশমন ঘটনাক্রমে এক বাপ্পীর দুশমন হয়ে ওঠার ব্যাপারটিতে হামজা হেসেওছিল। সে নিজেও চিন্তিত হয়ে উঠেছিল বিরোধী নারীর এভাবে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায়।
মাসখানেক পর কিছুটা সুস্থ হয়ে খোঁড়া পায়ে মাহেজাবিণ বাড়ি ফিরল। তার পরদিনই হামজার লোক এলো মাহেজাবিণের কাছে। মাহেজাবিণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে এটা বুঝে যে তাকে এখন অবধি হামজা নজরে রেখেছে। এই লুকোচুরি খেলার শেষ কোথায়? হামজা তাকে একপাক পাটোয়ারী বাড়িতে ডেকেছে, কিছু আলাপ-আলোচনা করার আছে বলে।
তার জবাবে মাহেজাবিণ ক্লান্ত হাতে একখানা ছোট্ট চিঠি লিখেছিল কেবল,
•
আপনার সঙ্গে আমার কোনো আলাপ-আলোচনা থাকতে পারে না। শেষবার যেখানে দেখা হয়েছিল, আমি আশা রাখি আবার দেখাটা আমার-আপনার সেখানেই হবে। সেদিন আপনার বিপক্ষের আইনজীবী হিসেবে আমি থাকলে খুব অবাক না হবার পরামর্শ থাকবে আমার। এবং কথাও সেখানেই হবে। আপনি আসামী এবং আমি প্রসিকিউটর হিসেবে অনেক কথাই হবে আশাকরি। খুব শীঘ্রই। ততদিন অপেক্ষা করুন। এবং যথাসম্ভব সুস্থ হোন। আপনার সুস্থতা একান্ত কাম্য।
পুনশ্চ: রিমিকে আমার অনুরাগ জানাবেন। সে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে, দেখা হয়নি। তাকে আসতে বলবেন। আমি আর কখনও পাটোয়ারী বাড়িতে পা রাখব না, তা বলে তার সঙ্গে আমার পরিচয় ফুরোবে না।
•
এরপর গুনে গুনে কেটে গেল মাঝখানে কমবেশি তিনটে মাস। হঠাৎ-ই একদিন—২৯ জুন বিকেলে মাহেজাবিণের ঠিকানায় এসে পৌঁছালেন সিস্টার ক্যাথারিন মাহেজাবিণের জীবনে আসা অবরুদ্ধ নিশীথগুলোয বিবরণ শুনতে। মাহেজাবিণের ল শেষ হতে তখন খুব বেশি দেরি নেই। আর কিছুদিন। এরপর বার কাউন্সিল পরীক্ষা, সেখানে উত্তীর্ণ হলে সে একজন আইনজীবী। অ্যাডভোকেট মাহেজাবিণ আমির।
সিস্টার ক্যাথারিন অতীত শুনতে শুনতে গোটা একটা রাত, তারপরেও একটি দিন অবধি মাহেজাবিণের কাছে কাটিয়ে গেছিলেন। সাথে প্রতিশ্রুতি নিয়ে গেছিলেন খুব শীঘ্রই একটাবার পাটোয়ারী বাড়িতে মাহেজাবিণকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যেতে চান। মাহেজাবিণ যেতে না চাইলেও জোরপূর্বক নিয়ে যেতে চান। জয় আমিরের ফটো দেখতে চান, হামজার অবস্থা তিনি সচক্ষে দেখতে চান। তার নিষ্পাপ বধূ, রিমিকে দেখতে চান।
কিন্তু পরিকল্পনা করাটাই উচিত নয় জীবনে। সেদিনের পাঁচ মাস পর মাহেজাবিণ খবর পেল সুইহারী মঠের একজন সিস্টার মেরি ক্যাথারিন মৃত্যুবরণ করেছেন। মাহেজাবিণ গিয়েছিল দেখতে। তখন আর মাহেজাবিণের কাছে পাটোয়ারী বাড়ি দেখার আবদার করা ব্রতী নারীটিও জীবিত নেই। তাঁর আবদারে আরেকটিবার হয়ত মাহেজাবিণ পাটোয়ারী বাড়িতে, এবং অভিশপ্ত আমির নিবাসে কদম রাখতো। তা আর হয়নি।
সিস্টার ক্যাথারিন কেবল মঠে শিক্ষাদানের কাজই নয়, তিনি হাসপাতাল এবং আশ্রমগুলোতে অসুস্থদের সেবায় নিয়জিত ব্রতী ছিলেন। তার কাছেই গোপন রয়ে গেল মাহেজাবিণ এক জীবনের বিবরণ।
এরপর আরেকটি বছর কেটে গেল সেইদিন থেকেও— যেদিন মাহেজাবিণ নিজের দূর্গম জীবনের অতীতের পাতাগুলো মেলে ধরেছিল এক সংসারহীন নারীর কাছে। আজ আবার ২৯ জুন কিন্তু খ্রিস্টাব্দ ২০১৯। আজ সে একজন প্রাকটিসিং অ্যাডভোকেট। এই তারিখটি একটু অদ্ভুত। জয় আমিরের জন্মদিন এটি। এ বছর ৩২তম জন্মদিন। লোকটা জন্মদিনের হিসেবে মাহেজাবিণের কাছে কয়েকটি জিনিস গচ্ছিত রেখে গেছে। ৭৫তম জন্মদিন অবধি উল্লেখ করেছে সেগুলো রেখে দিতে। এবং সেই হিসেবের সাথে একটি রক্তমাখা ঘড়ি রেখে গেছে, যেটি বের করতে হলে একটি কাগজ টান করতে হয়। সেই কাগজটিতে জয় আমির কিছু হিজিবিজি লিখে রেখে গেছে। এইসব তারিখগুলোতে ঘড়িখানা হাতে নেবার পর মাহেজাবিণ কাগজখানা নাড়তে-চাড়তেই দু’একবার চোখ বুলায়। চোখ বুলাতে গেলে একবার পড়ে ফেলে—
•
আমি না মরলে এই কাগজ তোমার পাবার কথা না। আচ্ছা, আমি কি শালা বুড়া হয়ে মরছি? বয়স কত হইছিল? দুই-চাইরটা বাচ্চা-কাচ্চা হইছিল তোমার-আমার? হাসি পেয়ে যাচ্ছে লিখতে বসে। জীবনে ভাবি নাই মরার আগে কোনোদিন এইসব ঢং করে মরা লাগবে।
তো কেমন কাটে দিনকাল? সব ঠিকঠাক? এখন আমি নাই, আমার পাপ নাই। সুখ আছে, সুখ?
সুখ কী, জানো? পাখি। শালার পাখিদের আবার রীতি-নীতি অন্যজাতের। তুমি যেই পাখিরে খাঁচায় পুষতে চাইবা, ওই শালা জীবনেও আপন হবে না। সুযোগ পাইলেই উড়াল মারবে, ফিরে তাকাবে না। সহজ না, ম্যাডাম। আপনার জীবন খুব কঠিন হবে। আপনি আইনজীবী হবেন, হন। তাই বলে আমার মতোন জয় আমিরদের বিপক্ষের হইয়েন না।এক জয় আমিরের বিপক্ষে গেলেন, আপনি তার হয়ে গেলেন। আবার কোন শালার বিপক্ষে যাবেন, সেই শালায়..
নাহ্, বিপক্ষে গিয়ে একবার দেখলেন তো, কী হয় এই পথে! আপনি পথিক ভালো, কিন্তু আপনার পথ না। এই দুনিয়া আপনার নীতিবোধ কেড়ে নিয়ে আপনাকে পরী থেকে শয়তান বানাতে সর্বদা সচেষ্ট।
হার্ভি ডেন্ট বলেছিল–
You either die a hero or live long enough to see yourself become the villain.
-হয় তুমি নায়ক হিসেবে মৃত্যুবরণ করো, নয়ত বেঁচে থাকো নিজেকে একসময় খলনায়ক হয়ে যেতে দেখার জন্য!
আমি মরলাম না। বেঁচে রইলাম। সেদিন মরলে কী হতো জানো? সর্বহারা এক ত্যাগী নায়ক, নিষ্পাপ জয় আমির হিসেবে মরে যেতাম। কিন্তু বেঁচে থাকতে গিয়ে আমি নিজেকে তোমার মতো নীতিবানদের চোখে ঘৃণিত এক পাপীষ্ঠ হয়ে যেতে দেখলাম। কিন্তু আমি থামালাম না নিজেকে। আমার মন চাইল না। কারণ আমি ততদিনে শিখে গেছি মানুষেরা বাঁচে না, বেঁচে থাকতে হলে অমানুষ হতে হবে। যে রাজনীতির দায়ে আমি বাপ হারাইছি, মারে নষ্ট হয়ে মরতে দেখছি, দাদার মাথা গলা থেকে আলাদা দেখে চাচার কোলে চড়ে নিজের পরিচয় থুয়ে বাইর হয়ে আসছি পথে, যেই পথে খালি খিদে। নিজের পেটে খিদে, পথের খিদে, পথের পথিকদের খিদে…
এই পথে রোজ আমার মতো জয় আমিরেরা পয়দা হয়, কিন্তু শালা দুনিয়ার কিচ্ছু যায়-আসে না। রোজ খবরের পাতায় মানুষ আমার মতোন জয় আমিরদের সব হারানোর গল্প পড়ে, তারপর চশমাটা খুলে দুটো দীর্ঘশ্বাস ফেলে খবরের কাগজটা সরিয়ে রাখলেই শেষ। আমরা ইনসাফ পেলাম কিনা, এক ম্যাচ রাজনীতির খেলায় সব হারানো আমরা কীভাবে বাঁচব, খিদের জ্বালায় কোন পথে একমুঠ ভাত খেয়ে বেড়ে উঠব, কী শিক্ষা পাব তা সমাজের দেখার সময় হলো না।
কিন্তু যখন কিছুকাল পর এই আমরা জয় আমির হয়ে সমাজের সামনে হুমকি হিসেবে দাঁড়াই, তারা তখন ভাবে এই অমানবিকেরা কারা? এদের নীতিজ্ঞান নেই কেন, মনুষ্যত্ব কোথায়? এদের জন্ম কীভাবে হলো? এরা এত ক্ষুধার্ত, ছিঃ! ভালো শিক্ষা পায়নি কেন?
তুমিও হবে, হয়েছও খানিকটা, আরও হবে। তুমি আর নীতিবান নেই। তোমার ভেতরে নমনীয়তা ফুরিয়ে আসছে। তুমি একসময় ক্ষমা করতে ভুলে যাবে। তুমি শিখে যাবে বাঁচতে হলে কঠোর হতে হয়, স্বার্থপর আর ক্ষমতাপরায়ন হতে হয়, মাফ করতে ভুলে যেতে হয়। বুকে সব হারানোর ব্যথা দমিয়ে রেখে বেশিক্ষণ অহিংসার বুলি ছাড়া খুব কঠিন, জুনিয়র। চট করে নীতির সুঁতো ছিঁড়ে প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। তখন মানুষ আর মানবিক থাকে না, জয় আমির হয়ে যায়। তুমিও ধীরে ধীরে জয় আমির হয়ে যেতে পারো। মানুষ তখন তোমার নিষ্ঠুরতায় ভয় পাবে, রেগে যাবে মনে মনে। মানুষ ব্যথা পেতে পেতে যেদিন ব্যথা সওয়ার ক্ষমতা লাভ করে, সেদিন থেকে সে মানুষের ব্যথা অনুভব করার ক্ষমতা হারায়। যা নীতিবানদের চোখে অমানবিকতা।
শোনো জুনিয়র,
তুমি ভাবো তুমি অন্যায় দেখে, অন্যায় সয়েও সৎ থাকতে পারবে। তুমি ভুল। দুনিয়া ভালো না। আমার অভিজ্ঞতা বেশি। একটা যুক্তিহীন সত্যি শোনো–সৎপথ মানুষকে অসৎ বানায়। সৎ থেকে তুমি শুধু হারাবে। তাতে তুমি সততার ওপর বিশ্বাস হারাবে, দ্বিধায় পড়বে, তারপর তুমি সৎ-অসৎ এর পার্থক্য ভুলে যাবে। কারণ ওই যে বললাম–বুকের হাহাকার নীতির চাইতে বেশি শক্তিশালী, মানুষের বিবেক ধ্বংস করতে ওর একবার নড়ে ওঠাই যথেষ্ট। নিজের ভাগ্য নিজেকে লিখতে হয়। আর তারপর সেই ভাগ্যলেখক ছোটে মানুষের ভাগ্য নষ্ট করতে। এটা নীতি—
এসব আমার নীতি। তোমার সাথে মিলবে না বোধহয়। আমাদের বড়ঘরে এক বিপ্লবী আছে, তোমার তার সাথে দেখা হবে না। তার সাথে মেলে নাই। সে আমার মতো খলনায়ক হয় নাই, সে বিপ্লবী হয়েছে। তুমিও হয়ত সেই পথেই যাবে। কারণ তোমরা এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে অন্ধকারকে গ্রহণ করেছ, আমি অন্ধকারে জন্মেছি, আমি অন্ধকারে গড়ে উঠেছি।
এক পাশের পৃষ্ঠা শেষ। এবার আরও ছোট ছোট অক্ষরে লেখা লাগবে। কতদিন পর এতখানি বাংলা লিখলাম, হাত কাঁপতেছে। বাতাসে পৃষ্ঠা উড়তেছে খুব, আরও সমস্যা। আমি এখন কোথায় জানো? একুশ তলার ছাদের ওপর পা ঝুলায়ে বসে আছি। খাতা কোলের ওপর, মোবাইল গালে ধরে ফ্ল্যাশ অন করে লিখতেছি। বিল্ডিংটা পলাশের চাচার। ওই ভ্যাড়াচ্চুদারে মারছি আধঘণ্টাখানেক হবে। জানটা দিলো একটা ভুলভাল আবদারে।
তোমাকে সেবার দেখলাম ভার্সিটির মাঠে, অন্তিকের বোন। এনাফ জুনিয়র এক চেংরি। শালী আমারে পাত্তাই দিলো না! হামজা ভাইরে বলি নাই। ছোট্ট এক জুনিয়র মেয়ে আমার সাথে এতবড় দুঃসাহস দেখায়ে চলে গেল, তা কাউকে বলা যায় না। যা কাউকে বলা যায় না, তা কোদাল হয়ে মন খুঁড়তে থাকে, বুঝলে? আমি সেই রাতে আড়াই বোতল মাল এক চুমুকে শ্যাষ করে একেবারে বেহেড হইছি। এরপর রাতে স্বপ্নে দেখলাম, তোমার সাথে ঘুরতে গেছি, এক মরুভূমিতে। এত মাল খেয়ে ঘুমাইছি, তাও শালা স্বপ্নে মরার পিপাসা পাইল। তুমি গেছো পানি খুঁজতে। কিন্তু পানি পাওয়ার আগেই এক ধুলিঝড়…
আর তোমার খোঁজ নাই। তুমি ধুলিঝড়ে তছনছ। আমি পিপাসা নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। ফজরের আজান হচ্ছে তখন। জ্বর আসল সেদিন সকালে আমার।
এক সাক্ষাতে এইরকম মারাত্মক স্বপ্ন যে চেংরিরে নিয়ে দেখা যায়, তার পিছু ছাড়া যায় না। কিন্তু বিশ্বাস করো জুনিয়র, আমার কোনো প্ল্যান ছিল না তোমারে বিয়ে করার। ছেহ্! প্রশ্নই ওঠে না। আমার বিয়ে করার কথাই ছিল না। অন্তত তোমার মতো সাদা পায়রারে। করলে তরুরে করা লাগতো মনেহয়, হামজা ভাইয়ের ইচ্ছায়। তোমার জন্যে জয় আমির না। জয় আমিরদের জন্যে কখনোই তোমাদেরকে বানানো হয় না। সব অপরিকল্পনায় হয়ে গেছে। কসম আমি বিশ্বাসই করি নাই আরমিণরে আমি বিয়ে করছি। এইজন্যে নিজেরে মানাইতে দুই-তিনদিন তোমার বাপের বাড়িতে তোমারে দেখতেও গেছিলাম সত্যিই এই ধরণের ঘটনা ঘটে গেছে কিনা!
তো যা বলার জন্যে এই বাল লিখতে বসা। অপরিকল্পিতভাবে যে অঘটন ঘটে গেল, তার আবার একটা শর্ত বাকি রয়ে গেছে। আমার-তোমার বিয়ে ইসলামমতে হইছে। ওইখানে দেনমোহরের কথা উঠছিল। আমি জানতাম ছাড়ার সময় এইটা দেয়া লাগে। কিন্তু কাজী শালা বলল, এইটা তোমার হক। আদায় করে দিলাম।
তোমার দেনমোহর শোধ। তো এখন কী? আমার সব ছোঁয়া ভুলে যাবা? মানুষ কিছু দিয়ে মূল্য না পাইলে তা আজীবন মনে রাখে, মূল্য পরিশোধ হইলে দেনাপাওয়া শেষ, সাথে স্মৃতিও। না, তুমি নিজেরে বিক্রি করো নাই। আবার কোনোদিন আমার নামেও করবা না, এইটা নিশ্চিত। চাইলাম না তোমারে। যাও! তোমারে চাইলে ওইটা আরেক পাপ। কম নাই আমার পাপ জীবনে, আরেকটা বাড়ালাম না, তাতে কী হবে? তোমারে চাইলে আমার পাপে ভাঁটা পড়ার প্রবল সম্ভাবনা। পাপ আমি ছাড়ব না, তোমারে আমি চাইব না!
তোমার বাপের জমি বিক্রি করা বারোলক্ষ টাকা আমার একাউন্টে থাকল। আর যা ঋণ ছিল তোমার আব্বার, ওইটা আমি শোধ করে দিসি। দেনমোহর ধরো দুইলাখ বেশি দিলাম। আমার জানা নাই নির্ধারিত এমাউন্টের বেশি দিলে সমস্যা আছে নাকি। থাকলে থাকল। স্বামী হিসেবে কিছু দিলে সমস্যা থাকার কথা না। না স্বামী না, আসামী। লেখা কাটলে সৌন্দর্য নষ্ট হয়। তাই কাটব না। তুমি স্বামী না পড়ে আসামী পড়ো।
শোনো, যে টাকা জমা থাকল ওইটা যদি আমার দেয়া দেনমোহর হিসাবে খরচ নাও করো তো তোমার বাপের জমি বেচা টাকা হিসেবে খরচা কোরো। মনে করবা আমি দেই নাই, তোমার বাপ দিছে। টাকা ছাড়া এক পাও চলতে পারবে না। উকিল হবার জন্যে ভালো রকম টাকা লাগবে। ঘটনা হইল আপনার মতো উকিল খুব দরকার, ম্যাডাম। তাইলে হয়ত আমার মতো জয় আমিরেরা মায়ের লাশ দেখিয়ে আপনার কাছে অপরাধীর শাস্তি আশা করতে পারবে, অপরাধীকে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখে তাদের আগুন নিভবে, আমার মতো পাপী তৈরি হবে না আরেকটা! কিন্তু ঘটনা হলো উকিল হিসেবে সবাই আপনাকে দেখবে, আমি বাদে। এইটা অবশ্য ভালোও। আমার মতো আইনবিদ্বেষী পাপীর ঘরওয়ালি আইনজীবী, বিষয়টা বেমানান। আপনি যখন উকিল হবেন ততদিন আমি থাকব না বোধহয়—
আমি আর বাঁচব না বেশিদিন। খুব অল্প সময় আছে আমার। এই দিনগুলোতে আমি মাত্রহীন পাপ করব। তোমার ঘেন্না আরও বাড়বে। তারপর যদি বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকি তো ক্যান্সারে মরব। নাহলে গুলি খেয়ে। আমি মরার পর আমিরদের একটা উত্তরাধিকারী দরকার। তাই মরার আগে জিন্নাহ্কে খুঁজে বের করার কাজটা বাকি। আর ওকে খুঁজতেই খুব ভয়াবহ কিছু পাপ করা লাগবে আমার। এরপর শেষ। পাপ থামাতে হলে পাপীকে মরে যেতে হয়। এমনিতেও রক্তের অবস্থা খারাপ। ব্লাড-সেলের পেছন মারা গেছে, বোন-ম্যারো ড্যামেজ। বেদম মাইর খাওয়ার পর কোনো বার ঠিকমতো চিকিৎসা করা হয় নাই, ক্যান্সার না হইলে আমি অলৌকিক মানুষ হয়ে যাইতাম। ম্যালা সমস্যা শরীরে। এখনও মাংসের ভেতরে কামড়াচ্ছে। শরীর ভালো না। জ্বর আসবে মনেহয়।
জীবনে ভালো আমি হইতে পারতাম। হইলাম না কেন জানা নাই। আমির পরিবারে বড়বাবা ছাড়া কেউ আমার মতোন ছিল না। সবচাইতে বড় দ্বন্দ্ব কোথায় লাগছে জানো? আমি পাপ করতে না চাইলে দুনিয়া ছাড়তে হবে, আর বেঁচে থাকলে আমি পাপ ছাড়ব না। আমার কাছে পাপের কারণ নাই। কিন্তু খুন আবার মদের মতোন। প্রথমবার জোশে এক ঢোক গিললে পরেরবার নেশায় এক বোতল লাগে। এরপর হাতের বাঁধন ছুটে গেলে আর বিবেক কাজ করে না। আর আমি তো রক্তে অভ্যস্ত খুব ছোটকালে। আমার কাছে পাপ পাপ না। আমি পাপ-পূণ্য বুঝি না।
তো ঘেন্না-টেন্না করো তো এখনও নাকি! বেশি করার দরকার নাই। আমার ইগোতে লাগবে। তবে শেষ হওয়া যাবে না কিন্তু! ওইটুকু আমার। আর কিছু নাই তোমার কাছে আমাকে দেবার মতোন। তুমি নিজেই কাঙাল। কিচ্ছু নাই আমার জন্য তোমার কাছে। তোমার ওই ঘৃণাটুকু আমার থাকলে ক্ষতি নাই। আমি নিজে এই জীবনে আমার থেকে পরিবার কেড়ে নেয়া আসামীদের ক্ষমা করি নাই, তুমিও কোরো না। এইখানে আমার-তোমার নীতির মিল থাক।
পৃষ্ঠা শেষের দিকে। হাতও কাঁপতেছে খুব। এই কাগজ যখন পাবে তুমি, আমি তখন বহুদূর। এই পাপের জনমে আর দেখা হবে না তোমার সাথে। তোমার চোখে ঘেন্না দেখার সুযোগটুকু হারিয়ে আমি পালাব। আমার তীর্থযাত্রা খুব সামনে। এখন একটা গান মনে পড়তেছে–
আমি মরে গেলে জানি তুমি কাঁদবে না,
ওখানেই শেষ করে দিও…
চাইব না কিছুই তো আর,
শুধু… মনে রেখো কোনো একদিন…….
পৃষ্ঠা শেষ। আর এক লাইন লেখা যাবে। তো–
বিদায় আমার পাপী জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত মেহমান, আমার ঘরের দুশমন। জয় বাংলা…
●
কাগজ ফুরোয় এখানে। শেষের দিকের লেখাগুলো ক্রমান্বয়ে ছোট হয়েছে। লেখার ধাঁচে এলোমেলো ভাব এসেছে।
এই বছর কয়েকে কাগজখানা মাহেজাবিণ মোট ছয়বার পড়েছে। প্রথম যেদিন পড়েছিল, দুবার। এরপর তারিখ এলে পড়া হয়। এর একটা কারণ আছে। প্রত্যেকবার কাগজখানা পড়ার পর সেও ফিরতি কিছু লেখে। এবারেও একখানা কাগজ তুলে নিয়ে লিখতে বসল—
•
জয় আমির,
আপনার কাগজখানা যখন আমি পেয়েছি, তার অনেক আগেই আপনাকেসহ আমি ক্ষমা করে দিয়েছি আমার সকল অন্যায়কারীকে। আমার-আপনার পথ কখনোই এক ছিল না। আপনি ধারণা করতেন, পরিস্থিতি মানুষকে খারাপ বানায়, আমাকেও জয় আমির বানিয়ে তুলবে। নাহ্ আমি আপনার মতো কাফের হয়ে জন্মাইনি। আমি আজও এক সৃষ্টিকর্তায় ভরসা রাখি যিনি আপনার হাল এমন করেছিলেন যে আপনার শত্রুরাও কেঁদেছে আপনার পরিণতিতে। যিনি আপনার গুরুর পরিণতি এমন করে রেখেছেন যা দেখে আমি অবধি তার পরিণতির ওপর সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছি। সেই আল্লাহ্ তায়ালাতে এতকিছুর পরেও আমি অটল বিশ্বাস ও ভরসা রাখি। আপনার আশা আমায় নিয়ে ভুল ছিল।
পরিস্থিতি মানুষকে জয় আমির বানায়, এটা সঠিক তখন, যখন মানুষটার ভেতরে আপনার মতো স্বার্থপরায়নতা রয়েছে। ঈমানদার কখনোই স্বার্থের ভিত্তিতে ধর্ম ও মানবিকতা পালন করে না। সর্বাবস্থায় এক আল্লাহ্ ও মানবিকতার ওপর কায়েম থাকাটাই ঈমান। আপনার মতো নড়বড়ে ঈমানদার আর স্বার্থপর এমনিতেও ভালো মানুষ হয় না পৃথিবীতে।
মাকে ধর্ষিতা হতে দেখলেন, দু’চারবার আল্লাহ্কে ডাকলেন, তিনি সাড়া দিলেন না, আপনার কাছে হয়ে গেল সেই মহান সত্ত্বা অস্থিত্বহীন! বাঃ রে! ঈমান তো হাতের মোয়া নয়। মুরসালীন মহানকে তো দেখেছেন! হাজার ফোঁটা রক্তেও একই দৃঢ়তা, একই বিশ্বাস! আপনি ঈমানদারদের ইতিহাস জানেন না। তাঁরা চূড়ান্ত বর্বরতার সামনেও সেই এক রবের সাক্ষ্য দিয়ে প্রাণ হারায় হাসতে হাসতে। আপনি তাদেরকে জানলে নিজেকে অবশ্যই একজন মুসলমানের ঘরের সন্তান হিসেবে ধিক্কার দিতেন।
আপনি জন্মেইছিলেন অবিশ্বাসী হয়ে, পরিস্থিতির দোষ দিয়ে গা বাঁচাতে চাইলে ওটা আমার কাছে অগ্রহণযোগ্য। আপনি প্রতিশোধের কথা বলেছেন, মেনে নিলাম যান। যারা আপনার সঙ্গে অন্যায় করেছিল তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। তারা সংখ্যায় কয়জন? অথচ আপনার হাত শত মানুষের রক্তে রাঙা। ওগুলো কী ছিল? কীসের প্রতিশোধ ছিল, নিরীহ, নিষ্পাপ প্রাণগুলোর অপরাধ কী ছিল? আমি জানতাম আপনার চিন্তাধারা অসুস্থ, এজন্য কোনোদিন বোঝাতেই যাইনি, রুচি পাইনি আপনাকে খুলে বোঝানোর। কারণ আপনি আপনার এই গোজামিল তত্ত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী। এটা বুঝেই আপনার একমাত্র শাস্তি নির্ধারণ করেছিলাম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।
আজ মনেহয় আপনি থাকলে আমি আলোচনায় বসতাম একদফা আপনার সঙ্গে। অনেক কথা বলার বাকি রেখেই আপনি চলে গেলেন। আমার ভেতরের বহুকথা আপনার না শোনা রয়ে গেছে। আবার কখনও সামনে এসে দাঁড়ালে বলব। কিন্তু ফিরে যদি আমাকে আমার স্থানে না পান, এই কাগজগুলো দেখে নেবেন।
আপনি আমার চোখের ঘেন্নায় খুব অভ্যস্ত আর আগ্রহীও! অথচ আপনি জানেননি ঘেন্না ছাড়া সামান্য পরিমাণ কৃতজ্ঞতাও ছিল সেখানে। একদিন আপনি আমার ইজ্জত বাঁচালেন, এক খু-খার অমানুষের সাথে একটুখানি শত্রুতা করলেন, আব্বুকে কাধে তুলে বয়ে নিয়ে এলেন। এরপর খানিকটা কৃতজ্ঞতা জমতে পারে না আমার ভেতরে? আপত্তি কোথায়? অনেকখানি কৃতজ্ঞতা জমিয়ে রেখেছিলাম আপনার জন্য। কিন্তু সেটুকু নিবেদনের সুযোগ না পাওয়ার ব্যথার গভীরতা আপনি মাপতে পারবেন না। আপনি তার আগেই আমাকে মেরে ফেললেন। খুব নিষ্ঠুর রকম মৃত্যু। সামান্য ছাড় দিলেন না। আমি কেন দেব? কেন? আপনি যদি থুতুর যোগ্য হয়ে সামান্য থুতু বরদাস্ত না করতে পারেন, আমি কেন এতকিছু বরদাস্ত করে আপনাকে ছাড় দেব?
আমার এই জীবনের দায় কার? আজও রাস্তায় বেরোলে গুঞ্জন শুনতে পাই জয় আমিরের বউ যায়। অথচ আমার কোথাও আপনি নেই। আপনি এই জগতের কোথাও নেই যেখানে গিয়ে আমি আপনার বিশাল বড় কলিজাটা ছিঁড়ে এনে আমার কলিজার আগুন নেভাতে পারি। আমার ভেতরে প্রতিমুহুর্তে আপনাকে সামনে রেখে হাজারও আলাপ পাড়ার জেদ ওঠে। কিন্তু আপনি নেই। কেন? আপনি নরক স্বীকার করে পাপ করলেন, আমার জীবনটা নরক করে সেখানে পৌঁছালেন।
কারণ আপনি জয় আমির হিংসুটে। আপনি ঠিক গুনে গুনে আপনার জীবনের সকল বৈশিষ্ট্য আমাকে দিয়ে গেছেন, যা আপনি বয়ে গেছেন। আমি আজ ঠিক আপনার মতোই নিঃস্ব, কাঙাল, আত্মচিৎকার গিলে হেসে বেড়ানো জীবন্মৃত আত্মা। আমি আপনাকে ক্ষমা করব না। কখনোই না। আপনি চাইলে সব ছেড়ে ফিরতে পারতেন, আমি নাই বা মানলাম, আপনি বেঁচে থাকতে পারতেন। আপনি কোনোটাই করেননি। আপনার ক্ষমা নেই। যতবার আপনার কথা উঠবে আমি বলব—জয় আমির আমার আসামী, তার স্থান কেবল আমার কাঠগড়ায়। যার কেইস আমি লড়ে যাব আজীবন, কিন্তু শুনানির রায় আসবে না কখনও।
তো সিনিয়র, যা বলতে আজ কলম তুলেছি। সামনের মাসে আপনার বড়সাহেবের বন্ধ হওয়া কেইস ফাইল আবার খুলতে যাচ্ছি। আমার প্রথম কেইস হাতে নিতে যাচ্ছি। আজ আপনি থাকলে কী করতেন, জানি না। হয়ত আমায় থামাতে চাইতেন, আরেকবার বদনাম করে অথবা মারধর করে আঁটকে রাখতেন কোনো বন্দিশালায়! জানি না। তবে আমার পরিকল্পনা খুব একটা ভালো নয়। আমি খুব খারাপ কিছু করার চেষ্টা করব আপনার বড়সাহবের সঙ্গে। নিজের সন্তানের খুনী নাকি অনেকগুলো প্রাণের নাশক হিসেবে–বলতে পারছি না।
•
এটুকু লিখে উঠে পড়ল অন্তূ। অস্থিরতা ঘিরে ধরল খুব তাকে। উঠে গিয়ে বেলকনির গ্রিলে মাথা ঠেকিয়ে আনমনেই গুনগুন করে উঠল। মাঝেমধ্যেই তার কানে ভেসে আসে আজকাল একটি গানের দু-চারটি কলি, তা-ই গেয়ে উঠল
সে—
না জানি কোন অপরাধে দিলা এমন জীবন
আমারে পুড়াইতে তোমার এত আয়োজন…
সুখে থাকার স্বপ্ন দিলা, সুখ তো দিল না
কত সুখে আছি বেঁচে, খবর নিলা না…
আমি ছাড়া কেউ নাই আমার দুঃখের পরিজন
আমারে ডুবাইতে তোমার এত্ত আয়োজন…..
পাড়ার অথবা কর্মক্ষেত্রের মহিলাদের খুব চিন্তা তাকে নিয়ে। সেদিন একজন জিজ্ঞেস করল, “তুমি বিয়ে করবা না?ʼʼ
মাহেজাবিণ বলল, “আমি কি অবিবাহিত?ʼʼ
কত প্রশ্ন জবাবহীন অবস্থায় দিন-রাত চক্রাকারে বয়ে যায়। মাহেজাবিণের বড় কৌতূহল জাগে জয়নাল আমিরের স্ত্রী অর্থাৎ জিন্নাহ আমিরের মায়ের ব্যাপারে। সেই নারীটি কে, কোথায় থাকেন, জীবিত অথবা মৃত! জানা হয়নি কখনও। সে কীসের অপরাধে এই জীবন পেয়েছে তাও অজানা। তার কোথাও কেউ নেই। মূলত এক শিশু ও জোয়ান একটি নারীর ভার বইতে তার এই বেঁচে থাকা। অবশ্য বেঁচে থাকার কোনো নিশ্চয়তা তার নেই। অবরুদ্ধ নিশীথ কখনও ফুরোয় না। কেবল চক্রাকারে ঘুরে বিভিন্ন বিন্দুতে স্থির হয়। এই শহরে রোজ চলে ঘটা করে অবরুদ্ধ নিশীথের খেলা।
—
রূপকথা মাহেজাবিণের কাছে বেশ কিছুমাস ছিল। তার শরীরে যে-সকল ক্ষতের দাগ পলাশের বদৌলতে ছিল, তা ঢেকে গেছিল কারাগারের অযাচিত উন্মাদ-অত্যাচারে। ইনফার্কশনের প্রভাবে ক্ষত থেকে পুঁজ ও রক্ত পড়ার ঘটনা নিয়মিত হয়ে উঠেছিল। তা মাহেজাবিণ নিজ হাতে পরিস্কার ও ড্রেসিং করে দিতে দিতে এমন সব গল্প তাকে শুনিয়েছে যা রূপকথার আন্দাজের চেয়ে কিছু বেশিই ছিল।
জয় আমিরের রেখে যাওয়া টাকাগুলো মাহেজাবিণ তাকে দিয়েছিল চিকিৎসার জন্য। সে গ্রহণ করেনি। তার নামে যথেষ্ট অর্থ আছে। এছাড়া শিক্ষাগতভাবে বিদেশী ডিগ্রিপ্রাপ্ত রূপকথা আজগর আজ পথের পাগলি অথবা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত, মাংস খসে পড়া কুকুরের চেয়েও তুচ্ছজীব। একটি ছোট্ট ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকছে। মাহেজাবিণ তাকে ছাড়তে চায়নি, ভয় ছিল সে আত্মহত্যা করবে। মাহেজাবিণ বোকা। মাহেজাবিণের কোনো ধারণা নেই তার সহনশীলতা সম্বন্ধে। তার শরীরটা আজ ব্যথা-অনুভূতিহীন ঘরের কোণে পড়ে থাকা আসবাবের মতো বৈকি!
একটি অসুস্থ পরিবার থেকে উঠে আসা অসুস্থ শরীর ও মনের অধিকারিনী কিনা সে!তার বাপের বিশাল বড় বাড়ি সিলগালা মারা। পলাশের আরও বাড়ি আছে, যা পুলিশের অশনাক্ত, কিন্তু সে যায়নি। সে একটি নতুন ফ্ল্যাটের বেলকনিতে, দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে পুরোনো দিন স্মরণ করে হাসতে চায়। তার একটা শখ আছে। শরীরের ক্ষতগুলোতে পচন ধরা অবস্থা। সে শুনেছে মানুষের মাংস পচলে তাতে পোকা হয়। এটা কখনও দেখা হয়নি। তার শখ হলো তার শরীরের ক্ষতগুলো ঠিকমতো পচে উঠলে সেখানে পোকা হোক। সেই পোকাদের কাছে সে বর্ণনা করবে শরীরের ব্যথা ও একটি সুস্থ জীবনের তৃষ্ণা কেমন হয়। তার মস্তিষ্ক খুব বেশি অনিয়ন্ত্রিত হতে গেলে সে দৌড়ে অন্তূর কাছে চলে যায়। অন্তিকের মেয়ের সাথে খেলে। এই তো সেদিন তার মনে হলো সেও নারী। জরায়ু আছে, গর্ভধারণ ক্ষমতা আছে, তার বিয়েও হয়েছিল। হতেই পারতো তারও এমন একটি সন্তান।
পরক্ষণেই নিজের ভাবনায় হেসেছে সে। সবাই কেন সব ধরণের আকাঙ্ক্ষা রাখবে? মাহেজাবিণের ভয় সে যখন তখন আত্মহত্যা করতে পারে। কিন্তু সে কখনোই আত্মহত্যা করবে না। সে বেঁচে থাকতে চায়। দেখতে চায় এই দুনিয়াটা আরও কেমন হতে পারে। ব্যথা তাকে ব্যথা দিতে পারে না, সেক্ষেত্রে তার চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে? এমন শক্তিশালী নারী সে মরবে কেন? সে বাঁচতে চায়।
এই তো সেবার পরাগের ফাঁসি হলো না। তাকে কারা যেন বাঁচিয়ে নিলো। বাঁচিয়ে নেবার বদলে পরাগের কাছে তার ত্রাসের ব্যক্তিত্ব কেনা হলো। সে কারাগার থেকে বেরিয়ে আবার ফিরল ত্রাসে। কিন্তু এবার সেই ত্রাসের সাম্রাজ্য তার অবৈধ বাপ বা পলাশের নয়। এবার অন্যের জন্য সে কেবল কাজের কাজী।
পরাগ রূপকথার সাথে জোর করে থাকে। রূপকথার ফ্ল্যাটেই থাকে। রূপকথা যুদ্ধ ঘোষনা করেছিল না থাকতে দেয়া নিয়ে। পরাগ গ্রাহ্য করেনি। করার কথাও নয়। রূপকথা পরাগ ছাড়া এবং পরাগের রূপকথা ছাড়া তো কোত্থাও কেউ নেই। একই বাপের সন্তান হিসেবে চিরকাল রূপকথা পরাগের বোন। রূপকথা বললেই পরাগ রূপকথাকে একা ছেড়ে দেবে নাকি?
কোর্টে আসা-যাওয়ার পথে বেশ কয়েকবার তার সাক্ষাৎ হয়েছিল মাহেজাবিণের সাথে। কথা হয়নি। কেবল চোখভরে দেখেছে সে জীবন-ঝড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তবু নীড়ের গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া অ্যাডভোকেট নারীটিকে। কয়দিন পর নাকি হামজার কেইস আবার রি-অপেনের কাজ হাত নেবে অ্যাডভোকেট সাহেবা। পরাগ সাহায্য করবে বলে ঠিক করেছে। নৈতিক উপায়ে না হোক অনৈতিক উপায়ে।
হামজার কেইস আবার রি-অপেন করাটা নেহাত সহজ কাজ নয়, প্রাণের ঝুঁকিসহ অসীম হয়রানির পথ। তবু এই কাজে হাত দিতে সে বদ্ধপরিকর। এবং সেই দিনের দু’দিন আগে মাহেজাবিণের দরজায় কেউ এলো। তখন মাগরিবের নামাজ শেষ হয়েছে সবে। গোধূলি লগ্ন যাকে বলে। মার্জিয়া দরজা খুলে একটি নারীকে পেল। চিনতে পারল না। সে দেখেনি কখনও।
ভেতরে ঢোকার তাড়া নেই নারীটির মাঝে। মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, “তুমি সে নও, যার কাছে আমি এসেছি।ʼʼ
মার্জিয়া ডাকে, “অন্তূ!ʼʼ
মাহেজাবিণ দরজার কাছে যায়। নারীটি আপাদমস্তক তাকে দেখে। একটি সাদাটে নীল শাড়ি পরা। চোখদুটো কী ভীষণ গভীর, গম্ভীর আর ব্যথাসিক্ত! মুখের গড়ন দেখলে বলতে মন চায় বড় যত্নে সাজানো সুশ্রী চেহারাখানা। একবার তাকালে আবার তাকিয়ে দেখার ইচ্ছে জাগা চেহারা থাকে কিছু, তেমন চেহারা মাহেজাবিণের। ঘাঁড়ের কাছে হালকা কোকড়া চুল পেচানো একটি খোঁপা।
মাহেজাবিণও চিনল না নারীটিকে। কখনোই দেখেনি সে। নারীটির মুখে স্মিত হাসি। চোখদুটো তাকেই দেখছে অপলক। বয়স কত হবে? চল্লিশের বেশিই! আপপৌরে করে শাড়ি পরা। তার ওপর একখানা কাতান ওড়না জড়ানো। মাথা, মুখ আবৃত তাতে। মাহেজাবিণকে দেখে মুখে ধরে রাখা ওড়নার প্রান্ত ছেড়ে দেয়ায় মাহেজাবিণ দেখতে পায় এক অনন্য চেহারার নারী। একটু সামান্য সাজগোজে সৌখিন বোধহয়! চোখের কাজল, ঠোঁটের সামান্য লিপষ্টিক তা-ই বলে।
মাহেজাবিণকে দেখা শেষ হলে নারীটি মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করে, “তুই তাহলে জয় আমিরের বউ, হু?ʼʼ
মাহেজাবিণ হ্যাঁ-না কিছু বলে না। সে বুঝতে চায় নারীটি কে, কেন এসেছে তার কাছে।
—○—
[উপন্যাস/উপাখ্যান কখনও সমাপ্ত হয় না। কেবল কোথাও শুরু করে কোনো এক পর্যায়ে থেমে যেতে হয়। তাই আমার সমাপ্ত লিখতে ইচ্ছে করে না।]